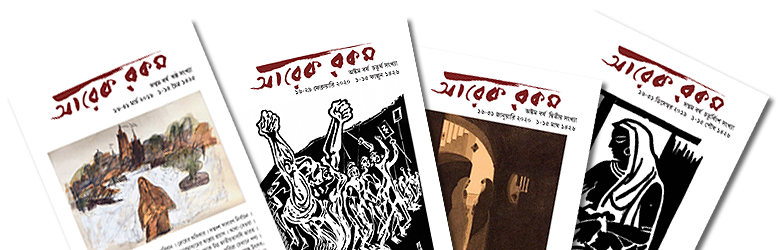আরেক রকম ● নবম বর্ষ অষ্টাদশ সংখ্যা ● ১৬-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ● ১-১৫ আশ্বিন, ১৪২৮
প্রবন্ধ
পরিবেশ সঙ্কট ও ভারতের পরিযায়ী শ্রমিক
সাম্যদেব ভট্টাচার্য
পৃথিবীর সব ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলার ইতিহাসের প্রথম পাতা থেকে ওলটাতে শুরু করলে, নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রতি কবি, শিল্পী, লেখকদের রোম্যানটিসিজিমের শুরু থেকে শেষ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। আমাদের মতো পাস করা আঁতেল বাঙ্গালিরা আজও শেলি, কিটস, ওয়ার্ডসওয়ারথ, দাড়িবুড়ো, বিভূতিভূষণ পেরিয়ে, সাহিত্য, ফটোগ্রাফি, ভ্রমণ পিপাসা এমনকি সিনেমার পর্দায় প্রকৃতির কোলে পা ছড়িয়ে বসে উদাস হতে পছন্দ করি। উদাসী মন কখন যে নৈসর্গিক, প্লেটোনিক, বৈবাহিক, বৈষয়িক সবরকম প্রেমের ককটেল বানিয়ে খাইয়ে দেয়, তা বোঝা সত্যি বড় দায়। ওদিকে ধরণী মায়ের অবস্থা হয়েছে অনেকটা ঘটোৎকচের মতো। অর্থাৎ কাজের বেলায় কাজি আর কাজ ফুরলে পাজি। সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্ক টোয়াইনের মতো রসিক মানুষও বলেছিলেন যে, আবহাওয়ার বিষয়ে সবাই মতামত রাখেন, কিন্তু কেউই কিছু করে ওঠেন না। তারপর টেমস, ভল্গা, মিসিসিপি, নীলনদ, গঙ্গা, সিন্ধু সব নদী দিয়েই প্রচুর জল গড়িয়ে গেছে। সাথে সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন মানবসভ্যতার বর্তমান সময়ের সবথেকে বড় সঙ্কট হিসেবে সামনে উঠে এসেছে। আর এই সঙ্কটের প্রধানতম কারণ হল সভ্য মানুষের বেপরোয়া মুনাফা লোটার অসভ্য নেশা।
সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের জমানা থেকে আজকের দিনের ইনফরমেশান বিপ্লবের দোরগোড়ায় আসার পথে, ধরণীকর্ষণ করে অমৃত তুলতে তুলতে আমরা যে পরিমাণ বিষ ছড়িয়েছি, তা হজম করা শিব ঠাকুরের বাবারও সাধ্য নয়। এককথায় বলতে গেলে বর্তমান পরিস্থিতিতে, গোটা মানবসভ্যতা এক অভূতপূর্ব সঙ্কটের সম্মুখীন, যার প্রতিকার করা কোনো একটি দেশ বা একটি সংগঠনের পক্ষে অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক প্রচেষ্টা ছাড়া এই সঙ্কট থেকে মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। সত্যি কথা বলতে তারপরেও যে এই সঙ্কটের থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।
জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতম দিকটি হল বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (global warming)। শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে ক্রমাগত শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে খনিজ সম্পদের অত্যাধিক ব্যবহার ও সেই কারণে ব্যাপক হারে পরিবেশে কার্বন নিষ্ক্রমণের মাত্রা এই গত শতাধিক বছর ধরে উত্তরোত্তর বেড়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকেই এককথায় বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলা যেতে পারে। গত ৩০-৩৫ বছর ধরে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রচুর জ্বলন্ত লক্ষণ দেখা দেওয়া সত্ত্বেও, পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের সরকারগুলি এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে গভীর অপরিণামদর্শীতার পরিচয় দিয়ে, এককথায় অগ্রাহ্য করে গেছে। গত তিন দশক ধরে খনিজ জ্বালানীর ব্যবহার যে পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়োজন ছিল, সেই লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছেও আমরা পৌঁছাতে পারিনি।
এই প্রসঙ্গে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণের দিক নির্দেশকারী সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থা “ইন্টার গভর্নম্যেনটাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ”, সংক্ষেপে আইপিসিসি-এর গাফিলতির কথা উল্লেখযোগ্য। সংস্থাটি অত্যন্ত নিন্দনীয়ভাবে এই সময়ে পৃথিবীর খনিজ জ্বালানীর হ্রাসের হার সংক্রান্ত তথ্য বিকৃত করে গেছে, আর ক্রমাগত সেই বিকৃত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ তাদের খনিজ জ্বালানীর ব্যবহারের মাপকাঠি ঠিক করেছে। সংস্থাটির খনিজ জ্বালানী এবং বাতাসে কার্বন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত হিসেব নিকেশ করা হয়েছে, “নেগেটিভ এমিসান টেকনোলজি”, সংক্ষেপে 'নেট' নামক এমন একটি অপ্রমাণিত ভবিষ্যতের প্রযুক্তির কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে, যার সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপী সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মোটের ওপর বলতে গেলে 'নেট' হচ্ছে এমন একটি প্রযুক্তি, যার প্রয়োগের মাধ্যমে কথিতভাবে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমানো যাবে, যা পরিবেশের বর্ধিত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে। কিন্তু বাস্তবে এর প্রায়োগিক রূপায়নের বিষয়টি অপরীক্ষিত এবং স্বভাবতই অনিশ্চিত। অথচ আইপিসিসি-র মতো সংস্থা এমন একটি অনিশ্চিত প্রযুক্তির কল্পিত সাফল্যের ওপর নির্ভর করে ক্রমাগত এতো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা দিয়ে চলেছে।
অন্যদিকে বাস্তবে সঙ্কট দিনে দিনে আরও ঘনীভূত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং সম্পদের অপচয় পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদকে দ্রুত নিঃশেষিত করছে। শিল্পজাত বর্জ্য নিষ্ক্রমণ জল, মাটি ও বাতাসের দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, বনসম্পদ হ্রাস, দূষণ, পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে জীব বৈচিত্রের অভূতপূর্ব হ্রাস ঘটছে। গত ২০০ বছরে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে, যার বেশীরভাগটাই হয়েছে ১৯৭০ সালের পর থেকে। এইভাবে যদি অনিয়ন্ত্রিত কার্বন নিষ্ক্রমণ চলতে থাকে, তাহলে আগামী শতকে আসার আগে পৃথিবীর তাপমাত্রার যে পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটবে, তা বিগত তুষার যুগচক্রের শেষে যে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়েছিল, তার থেকেও বেশি। তাই বোঝাই যাচ্ছে যে মানব সভ্যতা এই মুহূর্তে এক চরম অস্তিত্ব সঙ্কটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।
স্বাভাবিকভাবেই, এই খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আমাদের এখন শুধু সচেতন হয়ে উঠলেই চলবে না, পরিবেশ আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী মহাযজ্ঞে নিজেদের সাধ্যমতো অংশগ্রহণও করতে হবে।প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিৎ যে, এই পরিবেশ ও তার সঙ্কটের বিষয়টি বহুমুখী এবং বেশ জটিল। একে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধারা ও তাদের উপধারায় ভেঙ্গে দেখা যেতে পারে। এর সাথে একদিকে যেমন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয় জড়িয়ে আছে, যেগুলির প্রত্যেকটি আলাদা করে মৌলিক আলোচনার দাবি রাখে, অপরদিকে এর শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষিতটিও অনেকগুলি শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। সেই কারণে পরিবেশ সঙ্কট সম্বন্ধে একটি সার্বিক ভাসা ভাসা আলোচনা করার থেকে, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে একমুখী আলোচনা করা অনেক বেশি গঠনমূলক। এই লেখা সেরকমই একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিক থেকে অনুসন্ধান করার একটি প্রয়াস মাত্র। পরিবেশ সঙ্কটের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অথচ অত্যন্ত কম আলোচিত ধারা হল সমাজে খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রায় এর আর্থসামাজিক প্রভাব। এই লেখায় আমরা দেখবার চেষ্টা করবো যে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতম যে দিকটি, সেই বৈশ্বিক উষ্ণায়ণের কারণে ভারতবর্ষের পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনে কী ধরনের গুরুতর সমস্যা তৈরি হচ্ছে।
উষ্ণায়ণ ও পরিযায়ী শ্রমিক
আমাদের সময়ের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি হল যে কিভাবে মনুষ্যসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের গতিকে বিভিন্ন সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশমিত করা যায়। এই প্রশ্নটি আরও গুরুত্বপূর্ণ আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে। এরই সূত্র ধরে উঠে আসা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হল আর্থসামাজিক কারণে বৃহৎ সংখ্যক মানুষের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে অথবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হওয়ার ঘটনা। এর পিছনে আর্থসামাজিক কারণের সাথে জলবায়ুগত কারণটিও সমানভাবে গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে।
ঐতিহাসিকভাবে দেখলে, মানুষের পরিযায়ী হয়ে ওঠার প্রথম কারণ অবশ্যই ছিল জলবায়ু। ২০১১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতবর্ষের প্রায় ৪৫.৫ কোটি মানুষ (অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৭%), অন্য জায়গা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছেন, যার মধ্যে প্রায় ৬৪%-ই হল গ্রামীণ এলাকা থেকে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই, অর্থাৎ প্রায় ৩৬% এসেছেন উত্তরপ্রদেশ আর বিহারের মতো অপেক্ষাকৃত নিম্নআয় সম্পন্ন রাজ্য থেকে। অথচ এই রাজ্যদুটিই গাঙ্গেয় অঞ্চলের মধ্যে পড়ে, যেটি দক্ষিণ এশিয়ার সবথেকে বেশি ফসল উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি। এরসাথে আমরা যদি রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্য দুটি যুক্ত করি, তাহলে এই সংখ্যাটি প্রায় ৫০% পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
রাজ্য থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার এই প্রবণতা কিছুটা মরশুমি হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা দীর্ঘস্থায়ী। এই পরিযায়ী মানুষদের মধ্যে বেশিরভাগই পেশাগতভাবে দরিদ্র প্রান্তিক চাষি। এর থেকে এই কৃষি অর্থনীতির পদ্ধতিগত দুর্বলতা এবং ঝুঁকির বিষয়টিও প্রকট হয়ে ওঠে। অপরদিকে এই গাঙ্গেয় অঞ্চল ভারতের সবথেকে ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল, যেখানে প্রায় ৬৪ কোটি মানুষ দারিদ্রের মধ্যে জীবনযাপন করছেন। প্রসঙ্গত, এই অঞ্চল থেকে পরিযায়ী মানুষের সংখ্যা গত এক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং আগামী দিনে এই প্রবণতা পরিবর্তনের কোনো বস্তুগত সম্ভাবনা নেই। বৈশ্বিক উষ্ণায়ণের কারণে পরিবেশের ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা চাষাবাদের জন্য যত বিরূপ হয়ে উঠতে থাকবে, এই প্রান্তিক মানুষজনের নিজেদের অঞ্চলে প্রথাগত জীবিকায় থাকা ক্রমান্বয়ে ততই কঠিন হয়ে উঠবে। সেই কারণে জলবায়ুর পরিবর্তনকে প্রান্তিক মানুষের জীবিকার প্রয়োজনের স্থানান্তরিত হওয়ার পিছনে অন্যতম বড় কারণ হিসেবে দেখা যেতে পারে।
ভারতের মতো দেশে, জীবিকার প্রয়োজনে অনুন্নত গ্রাম থেকে বড় শহরগুলিতে চলে আসা এক চিরাচরিত রীতি এবং সেটি আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত থেকে দেখলে যথেষ্ট স্বাভাবিকও বটে। বস্তুত গ্রাম থেকে শহরের উদ্দেশে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের পরিযানের পিছনে মূলগত কারণ অবশ্যই খাদ্যসুরক্ষার অভাব। এটি শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্যি। প্রসঙ্গত ২০১৭ সালে রাষ্ট্র সঙ্ঘের Food and Agricultural Organization-এর বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে “Change the future of migration. Invest in food security and rural development” - স্লোগানটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ভারতের ক্ষেত্রে মূলত এই প্রবণতাটি থাকে দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, কলকাতার মতো বড় শহরগুলিতে আসার, যেখানে ইতিমধ্যেই জনসংখ্যার চাপ যথেষ্ট, এবং গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সঙ্কট যেখানে প্রকট হয়ে উঠছে। এই লেখায় আমরা মূলত আকস্মিক তাপপ্রবাহ ও উপকূলবর্তী বন্যা এই দুটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সাম্ভাব্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে আলোকপাত করবো এবং দেখাতে চেষ্টা করবো যে এর ফলে এই পরিযায়ী দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষজনের জীবন-জীবিকা কিভাবে বিপন্ন হওয়া প্রায় অবশ্যম্ভাবী।
আকস্মিক তাপপ্রবাহ ও উপকূলবর্তী বন্যা
আগামীদিনে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে ভয়াবহ তাপপ্রবাহ বৃদ্ধি পাবে বলে পরিবেশবিদরা অনুমান করছেন। (এই প্রসঙ্গে আগ্রহী পাঠক, চলতি বছরের 'জিওফিজিক্স রিসার্চ লেটার' পত্রিকার ৪৮ সংখ্যার “Deadly heat stress to become commonplace across south asia” শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন।) এর ফলে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের প্রবল স্বাস্থ্যসঙ্কট দেখা দেওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।
এটি একটি গবেষণালব্ধ সত্য যে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সেখানকার তাপমাত্রার বৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। 'নেচার' পত্রিকার ২০১৯ সালের ৫৭৩ সংখ্যার “Magnitude of urban heat islands largely explained by climate and population” শীর্ষক প্রবন্ধে মানলি এবং তাঁর সহযোগীরা তাপপ্রবাহ জনিত মৃত্যুর হারের সাথে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। শহরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে, জনসংখ্যার ঘনত্ব অনুযায়ী কিছু তাপীয় দ্বীপ (Urban heat island) তৈরি হয়, যেখানকার উষ্ণতা আশপাশের অঞ্চল থেকে অনেকটাই বেশি। এই ধরনের তাপীয় দ্বীপের তীব্রতার সাথে অঞ্চলের জনঘনত্বের এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণের স্বভাবতই একটা আনুপাতিক সম্পর্ক আছে (এই প্রসঙ্গে আগ্রহী পাঠক নেচারের উল্লিখিত প্রবন্ধটি দেখুন )।
গ্রীষ্মের সময় জনঘনত্ব ও বৃষ্টিপাতের সাথে সম্পর্ক রেখে, এই তাপীয় দ্বীপগুলির তাপমাত্রা ও সংখ্যা বেড়ে যায়। আরও বহু কারণের সাথে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যার ফলস্বরূপ গ্রীষ্মকালে প্রায় সমগ্র বিশ্বব্যাপী শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য, বিগত কয়েক দশক ধরে প্রচণ্ড মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এরফলে এই অঞ্চলগুলির মধ্যে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনারও অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটছে। ফলত এটি খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, দিল্লীর মতো অত্যন্ত ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে, তাতে প্রাণঘাতী তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা প্রবলভাবে বেড়ে চলেছে। গত কয়েক বছরে দিল্লী শহরের গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রার অভূতপূর্ব বৃদ্ধি এক্ষেত্রে যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ। প্রসঙ্গত এই সময়ে দিল্লীতে তাপ নিঃশেষণ জনিত অসুস্থতা এবং মৃত্যুর ঘটনাও উপর্যুপরি বেড়ে চলেছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল যে, এই দুর্যোগের সবথেকে বড় বলি হওয়ার সম্ভাবনা এই পরিযায়ী শ্রেণির মানুষজনের, কারণ তাঁরা ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে থাকেন যেখানে বসবাসের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধাগুলি অপর্যাপ্ত। এই ধরনের দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য যে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ, সেগুলি তাদের কাছে বিলাসিতার সমান। ওপর পক্ষে এটাও সত্য যে পরিযায়ী মানুষজনের সংখ্যা দিল্লীর মতো শহরগুলিতে ক্রমাগত বেড়ে চলাও সেখানকার জলবায়ু পরিস্থিতিকে উত্তরোত্তর আরও সংকটজনক করে তুলছে।
অপরদিকে মুম্বাই-এর মতো উপকূলবর্তী শহরগুলিতে ক্রমবর্ধমান ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ভয়াবহ বন্যা হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে চলেছে। গ্রীষ্মের সময় ভারত মহাসাগরের উত্তরভাগ জুড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে বিশেষত আরব সাগর জুড়ে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা ক্রমবর্ধমান। জলবায়ুর পরিবর্তন এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলেছে। বিষয়টির আরেকটু গভীরে গিয়ে চর্চা করা যাক।
সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাইক্লোনের ক্ষমতা অনেকগুনে বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চলতি বছরের মে মাসের হিসাব অনুযায়ী আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর উভয়ের তাপমাত্রাই স্বাভাবিকের থেকে অন্তত এক ডিগ্রি বেশী ছিল। অর্থাৎ এই সময়ে সাইক্লোনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রয়োজনীয় লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক সাইক্লোন সংক্রান্ত গবেষণা অনুযায়ী, শক্তিশালী সামুদ্রিক ঝড়ের সংখ্যা প্রতি দশকে ৮% করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে 'পিএনএএস' পত্রিকার গত বছরের ১১৭ সংখ্যার “Global increase in major tropical cyclone exceedance probability over the past four decades” প্রবন্ধটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধটিতে গত ৪ দশকের পরিসংখ্যান ব্যবহার করে সাইক্লোনের এই দশক প্রতি বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয়েছে। অপরদিকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের জলস্তরের যে নিয়মিত বৃদ্ধি ঘটছে, সামুদ্রিক ঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে সেটিও আরেকটি কারণ। নাসার তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর সমুদ্রের জলস্তর প্রায় ৩.৩ মিলিমিটার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
এইসকল তথ্য শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার উপকূলবর্তীয় শহরগুলির পক্ষে যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। এই সব অঞ্চলগুলিকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রাণভোমরা বলা যায়। তাই বলা চলে যে, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবন ও জীবিকা আগামী সম্ভবত কয়েক দশকের মধ্যে এক প্রবল সঙ্কটের মধ্যে পড়তে চলেছে। আর ভারতের কথায় আসলে, মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, শুধু মুম্বাই নয়, এদেশের প্রায় সব উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে অদূর ভবিষ্যতে প্রবল বন্যা আছড়ে পড়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। ইতিমধ্যেই আম্ফানের মতো ভয়ঙ্কর ঝড়ের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা সেই সত্যিকেই আরও জোরের সাথে প্রতিষ্ঠা করে। এইধরনের আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতি সামলানোর জন্য এইসব অঞ্চলগুলির প্রশাসনের কাছে আপৎকালীন ব্যবস্থাপনা ও ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই উপকূলবর্তী শহরগুলি, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এবং সেই কারণে এইসব শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নগরায়নের প্রবণতা বর্তমানে অনেক বেশী। স্বাভাবিকভাবেই, তাই এই শহরগুলি এবং তাদের লাগোয়া অঞ্চলে ঠিকা শ্রমিক, নির্মাণশিল্পী ইত্যাদি স্বল্প মজুরির শ্রমশক্তির চাহিদা প্রচুর।সেই কারণে কাজের খোঁজে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী মানুষের সংখ্যা এইসব অঞ্চলে উপর্যুপরি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। স্বভাবতই শহরগুলির আঞ্চলিক তাপমাত্রার ওপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে, যা আবার ঘুরিয়ে তাপপ্রবাহ এবং সামুদ্রিক ঝড়ের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলছে। মুম্বাইয়ের মতো শহরগুলিতে ভিনরাজ্য থেকে কাজ করতে আসা মানুষজন মূলত নিচু বস্তি এলাকায় বসবাস করেন। তাই এটি সহজেই অনুমান করা যায় যে এইরকম আকস্মিক দুর্যোগ হলে এঁদের জীবন-জীবিকার ওপর কীরকম ভয়াবহ আঘাত নেমে আসবে। জীবনের ঝুঁকির কথা ছেড়ে দিলেও, শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যা হবে তা সামলে ওঠা এঁদের পক্ষে অর্থনৈতিকভাবে প্রায় অসম্ভব।
মোটের ওপর তাই বলাই যায় যে, ভারতের ঘনবসতিপূর্ণ ও শ্রমনিবিড় বড় শহরগুলি আগামীদিনে পরিবেশ সংক্রান্ত দুর্যোগের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠতে চলেছে, যার সবথেকে ক্ষতিকারক প্রভাব পড়বে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় থাকা গরীব শ্রমজীবী মানুষজনের ওপর, যাদের বেশিরভাগই ভিন রাজ্য থেকে কাজের খোঁজে শহরে এসে বসবাস করছেন। উপযুক্ত বাসস্থান, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, পানীয় জলের মতো ন্যূনতম বাবস্থাপনার অভাব বাস্তব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে, এই প্রান্তিক পরিযায়ী মানুষদের সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সুদূরপ্রসারী আর্থসামাজিক পরিকল্পনা নেওয়া এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে সর্বস্তরের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলিকে সচেতন হয়ে উঠতে হবে।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার পদ্ধতি মূলত দু'রকম। প্রথমত দুর্যোগ যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া (preventive measures) এবং দ্বিতীয়ত দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া (mitigative measures)। কার্যক্ষেত্রে প্রাথমিক ব্যাবস্থাপনাটির জন্য বেশ কিছু প্রকল্পের অন্তত ঘোষণা শোনা গেলেও, দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি আমাদের দেশে একেবারেই অবহেলিত। আমাদের দেশে যেকোনো রকম দুর্যোগ মোকাবিলার পরিকল্পনা যে কতটা অপ্রতুল, তা আমরা গত এক বছরের ওপর ধরে অতিমারি মোকাবিলায় যে চরম প্রশাসনিক গাফিলতি দেখেছি, তার থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের অতি দ্রুত এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ে তুলতে হবে, যার কথা ২০২১ সালের ভারত সরকারের National Action Plan for Climate Change-এর নথিতে উল্লেখও করা হয়েছে।
ভারত নিজেকে বর্তমানে নীতিগতভাবে, জলবায়ু বান্ধব সংবেদনশীল অর্থনীতির পক্ষে বলে দাবি করে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন খুব একটা চোখে পড়ে না। ভারতকে আসন্ন জলবায়ু সঙ্কটের যথার্থ মোকাবিলা করতে গেলে শুধুমাত্র নীতি ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, তার যথাযথ প্রণয়নের রাস্তাও বাতলে দিতে হবে। সাথে সাথে জলবায়ু বান্ধব নীতি প্রণয়নকে সুচারুভাবে বিকেন্দ্রীভূত করতে হবে রাজ্য, জেলা, মহকুমা এমনকি ব্লক স্তর পর্যন্ত। আলাদা করে নজর দিতে হবে কৃষিক্ষেত্রে। বিশেষ করে সেই সব অঞ্চলে, যেখান থেকে কৃষি বান্ধব পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও, প্রান্তিক কৃষিনির্ভরশীল মানুষ বৃহৎ সংখ্যায় জীবিকার প্রয়োজনে স্থানান্তরিত হচ্ছেন। চাষাবাদের ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের প্রভাব ন্যূনতম করবার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিতে হবে এবং তার যথার্থ প্রণয়নও করতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে সরকারি ভরতুকি বৃদ্ধি, উন্নত অভিযোজনশীল ফসলের চাষকে উৎসাহিত করা, উন্নত জলসেচ-এর ব্যবস্থা করা, ফসলের যথার্থ মুল্য যাতে কৃষক পায় তা নিশ্চিত করা, সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে ফসল কেনা, উন্নত মানের সরকারি গুদামের সংখ্যাবৃদ্ধি, বেসরকারি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে ফসল ক্রয় বিক্রয়ের দাম বেঁধে দেওয়া, মজুতদারি ঠেকাতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি জনবান্ধব সংবেদনশীল নীতি প্রণয়নকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের স্তর থেকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রান্তিক মানুষকে যদি তার নিজের জায়গায় যথার্থ রোজগারের সুযোগ সুবিধা না দেওয়া যায়, তবে বৃহৎ সংখ্যায় পরিযানের এই প্রবণতা কিছুতেই ঠেকানো যাবে না। আর এই প্রবণতা ঠেকানো না গেলে সঙ্কটের সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে।
আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে গত কয়েক দশক যাবৎ পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কৃষিক্ষেত্রে সঙ্কট ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই প্রবণতা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। তাই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া আজকে অতি আবশ্যক হয়ে উঠেছে। যথাযথ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা যেমন কৃষিক্ষেত্রে সঙ্কটকে প্রশমিত করবে, তেমনি তার ফলস্বরূপ, প্রান্তিক মানুষের বড় শহরের উদ্দেশে পলায়নের প্রবণতাকেও কমাতে সাহায্য করবে। এ প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাদ্যসুরক্ষার অভাব, গ্রাম থেকে শহরে ব্যাপক পরিযানের পিছনে অন্যতম বড় কারণ। আর কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনশীলতার ওপর খাদ্যসুরক্ষার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অন্যদিকে দেশের কৃষি পরিস্থিতি সঙ্কটাপন্ন হয়ে চলেছে পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন আর ক্রমাগত নগরায়ণের মতো বিভিন্ন কারণে কৃষিজমির হ্রাসের জন্য। এছাড়াও ভারতে কৃষিসঙ্কটের পিছনে রেশন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, সরকারি ভরতুকির ও আর্থিক সুরক্ষার অভাব, বেসরকারি ভুঁইফোড় মজুতদারদের প্রভাব, এরকম প্রচুর অর্থনৈতিক কারণও সমানভাবে দায়ি। কৃষিসঙ্কটের নেপথ্যের অর্থনৈতিক কারণ আলাদা করে গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে, যার সুযোগ এই লেখাতে নেই। সেই কারণে আমরা বিষয়টিকে শুধুমাত্র উপস্থাপিত করে বিষয়ান্তরে চলে যাচ্ছি। কিন্তু তার সাথে এটাও উল্লেখ করছি যে, আমাদের বর্তমান লেখাটির মূল যে বিষয়, সেটিকে সততার সাথে যথার্থভাবে বুঝে উঠতে গেলে কৃষি অর্থনীতির প্রশ্নগুলিকে অগ্রাহ্য করা কখনই সম্ভব নয়।
আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশে, যেখানে জনসংখ্যার অধিকাংশই হয় কৃষি বা তার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের সাথে জুড়ে আছে, সেখানে পরিবেশ, পরিযান ও জলবায়ুর প্রশ্নগুলি সরাসরি কৃষি অর্থনীতির সাথে যুক্ত। তাই কৃষি অর্থনীতিকে গুরুত্ব না দিয়ে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের শহরে পলায়নের সমস্যা এবং সেই সম্পর্কিত পরিবেশ সঙ্কটকে কখনই মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। অপরদিকে বড় শহরগুলি, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের শহরগুলিতে ক্ষতিকারক কার্বন নিষ্ক্রমণের মাত্রা যদিও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবুও এই শহরগুলিকে পরিবেশ বান্ধব কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবর্তন করা খুবই সম্ভব। যে সকল শহরগুলিতে মারাত্মক তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা বেশি, সেখানে যথাযথ প্রতিকারমূলক কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। মুম্বাইয়ের মতো বড় শহর, যেখানে পরিযায়ী শ্রমিকের অন্তঃপ্রবাহ হয়তো সবথেকে বেশি, এবং যে শহরটি বন্যাপ্রবণও বটে, সেখানে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থা ভীষণভাবেই অপ্রতুল। বড় শহরগুলির এই ঘাটতি যত শীঘ্র সম্ভব দূর করতে হবে। অপরদিকে শহরে বসবাসকারী পরিযায়ী শ্রমিক, যাদের বেশিরভাগ অংশই বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্র বা সার্ভিস সেক্টরের সাথে যুক্ত, তাদের জীবন-জীবিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত জরুরি। সেই কারণে রেশন ব্যবস্থা, সরকারি হাসপাতাল, সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রকল্প ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপর নতুন করে জোর দিতে হবে।
আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট, যেকোনো রকম বিপর্যয়েরই প্রথম এবং ভয়ঙ্করতম আঘাত আসে দরিদ্র, প্রান্তিক, পরিযায়ী খেটে খাওয়া মানুষের ওপর। এর জ্বলন্ত উদাহরণ আমরা গত একবছরের বেশী সময় যাবৎ ধরে দেখে চলেছি অতিমারি বিপর্যয়ের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। গত বছর কয়েক ঘণ্টার নোটিশে ঘোষিত লকডাউনের পরবর্তী প্রায় কয়েক মাস যাবৎ যে অমানবিক দৃশ্য সামনে এসেছে, তা অদূর ভবিষ্যতে ভোলবার নয়। প্রায় ৪ কোটি মানুষ মাত্র একটি ঘোষণার জেরে মুম্বাই, দিল্লীর মতো শহরগুলি থেকে ভরা গ্রীষ্মের দাবদাহ মাথায় নিয়ে পায়ে হেঁটে নিজেদের গ্রামের পথে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছেন। পথ দুর্ঘটনায়, অথবা প্রচণ্ড গরমে কত মানুষের যে মৃত্যু হয়েছে তার সঠিক হিসেব আজও নেই। আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা সমাজের বৃহত্তম অংশের মানুষকে প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর করে তুলছে দিনের পর দিন ধরে। আর আমাদের গোটা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আলোচনা থেকেই এই মানুষগুলি যেন চিরতরে মুছে গেছে। আমাদের আইপিএল দেখা, মঙ্গলগ্রহে যাওয়া, বুলেট ট্রেন চালানো, জনে জনে সুন্দর পিচাই হওয়ার স্বপ্ন দেখা বিশ্বগুরু ভারতের পরিসরের মধ্যে দেশের সবথেকে বেশি সংখ্যক এই মানুষগুলি এক চিলতে জায়গাও আর পান না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে মঙ্গলগ্রহে যেমন মানুষ থাকে না, তেমনি দেশের বেশির ভাগ মানুষকে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক গোটা ডিসকোর্সটারই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাধ করে ডেমোক্রেসি কপচানোও যায় না।