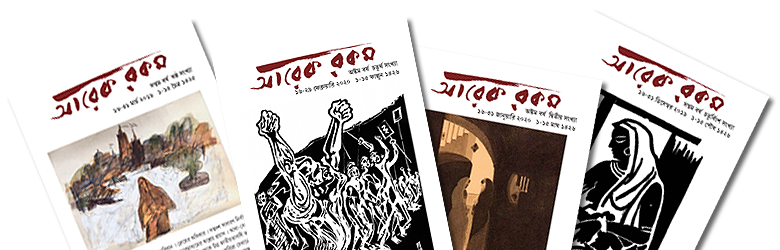আরেক রকম ● নবম বর্ষ অষ্টাদশ সংখ্যা ● ১৬-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ● ১-১৫ আশ্বিন, ১৪২৮
প্রবন্ধ
প্যারি কমিউন - যুগান্তের ইস্তেহার
পার্থ রায়
মার্কস-এঙ্গেলসের যুগলবন্দীতে রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর জন্যে একটা প্রাথমিক ও সংক্ষিপ্ত খসড়া প্রস্তুত করছিলেন এঙ্গেলস, প্রশ্নোত্তরের আকারে, ১৮৪৭ সালের নভেম্বর মাসে। সেই লেখাতে এঙ্গেলস বললেন, কমিউনিস্টরা খুব ভাল করেই জানে যে, বিপ্লব খামখেয়ালের বশে বা, কারো ইচ্ছা অনিচ্ছায়, ঘটানো যায় না, বরং সর্বত্র এবং সব সময় তা হয়েছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত অবস্থাগুলির পরিণতি হিসেবে, যে পরিস্থিতিগুলি কোনো একটা দল বা পুরো দস্তুর কোনো শ্রেণির আকাঙ্ক্ষায় বা হুকুমে উদ্ভূত হয়নি। যদিও কমিউনিস্টরা শান্তিপূর্ণ পথের অনুসারী, তবু তারা এও দেখতে পাচ্ছে, যে প্রায় সমস্ত সভ্য দেশে প্রলেতারিয়েতের অগ্রগতি হিংস্রভাবে দমন করা হচ্ছে, এবং কমিউনিজমের প্রতিপক্ষরা সর্বশক্তি দিয়ে বিপ্লবের বিরুদ্ধে কাজ করছে (প্রিন্সিপলস অফ কমিউনিজম, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, পল সুইজির ইংরেজি অনুবাদ, মান্থলি রিভিউ, ১৯৫২)।
এঙ্গেলসের এই লেখার মাত্র ২৪ বছরের মধ্যে তার বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে পৃথিবীর প্রথম শ্রমিকরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটলো। বলা বাহুল্য, প্যারি কমিউন জন্ম নিলো কোন পরিকল্পনামাফিক নয়, গরিব গুর্বো জনতার কোন ষড়যন্ত্রের ফলেও নয়, কারো আকাঙ্ক্ষায় বা আজ্ঞাবশতও নয় - নিতান্তই, ‘উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিণতি হিসেবে’। এমনকি, প্রায় বিনা রক্তপাতে সেই শ্রমিক রাষ্ট্র - প্যারি কমিউন - জন্মলাভ করলো (যদিওবা কিছু রক্তপাত ঘটলো, তা ঘটলো ভার্সিল সেনাবাহিনীর একাংশ বন্দুক উলটো দিকে ঘুরিয়ে বিদ্রোহ করার ফলে)। গরিব জনতার স্বাধীনতা আর মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বন্ধনহীন করে যে প্যারি কমিউন জন্ম নিলো, তা কিন্তু ফ্রান্সের (এমনকি ইউরোপের অন্য দেশগুলির) বুর্জোয়াদের হাড়ে কাঁপন ধরালো। শুরু হলো অন্তহীন ষড়যন্ত্র, সারা ইউরোপ জুড়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ পূর্ণ প্রচার, এবং শেষ পর্যন্ত হামলা ও হিংস্রতা - যা আজও অন্তহীনভাবে চলছে।
২০২১ সালে, প্যারি কমিউনের দেড়শো বছরে, যখন ফ্রান্সে বা সারা বিশ্ব জুড়ে কমিউনের দিনগুলিকে স্মরণ করা হচ্ছে, তখন আবারও প্রচারমাধ্যম জুড়ে, ঘৃণার বিষভাণ্ড উপুড় করে কমিউনের অপযশ করা হচ্ছে। সত্যিকে ষোলো আনা উল্টিয়ে বলা হচ্ছে প্যারি কমিউন নাকি অরাজকতা আর শ্রেণি বিদ্বেষ। বলা হচ্ছে, কমিউনার্ডরা (অর্থাৎ, কমিউনের সংগঠকরা) নাকি ‘খুনে’। ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'বিবিসি নিউজ' সংবাদ শিরোনামে লিখেছে, ‘প্যারি কমিউন - যে বিদ্রোহ সার্ধ শতবর্ষেও ফ্রান্সের মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে চলেছে’ (বিবিসি নিউজ, ১৮ মার্চ, ২০২১)।আরেকটি ব্রিটিশ সংবাদপত্র, 'দি গার্ডিয়ান', প্রায় একই ভাষায় কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে কমিউনকেঃ দেড়শো বছর পরে কমিউনার্ডরা ফিরে আসছে, আবারও ভাগ করছে প্যারিসকে (দি গার্ডিয়ান, ৭ মার্চ, ২০২১)। তাঁদের বক্তব্য কমিউনের দিনগুলিকে স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বাড়ানো হচ্ছে।
শুনে মনে হয়, পৃথিবী যেন বা ভেদাভেদহীন, এখানে ভাগ বাঁটোয়ারা নেই, ধনী-দরিদ্র নেই, মজুর-মালিক নেই। যেন বা শিল্পোন্নত ব্রিটেন বা ফ্রান্সে কেবল সমানাধিকার আর সাম্যই বিরাজমান, যেন বা শোষণ আর লুন্ঠন ধরাতলে নেই, কখনও ছিলনা, তাদের গ্রহান্তর থেকে এনে পৄথিবীর ধুলোয় টেনে নামাচ্ছে প্যারি কমিউন। আহারে, সংবাদমাধ্যম! কী চমৎকার, সরল তোমাদের গণিত যাতে শুধু ব্যাঙ্কের আমানতের যোগ আর গুনটুকুই ধরা পরে, কিন্তু না-পাওয়া-বেতনের বিয়োগ আর ভাগগুলো ধরা পড়ে না। বলা বাহুল্য, পুঁজিবাদের পৄষ্ঠপোষক এই সংবাদমাধ্যমগুলির সাংবাদিকরা ক্ষুধা আর ক্ষুধামান্দ্যের ভিতর যে ঘোরতর অসাম্য তা দেখতে পান না। লুটেরা আর লুন্ঠিতকে এক পঙতিতে বসিয়ে শাটার টিপে তাঁরা ফটো তোলেন আর দেশ-বিদেশের খবরের কাগজে সে ছবি ত্বরিৎগতিতে ছাপাও হয়। কিন্তু সে ছবিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পিটুনি খাওয়া মজুর তার পিটুনি-দেওয়া হুজুরের গুণ্ডাদের সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই, অনেক বাগাড়ম্বর করে, অনেক ধুম্রজাল ছড়িয়ে, যে ঐক্য আবিষ্কার করার চেষ্টা হয় তা আসলে নিতান্তই কৃত্রিম, অবাস্তব এবং এমনকি, হাস্যকর।
পুঁজিবাদে অসাম্যের অশ্লীলতাকেই ‘স্বাভাবিক নিয়ম’ হিসেবে চালানো হয়। সেটাকেই বলে ‘শান্তি’, সেটাকেই বলে ‘মিলন’, সেটাকেই বলে ‘ঐক্য’। একদিকে চাষা, মজুর, কেরানি, দোকানি, কারিগর, কর্মচারীদের ক্রমবর্ধমান অভাবী ভিড়, অন্যদিকে কতিপয় দেশী বিদেশী মালিকদের দু'কুল ভাসানো ধনসম্পদ। একদিকে অভিজাত সম্প্রদায়, অন্যদিকে জীবনযাপনের জাঁতাকলে পিষ্ট অভাবী সম্প্রদায়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সৌজন্যে সমাজদেহের একদিকে অন্তহীন ক্ষয়, অন্যদিকে বিরামহীন নির্মাণ, এইরকম এক ‘শোষক আর শোষিতের ঐক্য’! আসলে, জাদুকরের ভোজবাজি - বাস্তবে অনুপস্থিত!
নব্য উদারবাদী রাষ্ট্রে সমাজদেহের বিপাক ক্রিয়ার এই গোলযোগ এখন আর সামান্য রোগ নয়, তা এখন ভয়ংকর মহামারির আকার ধারণ করেছে। সমাজদেহের এই বুনিয়াদি অসুখ শূণ্যগর্ভ ঐক্যের কোনো সান্তনাবাক্যে নিরসন হবে না। অন্তহীন কথার ঝুমঝুমি বাজিয়েও এর নিরাময় সম্ভব নয়। নিরাময়ের জন্যে প্রয়োজন অনুসন্ধান, রোগনির্ণয়, স্বীকৄতি। হ্যাঁ, অসাম্য আছে, হ্যাঁ, শোষণ আছে, হ্যাঁ, শ্রেণিভেদ আছে। তাই, জোড়াতাপ্পি লাগানো ঐক্য নয়, একমাত্র শ্রেণিশোষণের অবসানেই চূড়ান্ত, অনপনেয়, টেঁকসই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আশু প্রয়োজন বর্বর শ্রেণিশোষণের উচ্ছেদ, এবং কালক্রমে শ্রেণির উচ্ছেদ। শ্রেণির উচ্ছেদের ভিতর দিয়ে টেঁকসই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই শ্রেণিযুদ্ধ ক্রমশঃ তীব্র হওয়া চাই।সমাজদেহে শ্রেণিযুদ্ধ আপন গতিতে চলছে অবিরাম, তাকে সচেষ্ট, সক্রিয়ভাবে বাড়াতেই হবে। শ্রেণিশোষণের উচ্ছেদের লক্ষ্যকে সফল করার স্বার্থেই কমিউনের গৌরবজনক ঐতিহ্যকে স্মরণ করতে হবে, ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। তাই, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রচারকদের কমিউনের বিরুদ্ধে তোলা বিভেদের অভিযোগ শুধু যে ভিত্তিহীন তা নয়, তা পুঁজিবাদের ছাতাপড়া অচলায়তনকে শ্রেণিসংগ্রামের গর্জমান ঘূর্ণাবর্তের কবল থেকে রক্ষা করার একটা শঠতাপূর্ণ মিথ্যা প্রচেষ্টাও বটে।
কমিউন হলো, মার্কসের ভাষায়, ‘দখলদারদের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করা’ (‘expropriation of the expropriators’)।সমস্ত দখলদারির নিঃশর্ত, নিরঙ্কুশ অবসানের জন্যে গরীব গুর্বো শ্রমিকজনতার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল - এই লক্ষ্যে কমিউন ছিলো আবিশ্ব প্রলেতারিয়েতের পক্ষে ঐতিহাসিক প্রথম পদক্ষেপ।
কমিউনের উদ্ভব
উনিশ শতকের পুঁজিবাদী দুনিয়ায় প্যারি কমিউন ছিল, উজ্জ্বল উল্কার মতো। কিন্তু মাত্র ৭২ দিন। প্যারিসের জনজাগরণের শুরু ১৮ই মার্চ, ১৮৭১। ক্ষমতা দখল করার পর নতুন শাসক অ্যাডল্ফ থিয়ার্স সেনা পাঠিয়েছে প্যারিসের সশস্ত্র শ্রমিকজনতাকে নিরস্ত্র করার জন্যে। ক্ষুব্ধ জনতা আর ন্যাশনাল গার্ড একত্র হয়ে সেই নিরস্ত্রীকরণের প্রতিরোধ করেছে। থিয়ার্সের পাঠানো সরকারি সেনার একাংশ বন্দুকের নল উলটোদিকে ঘুরিয়েছে, হত্যা করেছে সরকারি বাহিনীরই দুই জেনেরেলকে। জনতা দখল নিয়েছে গোটা প্যারিসের, সমবেত হয়েছে শহরের তাৎপর্যপূর্ণ স্থান হোটেল ডে ভিলা (সিটি হল), তুলেছে লাল পতাকা। ইতিমধ্যে, প্যারিসের ক্ষুব্ধ সশস্ত্র জনতার মেজাজ টের পেয়ে থিয়ার্স সরকার লোটাকম্বল গুটিয়ে পালিয়েছে ফ্রান্সের আরেক শহর ভার্সাই-তে। সম্পূর্ণ অপকল্পিতভাবে - যদিও আকস্মিকভাবে নয় - শুরুয়াৎ হয়েছে পৄথিবীর প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্র প্যারি কমিউনের।
১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর এই হোটেল ডে ভিলাতেই সমবেত হয়েছিলো প্যারিসের জনতা। জনতা উদ্বেলিত, খবর পৌঁছিয়েছে প্যারিসে, সাদানের (Sedan) যুদ্ধে জার্মানির কাছে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত হয়েছে ফ্রান্সের সেনাবাহিনী, সশরীরে আত্মসমর্পণ করেছেন লুই বোনপার্টের ভাগিনা ফ্রান্সের সর্বময় শাসক নেপোলিয়ান-৩।এর আগে, ১৮৭০-এ জার্মানির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু করেছিল ফ্রান্স। এখন, নেপোলিয়ানের সেই সাম্রাজ্য লোলুপতা ধুলোয় মিশেছে। এখন, ফ্রান্সের দখল নিতে এগিয়ে আসছে জার্মানির সেনাবাহিনী। খবর পেয়ে হোটেল ডে ভিলার শীর্ষে টাঙ্গানো নেপোলিয়ান সাম্রাজ্যের প্রতীক দ্বিতীয় রিপাবলিকের পতাকা টেনে নামিয়েছে ক্ষুব্ধ জনতা, প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তৄতীয় রিপাবলিকের। ক্ষমতায় বসানো হয়েছে লুই জুল ত্রোচু-কে। নতুন সরকারের নাম হয়েছে ‘গভর্নমেন্ট অফ ন্যাশনাল ডিফেন্স’ - জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার! ক্রমে, অগ্রগামী জার্মান সেনাবাহিনী অবরুদ্ধ করছে প্যারিস, আর পরবর্তী তিন মাসের জন্যে অবরুদ্ধ হচ্ছে প্যারিস। ইতিমধ্যে, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন এই ‘জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার’ বিসমার্কের (অটো ভন বিসমার্ক) কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। অস্ত্র সংবরণ করেছে জার্মান সেনাবাহিনী, আলোচনা চালিয়ে তৈরি হচ্ছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের দলিলঃ ফ্রান্সের সেনাবাহিনী জার্মান সেনাবাহিনীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করবে, ফ্রান্সের দুই ভূখণ্ড আলজাস আর লারেইন জার্মানিকে ছেড়ে দেবে ফ্রান্স যা অবিলম্বে জার্মানির মানচিত্রে যুক্ত হবে, বিপুল অর্থ ফ্রান্স দেবে জার্মানিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ, আইনসভার নির্বাচন ডেকে সেই নতুন আইনসভার অধিবেশন বসাতে হবে বর্দো শহরে। সেই অধিবেশনে এই চুক্তিকে ছাড়পত্র দিতে হবে।
চুক্তি মোতাবেক নির্বাচন হয়েছে ১৮৭১-এর ফেব্রুয়ারির শুরুতে। ফেব্রুয়ারির শেষে, নির্বাচনের পরে, রিপাবলিকানদের পক্ষে ক্ষমতা দখল করে দাসত্বের চুক্তি চূড়ান্ত করেছে থিয়ার্স সরকার। ততক্ষণে, এই আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে প্যারিসের স্বাধীনতাকামী, জাগ্রত জনতা। এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেই ১৮৭১ সালের মার্চে, হোটেল ডে ভিলার শীর্ষে তোলা হয়েছে কমিউনের রক্তপতাকা, এবং তা মোটেই আকস্মিক নয়।
উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ
কমিউনের নির্বাচিত সদস্যদের ভিতর এক তৄতীয়াংশ ছিলেন গায়েগতরে-খাটা শ্রমিক এবং এদের মধ্যে অনেকেই মার্কস-এঙ্গেলসের নেতৃত্বাধীন প্রথম আন্তর্জাতিকের ফ্রান্স শাখার সদস্য। ভার্সাই বাহিনীর পশ্চাদপসরণ ও প্যারিস মুক্ত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই এই সদস্যরা প্যারিস ন্যাশনাল গার্ডের কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ নির্বাচনে প্যারিসের জনতার দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন। এরা কেউ, মার্কসের ভাষা্য়, ‘প্রাজ্ঞ সমাজবাদী’ ছিলেন না। কিন্তু সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স গ্রন্থে মার্কস বললেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের পদক্ষেপে অসাধারণ ‘বিচক্ষণতা’ আর ‘সংযমের’ পরিচয় ছিলো।
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কমিউনের পদক্ষেপগুলির ভিতর অন্যতম ছিলো, রাষ্ট্রের দমনমূলক বাহিনী - অর্থাৎ মজুদ সেনা বাহিনীর - বিলোপসাধন, চার্চ ও রাষ্ট্রের ভিতর পারস্পারিক সহযোগিতামূলক সম্পর্কের বিলোপসাধন (সেকুলারাইজেশন অফ স্টেট) ও চার্চের সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা, বুর্জোয়া রাষ্ট্রপালিত আমলাতন্ত্রের বিলোপসাধন ও সরকারি অভিজাততন্ত্রের আভিজাত্যমোচন (যেমন, প্রশাসনের সব স্তরে প্রতিটি পদস্থ সরকারি অফিসার ও আমলাকেই নির্বাচিত হতে হবে, তাঁদের কাজ জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে যে কোনো সময়ে তাঁরা অপসারিত বা পদচ্যুত হতে পারবেন, এবং তাঁদের বেতন মজুরদের বেতনের চেয়ে বেশি হবে না অর্থাৎ, ৬০০০ ফ্রাঙ্ক-এর বেশি হবে না।) বন্ধ-করে-দেওয়া বা পরিত্যক্ত কারখানাগুলিকে শ্রমিকদের সংগঠনগুলির হাতে হস্তান্তর করা, তদ্বারা পুনরায় কাজ চালু করা, মজুরদের বেতনের ব্যবস্থা করা এবং তৎবিষয়ে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করা এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদান ইত্যাদি।
সামাজিক ক্ষেত্রে পদক্ষেপগুলির ভিতর উল্লেখযোগ্য হলো, শিক্ষাদানের জন্যে বেতন নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা ও বিনামূল্যে শিক্ষা ও শিক্ষাসামগ্রীর ব্যবস্থা করা, রুটির কারখানায় রাতের শিফটে কাজের ব্যবস্থার বিলোপ, মালিকপক্ষের নানা অভ্যস্ত তস্করতার (বিভিন্ন অজুহাতে মজুরদের উপর জরিমানা চাপানো এবং বেতন কাটা) উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা ও জরিমানার ব্যবস্থা করা।
কমিউনের সংগঠনে ও কর্মকাণ্ডে নারীদের ভূমিকা ছিলো উল্লেখযোগ্য। কমিউনে নারীরা যে সমস্ত কমিটিতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন সেই কমিটিগুলি নারী অধিকারের প্রশ্নে এবং কমিউন দ্বারা গঠিত জায়মান সমাজে নারীদের অবস্থান কী হবে তা স্থির করার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়েছিলো।থিয়ার্সের সেনাবাহিনীর গোপন তৎপরতার উপর নজরদারির জন্যে কমিউনের অগ্রণী নারীবাহিনীর নেতৄত্বে তৈরি হয়েছিল ভিজিলেন্স কমিটি। নারী কমিউনার্ডদের ভিতর লুই মিচেল বা এলিজাবেথ ড্রিমিট্র্রাইয়ের মতো অসংখ্য নারী কমিউনের জয়যাত্রায়, সংগঠনে এবং অন্তিম প্রতিরোধে সক্রিয়, সাহসী এবং, বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক যোগদান রেখেছিলেন।
কমিউনার্ডদের ভিতর উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছিলেন লুই অগাস্ত ব্লাঙ্কি এবং পিয়ের জোসেফ প্রুধোঁর সমর্থকরা।যদিও, কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের অনুগামী ব্লাঙ্কিবাদীরা শ্রেণিসংগ্রামে অবিশ্বাসী আর প্রুধোঁবাদীদের বিশ্বাস নৈরাজ্যবাদে, কমিউনার্ডরা কিন্তু তাদের নির্মিত বিপজ্জনক রাস্তায় হাঁটেননি। যদিও, মার্কস-এঙ্গেলসের দ্বারা নির্মীয়মাণ জার্মান বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তাঁদের সম্যক পরিচয় ছিল না, তবু সহজাত বৈপ্লবিক স্বভাবের প্রভাবে কমিউনার্ডরা কমিউনকে নির্মাণ করেছেন শ্রমিকশ্রেণির অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিপ্লবী চেতনায় পরিচালিত হয়ে। সে কারণেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক করণীয় কাজ অসামাপ্ত ছিল। তার মধ্যে একটি হল ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সের অর্থ ও পরিচালনভার কমিউনের হস্তান্তর না করা। তবু, ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ঠাট্টা এটাই যে, কার্যক্ষেত্রে, ব্লাঙ্কিবাদ আর প্রুধোঁবাদের তাবৎ তাত্ত্বিক পাঁয়তাড়া রইল একদিকে আর কমিউন চলল উলটো রাস্তায়।
কমিউন সম্পর্কে মার্কস বললেন, কমিউন নিশ্চিতভাবেই শ্রমিক শ্রেণির সরকার, যা কিনা আত্মসাৎকারী শ্রেণির বিরুদ্ধে উৎপাদনকারী শ্রেণির সংগ্রামের ফসল এবং কার্যক্ষেত্রে কীভাবে শ্রমের অর্থনৈতিক বন্ধনমুক্তি ঘটবে তার রাজনৈতিক আকার শেষাবধি আবিষ্কৃত হলো। তিনি আরও বললেন, কমিউন হলো ‘বিশদভাবে উদার ও মুক্ত একটি রাজনৈতিক আকার, যখন কিনা, অতীতের সমস্ত সরকারের আকার ছিলো নির্ভুলভাবে শোষণমূলক।
ফরাসি ও জার্মান বুর্জোয়ার মিলিত হামলা
১৮৭১ সালের ২১ থেকে ২৮শে মে কমিউনের উপর নেমে এলো থিয়ার্সের সেনাবাহিনীর তীব্র আক্রমণ।ইতিমধ্যে, থিয়ার্স সরকার আলোচনার প্রহসন চালিয়ে সময় খরিদ করছিলো, কেননা তখনও থিয়ার্সের যুদ্ধবিধ্বস্ত সেনাবাহিনী হামলা চালানোর ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। থিয়ার্সের সেনা সংগ্রহের প্রচেষ্টাও, শেষ পর্যন্ত, উপহাসযোগ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই, প্যারিসের পতন ঘটানোর জন্যে তার দরকার হলো ফ্রান্সের সেই সেনাদল যারা কিনা সে সময়ে জার্মানির যুদ্ধবন্দী। সুতরাং, থিয়ার্স বিসমার্কের শরণাগত। বিসমার্কও সম্মত, নির্দিষ্ট সংখ্যক যুদ্ধবন্দীকে দেওয়া হবে।কিন্তু শর্ত হলো, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ফ্রান্সের প্রদেয় ৫০০ মিলিয়ন ফ্রাঁ প্যারিসের পতন ঘটা মাত্র, পত্রপাঠ, দিতে হবে।
শুরু হলো, আধুনিক ইতিহাসের বর্বরতম আক্রমণ, প্যারিসবাসীর উপর। আট দিন ধরে শৌর্য, সাহস আর আত্মত্যাগের নতুন দৄষ্টান্ত স্থাপন করলো কমিউন। সভ্যতা আর ন্যায়বিচারের ললিত বানী রক্ত স্রোতে ভাসিয়ে, পুরুষ, নারী, শিশুদের নির্বিচার হত্যার নারকীয় উৎসবে, ফ্রান্সের বুর্জোয়ারাও তৈরি করলো নতুন দৃষ্টান্ত, বিবেকহীন প্রতিহিংসার। প্রতিরোধের যুদ্ধে নিহত হলেন শত শত নারী ও পুরুষ কমিউনার্ড। থিয়ার্সের পাঠানো রক্তপিপাসু শৃগালরা যুদ্ধবন্দী কমিউনার্ড সহ শত শত প্যারিসবাসীকে পের লাসে কবরস্থানের দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করল। যেন বা, অভিজাত বুর্জোয়াদের ঠাণ্ডা মাথায় ঘটানো হত্যার-স্তুপীকৄত লাশের - সে এক পাইকারি বাজার। লাশ সব বয়েসের, সব লিঙ্গের - হত্যার উদ্দেশ্য শুধু হত্যা নয় - একটা শ্রেণিকে নিষ্পিষ্ট করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বন্দীদের উপর অত্যাচার চলছে, চলছে হান্টিং - খুঁজে আনো, কেউ যেন পালাতে না পারে। এমনকি কমিউনের সঙ্গে যাঁরা কোনোভাবে যুক্ত নয় তাঁদেরকেও হত্যা করা হলো।
শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে বিজয়ী ও বিজিত শাসকশ্রেণির যুগলবন্দী চক্রান্ত! জার্মান বুর্জোয়ার সঙ্গে কমিউনের কোনো যুদ্ধ ছিলো না। বরং, জার্মান সেনাবাহিনী প্যারিসের বিষয়ে ‘নিরপেক্ষতা’ ঘোষণা করেছিলো।অন্যদিকে, প্যারিসও শান্তির পূর্বশর্তগুলো লঙ্ঘন করেনি। তাহলে, শ্রমিকশ্রেণির গণহত্যা সংগঠিত করার জন্যে, একযোগে বিজয়ী ও বিজিত শাসকদের এই পরমাশ্চর্য ভ্রাতৄত্বের কারণ কী? এবং এর উৎসই বা কোথায়?
জাতীয় বুর্জোয়া তো বুকের ছাতির মাপে ‘দেশপ্রেমিক’, ‘দেশরক্ষা’র ষুদ্ধ তার ‘মহান যুদ্ধ’! দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে হবে, এখন শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিরোধ বন্ধ থাক, শ্রেণিসংগ্রাম বন্ধ থাক! কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়ার এই ‘দেশপ্রেমিক’ আত্মম্ভরিতা ও গর্জন আসলে কী? তাহলে আক্রমণকারী জার্মান সেনার সঙ্গে ফ্রান্সের আক্রান্ত বুর্জোয়ার এই জোট কি মস্ত ধাপ্পাবাজি নয়? আসলেই তাই! বুর্জোয়ার দেশপ্রেম - প্রকৃতই - রংচংয়ে জোব্বা চড়ানো একটি শূণ্যগর্ভ অতিনাটক, যার উদ্দেশ্য হলো শ্রেণিসংগ্রামকে মুলতুবি রাখা। যখন শ্রেণীসংগ্রাম গৄহযুদ্ধের আকার নেয়, যেমন ফ্রান্সে নিয়েছিলো, জাতীয় বুর্জোয়া তখন এই রংচংয়ে জোব্বাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। শ্রেণির আধিপত্য ও শাসন সংকটের মুখে পরলে তাঁদের ‘দেশপ্রেম’ চুলোয় যায়, এমনকি বিজয়ী ও বিজিত শাসক পরস্পর গলা জড়িয়ে শ্রেণিসংগ্রাম খতম করতে নেমে পড়ে। তখন, জাতীয়তাবাদী জোব্বা নালায় বিসর্জন দিয়ে বুর্জোয়া শাসকরা সীমান্তরহিতভাবে একাত্ম হয়ে ওঠে, কেননা, শ্রমিক শ্রেণির বিজয় অভিযানকে স্তব্ধ করতেই হবে!
কমিউন বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করেছিলো। বুর্জোয়াদের প্রতিহিংসার কারণ সেটাই। আর শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র তৈরি করতে হলে পুরোনো রাষ্ট্রের মেশিনগুলি (সেনাপুলিশ, আইনসভা, বিচারব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি) ধ্বংস করতেই হবে, কেননা, শ্রমিকরাষ্ট্রের আশু ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যের সঙ্গে তা সম্পূর্ণভাবে বেমানান (এঙ্গেলসের ভূমিকা, কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো, জার্মান সংস্করণ, ১৮৭২)।
‘আর এক আরম্ভের জন্যে’
বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে, ‘আর এক আরম্ভের জন্যে’। শ্রমিকশ্রেণি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলেও, নতুন রাষ্ট্রে শ্রেণি শাসনের অবসান হচ্ছে না। স্থাপন হচ্ছে সেই রাষ্ট্র যেখানে কতিপয় বুর্জোয়াদের উপর কর্তৃত্ব থাকবে সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব প্রলেতারিয়েতের। কিন্তু সেই কর্তৃত্ব রাখতে হবে জোরের সঙ্গে। পরিবর্তনকামী, বস্তুত প্রতিবিপ্লবকামী, সংখ্যালঘিষ্ঠ বুর্জোয়াদের জোরের সঙ্গে দাবিয়ে রেখেই শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে হবে, আর সেটাই হবে আশু ভবিষ্যতের জন্যে সাম্প্রতিক ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র - সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব জনতার গণতন্ত্র।লেনিন লিখলেন, ‘It is still necessary to suppress the bourgeoisie and crush their resistance. This was particularly necessary for the Commune; one of the reasons for its defeat was that it did not do this with sufficient determination. The organ of suppression, however, is here the majority of the population, not a minority, as was always the case under slavery, serfdom, and wage slavery’ (রাষ্ট্র ও বিপ্লব)।
লেনিন বললেন, এই প্রলেতারীয় একনায়ককত্ব ছাড়া প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের অস্ত্বিত্ব কল্পনা করা যায় না। কিন্তু, ‘একনায়কত্ব’ শুনে ভীত সন্ত্রস্ত ফিলিস্তিনরা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠছে! ‘একনায়কত্ব’! কম্যুনিস্টরা তাহলে একনায়কত্বের কথা বলছে? বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ঘোষিত ‘গণতন্ত্রের’ নামে অঘোষিত ‘একনায়কত্ব’ চলতে পারে, কিন্তু প্রলেতারীয় রাষ্ট্রে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত ‘শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্ব’ - যদি তা বিপুল সংখ্যক নিপীড়িত জনতার জন্যে প্রকৃত গণতন্ত্রও হয় - চলতে পারেনা। 'সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স' গ্রন্থের ভূমিকায় (১৮৯১ সালের সংস্করণ) এঙ্গেলস এর জবাব দিয়েছিলেন, বেশ তবে, ভদ্র মহোদয়েরা কী জানতে চান এই ‘প্রলেতারীয় একনায়ককত্ব’ জিনিসটা দেখতে কেমন? কমিঊনের দিকে তাকান। ওটাই ছিল প্রলেতারীয় একনায়ককত্ব। লেনিন বললেন, এটাই কমিউনের শিক্ষা।
মার্কস তার 'সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স' গ্রন্থে লিখলেন, ফ্রান্সের তৎকালীন সমাজের সবচেয়ে সেরা উপাদানগুলির প্রকৃত প্রতিনিধি হলো প্যারি কমিউন এবং সেই অর্থে কমিউনের সরকার সত্যিকারের জাতীয়, কিন্তু একই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির সরকার হিসেবে তা শ্রমের বন্ধন মুক্তির বিশ্বজোড়া আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করেছে, এবং সেই সূত্রে তার চরিত্র সোচ্চারভাবে আন্তর্জাতিক। জার্মান সেনাবাহিনী যেমন ফ্রান্সের দুটো প্রদেশকে জার্মান ভূখণ্ডে যুক্ত করেছে, কমিউন তেমনই ফ্রান্সের শ্রমিক জনতাকে সারা বিশ্বের শ্রমিক জনতার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। আর তাই, কমিউনের কামানের তোপধ্বনি সারা বিশ্বের নিদ্রিত গরিব জনতার ঘুম ভাঙ্গিয়েছে, এবং, আজও, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় গরিব জনতার ঘুম ভাঙ্গছে, কোনোদিন তা ভাঙবে ইউরোপ-আমেরিকাতেও।
বুর্জোয়া সরকারগুলির মত ‘আমরা নির্ভুল’ এমন দাবি কখনো করেনি কমিউন। বরং, কমিউন তার সমস্ত বক্তব্য, ঘোষণা ও কাজ সমস্ত জনতার সামনে সর্বসমক্ষে রেখেছে। তাঁরা তাঁদের সমস্ত ঠিক-ভুলের সাক্ষী রেখেছিলেন প্যারিসের শ্রমিক জনতাকে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ‘সরকারি গোপনীয়তা’ তাঁদের ছিল না। প্রলেতারীয় একনায়ককত্ব যে আসলে উন্নততর গণতন্ত্র তা সর্বপ্রথম হাতে কলমে করে দেখিয়েছে কমিউন। তবু, গণতন্ত্রের নামেই বুর্জোয়ারা কামান আর বন্দুক নিয়ে কমিউনের উপর হামলা চালিয়ে শত শত কমিউনার্ডকে খুন করে কমিউনকে মাটিতে মিশিয়েছে। কমিউনকে মাটিতে মিশিয়েছে বটে, কিন্তু শত চেষ্টাতেও বুর্জোয়ারা কমিউনের সেই চিন্তাচেতনাকে মাটিচাপা দিয়ে কবরস্থ করতে পারেনি। সারা বিশ্বজুড়ে আজ মানুষ গাইছে প্যারি কমিউনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ একজন শ্রমিকযোদ্ধার রচিত দুনিয়া কাঁপানো গান, আন্তর্জাতিক (ইন্টারন্যাশনালঃ ‘জাগো জাগো জাগো সর্বহারা, অনশন-বন্দী ক্রীতদাস….’)। সেই গানের ভিতর দিয়ে আজও যুগান্তের ইস্তেহার ছড়িয়ে চলেছে প্যারি কমিউন। দেড়শো বছর পরে আজ সারা বিশ্ব জুড়ে নানা ভাষায় অনুবাদ করে এই গান একই সুরে সমস্বরে গাইছে দেশে দেশে সমস্ত গরিব মানুষ। গানটি লিখেছিলেন একজন কমিউনার্ড, ইউজিন ফাদিয়ার। প্যারি কমিউনের পতনের পর, রক্তের নদী পেরিয়ে তাঁকে প্রথমে ইংল্যান্ড এবং তারপর আমেরিকায় দেশান্তরী হতে হয়। গানটি (বলা ভালো, কবিতাটি) লেখা হয়েছিলো ১৮৭১ সালের জুনে, প্রবাসে।
আজকের পৃথিবীতে ইওরোপ-আমেরিকার কিছু ‘লেবার পার্টি’ বা ‘বামপন্থী দল’ মুখে প্যারি কমিউন আওড়ালেও, বাস্তবে প্যারি কমিউনের ‘উত্তরাধিকার ও শিক্ষা’কে তাঁরা বর্জন করছেন। তাঁরা যে রাজনীতির অনুসরণ করছেন তা হলো ‘কিছু রিলিফ দেওয়ার’ রাজনীতি। তাঁরা শ্রমিক কৃষক গরিব জনতার জন্যে নিয়ে আসেন আধখানা রুটি। গরিব জনতা চীৎকার করে বলে, ‘পুরো রুটিটা কোথায়?’ বুর্জোয়া পার্লামেন্টের ভিতরে ‘বাঘের মতো লড়াই করে’ তাঁরা গরিব জনতার জন্যে নিয়ে আসেন এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া।কিন্তু ক্ষুব্ধ গরিব জনতা বলে, ‘পুরো পোষাকটা কোথায়?’
সংসদসর্বস্বতার (parliametarism) ঘেরাটোপে আটকে পড়ে তাঁরা জনতার জন্যে যা নিয়ে আসেন তা গরিব জনতার শোষণমুক্তি নয়, শ্রমিক কৃষক গরিব জনতার হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা নয়, তা মুক্তিকামী জনতার ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষার হিসেবে নিতান্ত সিকি বা আধুলিও নয়।
অথচ পুঁজিবাদের উদারবাদী বিশ্বায়নের যুগে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে যখন তার কল্যাণ রাষ্ট্রের মুখোশ ক্রমশই আলগা হয়ে খসে খসে পড়ছে, তখন এই ‘কিছু রিলিফ দেওয়ার’ রাজনীতিটাও ধারাবাহিকভাবে তার ক্ষমতা ও জৌলুশ হারাচ্ছে। তাই সার্ধশতবর্ষ পরে প্যারি কমিউনের উত্তরাধিকার (রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল) ও প্যারি কমিউনের শিক্ষা (প্রলেতারিয়েতের একনায়ককত্ব) আজ আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষেও।