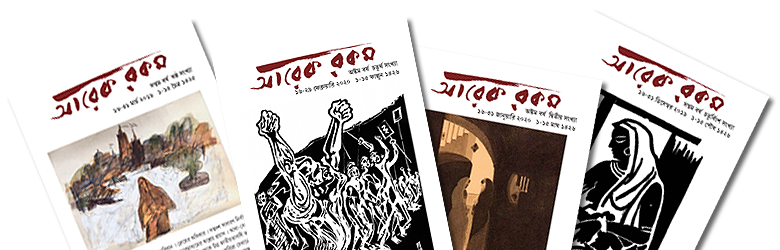আরেক রকম ● নবম বর্ষ অষ্টাদশ সংখ্যা ● ১৬-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ● ১-১৫ আশ্বিন, ১৪২৮
প্রবন্ধ
জিডিপি বৃদ্ধির হার আর মিথ্যার বেসাতি
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
ভারতের চলতি আর্থিক বছর ২০২১-২২-এর প্রথম ত্রৈমাসিকের জিডিপি বা আভ্যন্তরীণ আয়ের প্রাথমিক আনুমানিক হিসাব প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ত্রৈমাসিকে অর্থব্যবস্থা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে ২০.১ শতাংশ। এপ্রিল থেকে জুন - এই তিন মাসে (২০১১-১২ মূল্যের সাপেক্ষে) জিডিপি-র মান গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩২.৩৮ লক্ষ কোটি টাকায়। গত বছর যখন অতিমারির হামলা প্রথম দেশের ওপর এসে পড়ে এবং তড়িঘড়ি ঠিক এই সময় সার্বিক লকডাউন ঘোষণা করে দেওয়া হয় - তখন এই একই ত্রৈমাসিকে জিডিপিতে ধস নামে প্রায় ২৪.৪ শতাংশ।
আজকাল যে রকম প্রায়শই দেখা যায় নানা ধরনের সংবাদ মাধ্যমে, এই ঘোষণার পরেই কিছু সংবাদ মাধ্যম এই নিয়ে ঢোল পিটতে শুরু করে যে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা অতিমারি-জনিত অর্থনৈতিক মন্দার বাইরে এসে গেছে প্রায়, কিছু তথাকথিত বিশেষজ্ঞ অর্থব্যবস্থায় প্রচণ্ড গতিও দেখতে আরম্ভ করেন। শাসক দলের আইটি সেল ও সমর্থকদের দাপাদাপিও শুরু হয়ে যায় ফেসবুক, টুইটার প্রভৃতি বৈদ্যুতিন সমাজ মাধ্যমে। তাদের দাবি - এই রকম ২০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি জাতীয় আয়ে কোনো দিন দেখা যায়নি, অতএব জয় হোক বর্তমান কেন্দ্র সরকারের এবং সরকারের একমাত্র মুখ সেই প্রধানমন্ত্রীর যিনি এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।
প্রথমেই এটা বলে শুরু করা উচিত যে এগুলো সর্বৈব মিথ্যা প্রচার, এর কোনো কিছুর মধ্যেই ছিটেফোঁটাও সত্যতা নেই।
গত বছর প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি-র মান ছিল ২৬.৯৫ লক্ষ কোটি টাকা, ২০১৯-২০-তে এই মান ছিল ৩৫.৬৭ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ চলতি বছরে প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি-র মান ২০১৯-২০-র মানের তুলনায় প্রায় ২.৮ লক্ষ কোটি টাকা কম। ২০১৮-১৯-এর প্রথম ত্রৈমাসিকের জিডিপি-র মানের চেয়েও চলতি আর্থিক বছরের জিডিপি প্রায় ১৪.৬১ লক্ষ কোটি টাকা কম।
সুতরাং, এটা খুবই পরিষ্কার যে জিডিপি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে আপাতত। ২০১৮-১৯ সালের মানের ধারেকাছেও এখনো আসতে পারেনি।
পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে দেখলে এর মধ্যে আশ্চর্যেরও কিছু নেই। গত বছর এই ত্রৈমাসিকে জিডিপি-তে ধস নামার পরিমাণ ছিল ২৪.৪ শতাংশ। তার পরে অর্থব্যবস্থা থেকে সার্বিক লকডাউন উঠে গেছে, যদিও অতিমারির বার বার ফিরে আসার ফলে নিয়ন্ত্রিত লকডাউন এখনও মাঝে মাঝেই হচ্ছে, তাহলেও জিডিপি খানিকটা বেড়ে যাওয়াটা অনেকটাই প্রত্যাশিত। সার্বিক লকডাউন উঠে যাওয়ার পরেও যদি জিডিপি একেবারেই না বাড়ত তাহলে সেটাই খুব দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াত।
কিন্তু এই বৃদ্ধি নিয়ে ঢাক পেটানোর মত কোনো কারণ নেই। খুব সহজ ভাবে ব্যাপারটার ওপরে চোখ রাখা যাক। ধরা যাক, ২০১৯-২০-তে প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপির মান ছিল ১০০ টাকা, গত বছর প্রথম ত্রৈমাসিকে ২৪.৪ শতাংশ কমে যাওয়ার পরে তাহলে জিডিপি-র মান গিয়ে দাঁড়ায় (১০০ - ২৪.৪) = ৭৫.৬০ টাকায়।
ফলত, ২০১৯-২০-র ১০০ টাকার মানে ফিরে যাওয়ার জন্য এই বছর প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি-কে বাড়তে হত ২৪.৪০ টাকা। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে গত বছরে জিডিপি-র মান কমে দাঁড়িয়েছিল ৭৫.৬০ টাকায়। অর্থাৎ, ২০১৯-২০-র প্রথম ত্রৈমাসিকের মানে ফেরত যেতে হলে জিডিপি-র বৃদ্ধির হার হতে হত {(২৪.৪০/৭৫.৬০) x ১০০} = ৩২.৩ শতাংশ।
আসলে বৃদ্ধির হার হয়েছে কত? ২০.১ শতাংশ। অর্থাৎ এই বছর প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি-র বৃদ্ধি হয়েছে {৭৫.৬০ x (২০.১/১০০)} = ১৫.২০ টাকা। একে ৭৫.৬০ টাকার সঙ্গে জুড়ে দিলে দাঁড়ায় ৯০.৮০ টাকা - আমাদের কাল্পনিক অর্থব্যবস্থার চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের জিডিপির মান।
২০১৯-২০ সালে প্রথম ত্রৈমাসিকের ১০০ টাকার কাল্পনিক জিডিপির থেকে বর্তমান বছরের জিডিপি এখনও ৯.২০ টাকা কম। অন্য ভাবে বললে, ২০১৯-২০ প্রথম ত্রৈমাসিকের তুলনায় এই বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের বৃদ্ধির হার ৯.২ শতাংশ কমে গেছে। এই ঋণাত্মক বৃদ্ধির হারই হল আসল সত্য।
জিডিপি-র মূল অংশগুলি হল ব্যক্তিগত ভোগ্যপণ্যের খরচ, সরকারী খরচ, পুঁজির সৃষ্টি বা লগ্নী, আমদানি ও রপ্তানি। এই সব কিছু নিয়েই জিডিপি বা আভ্যন্তরীণ আয়।
সমীকরণ আকারে লিখলে -
আভ্যন্তরীণ আয় = ব্যক্তিগত ভোগ্য খরচ + সরকারী খরচ + পুঁজির লগ্নী + (রপ্তানি - আমদানি)
২০১৯-২০-র তুলনায় দেখলে সরকারী খরচ এবং রপ্তানি বাদে এর প্রতিটিই কমেছে ২০২১-২২-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে। আমদানি কমেছে ৪৬.৮৩ হাজার কোটি টাকা, ব্যক্তিগত ভোগ্য খরচ ২.৪০ লক্ষ কোটি টাকা, পুঁজির লগ্নী কমেছে ২.১১ লক্ষ কোটি টাকা।
অতিমারি আসার আগেও ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় চাহিদার অভাব দেখা দিয়েছিল। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে - চাহিদার অভাব এলে অর্থব্যবস্থায় কী হয়?
সাধারণ মানুষের হাতে ক্রয়ক্ষমতা কমে গেলে চাহিদা কম হয়ে যায়। মানুষের আয় এবং ফলে ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে মানুষ নানা ধরণের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও ভোগ্য পণ্য কেনে, এর ফলে এই সব পণ্যদ্রব্যের চাহিদা অর্থব্যবস্থায় বাড়ে, চাহিদা বাড়লে তখন সাথে সাথে উৎপাদনও বাড়ে। এই ভাবেই অর্থব্যবস্থা এগিয়ে চলে।
কিন্তু এর উলটোটাও ঘটে। চাহিদা কমলে উৎপাদন কমে, উৎপাদন কমলে শ্রমিক ছাঁটাই হয় বা শ্রমিকের বেতন কমে, এর ফলে ক্রয়ক্ষমতা আরো হ্রাস পায়, ফলে তখন আরো উৎপাদন কমে যেতে থাকে। এই কারণেই অর্থব্যবস্থায় চাহিদা এবং ক্রয়ক্ষমতা এত গুরুত্বপূর্ণ।
প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলা যায়, এই চাহিদার ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা অতিমারির আগেও দেখা গিয়েছিল, পরিসংখ্যান বলছে অর্থব্যবস্থা সেই প্রবণতা থেকে এখনও মুক্তি পায় নি, অতিমারি এই প্রবণতাকে আরও প্রবল করে তুলেছে। এক দিকে ভোগ্যপণ্যের চাহিদার অভাব, আর এক দিকে পুঁজির লগ্নীর অভাব এই সমস্যাকেই আরো সুস্পষ্ট করে তুলেছে। এরই ফল জিডিপি-র অধিকাংশ উপাদান এখনও ২০১৮-র স্তরেই রয়ে গেছে।
এই অবস্থায় প্রথম ত্রৈমাসিকের ২০.১ শতাংশ বৃদ্ধির হার নিয়ে ঢোল পেটানোকে ভাঁওতাবাজি বললেও খুব কমই বলা হয়।
যদি অর্থব্যবস্থার আলাদা আলাদা সেক্টরের উৎপাদন মূল্য দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে গত এক বছরে কৃষি, অরণ্য ও মৎস্য সম্পদ সব চাইতে ভাল উৎপাদন করেছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, জলসম্পদ এবং অন্যান্য উপযোগী পরিষেবার উৎপাদন মূল্যও বেড়েছে। বাকি সমস্ত সেক্টরে গত বছর অতিমারির ফলে যে ধস নেমেছিল তার থেকে কোনো সেক্টরই এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি।
যদি ২০১৯-২০-র প্রথম ত্রৈমাসিকের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে ম্যানুফ্যাকচারিং ২৩.৭০ হাজার কোটি টাকা কম উৎপাদন করেছে ২০২১-২২-র প্রথম ত্রৈমাসিকে, খনি সম্পর্কিত উৎপাদন ১.৪৭ হাজার কোটি টাকা কম, নির্মাণ সেক্টরে ৩৮.৮৪ হাজার কোটি টাকা কম উৎপাদন। সব চাইতে দুশ্চিন্তার পরিসংখ্যান হোটেল, আভ্যন্তরীণ ব্যবসা, পরিবহন, যোগাযোগ এবং ব্রডকাস্টিং জাতীয় পরিষেবাগুলিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার উৎপাদন কম - ২০১৯-২০-র নিরিখে।
অথচ এই পরিষেবা সেক্টরগুলিতেই দেশের বেশির ভাগ মানুষ কাজ করেন। এই সব সেক্টরের কর্মনিযুক্তির ধরনও অনিয়মিত, এই কর্মীরা বেশির ভাগ নিয়মিত চাকরির যে সব সুবিধা থাকে (পেনসন, মেডিকেল এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক সুবিধা) তার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। অতিমারিতে চাকরি চলে গেলে বা বেতন হঠাৎ খুব কম হয়ে গেলে এই সব সেক্টরে কর্মরত মানুষদের অসহায় হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।
এই রকম চিন্তাজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দরকার ছিল কর্মহারা মানুষদের হাতে ক্রয়ক্ষমতা তুলে দেওয়ার। তাতে সেই মানুষেরাও সুস্থ ভাবে বাঁচতে পারত, আর অর্থব্যবস্থার এই ক্রমহ্রাসমান চাহিদার সমস্যারও অনেকটাই সমাধান পাওয়া যেত।
কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার সেই পথের ধারেকাছেও যাচ্ছে না, ক্রমাগত মিথ্যা প্রচার আর স্তোকবাক্য দিয়ে চলেছে গত এক বছর ধরে, এখন ঘোষণা করে সরকারী সম্পত্তি লিজে দেওয়ারও প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়েছে। যেটুকু সমাজকল্যাণমূলক খরচ করা হয়েছে বিগত এক বছরে তা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। অর্থব্যবস্থার হাল যে একেবারেই ভাল নয় প্রথম ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে প্রায়।
এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের এই ২০.১ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির মিথ্যা ঢাক পেটানোর আড়ম্বর খুবই দৃষ্টিকটু এবং অনৈতিক।