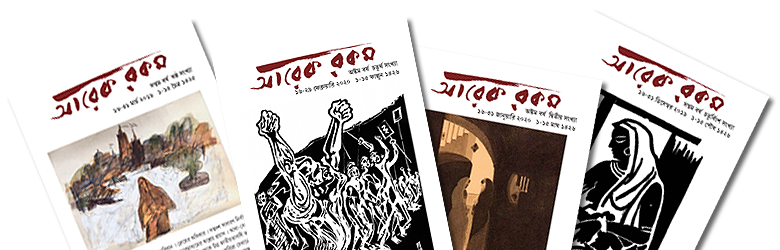আরেক রকম ● নবম বর্ষ অষ্টাদশ সংখ্যা ● ১৬-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ● ১-১৫ আশ্বিন, ১৪২৮
প্রবন্ধ
বাংলাদেশের কবিতা
মজিদ মাহমুদ
কাকে বলব বাংলাদেশি কবিতা? বাংলাদেশ তো আগেও ছিল। ইতিহাস যখন তৈরি হয়নি তখনো। এমনকি ভাষা তৈরির আগেও বাংলাদেশ এখানেই ছিল। বাংলা মানে এখন বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা তৈরি হওয়ার আগে বাংলা বলতে অন্য কিছু বোঝাতো। হতে পারে নিচু-জলাভূমি। হতে পারে কোনো দেবতার নাম। কিংবা এখানকার লোকেরা দশফুট উঁচু আর বিশফুট প্রস্থ আল নির্মাণ করতো। আজ আর তার কোনো আলাদা অর্থ নেই। আজ বাংলা মানে বাংলা ভাষা। তাই মোটা দাগে বলা যায়, বাংলা কবিতা মানে বাংলাদেশি কবিতা। তবে রাজনীতিকভাবে এই সামান্যিকরণের কোনো অর্থ নেই। ইতিহাস কিংবা ভূগোল আলোচনার স্বার্থে হয়তো বাংলা ছিল, পূর্ব-বাংলা ছিল, বাংলাদেশও হয়তো ছিল; কিন্তু স্বাধীন বাংলা ছিল না। বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমল, বিদ্রোহী বাংলা রাজনৈতিক ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্য হলেও ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের আগে পুরোপুরী কেন্দ্রের শাসনমুক্ত ছিল না। কেন্দ্রের শাসনমুক্ত বাংলা অঞ্চলকেই আমরা আজ বাংলাদেশ বলি। বাংলাদেশের বাইরেও বাংলা আছে; বাংলা সাহিত্য আছে; বাঙালির সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে; কিন্তু কেন্দ্রের শাসনমুক্ত নেই। তাই বলে দেশকে যেভাবে বিভাজন করা সম্ভব, ভূগোল ও মাটিকে যে ভাবে বিভাজন করা সম্ভব ভাষাকে, সাহিত্যকে কি সেভাবে বিভাজন করা সম্ভব? বাংলাভাষি যেখানেই আছে, বাংলা সাহিত্য যারা রচনা করছেন, বাংলা কবিতা যারা পড়ছেন তাদের কিভাবে শ্রেণিকরণ করা সম্ভব? তবে কবিতার বিষয় যখন ভূগোল ও রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি তখন হয়তো কবিতায় মোটা দাগে একটি শ্রেণিকরণ সম্ভব; কিন্তু কবিতা-সাহিত্য যখন প্রেম ভালোবাসা, রিরংসা-ক্ষোভ, বাৎসল্য মানবিকতা তখন আমরা কবিতাকে কীভাবে আলাদা করব। কেবল স্বভাষা নয়, পরভাষার সাহিত্যকেও তখন আলাদা করা সম্ভব নয়। তবু আমার এই আলোচনা বাংলাদেশী কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই সর্বাগ্রে বিষয়টি খোলাসা করে নিতে চাই।
হুট করে বাংলাদেশের কবিতা আলোচনার ঝুঁকি রয়েছে। রয়েছে ভুল বুঝবার অবকাশ। তবু কাল এবং স্থান আমাদের যেভাবে বেঁধে রাখে। ইচ্ছে করলেই আমরা তার কবল থেকে বের হতে পারি না। আমরা যেখানে যাই ভাষা ও স্বদেশ আমাদের সঙ্গে থাকে। ভাষা মানে আমার পরিচিত শব্দ সম্ভার; যার প্রতিটি স্বর ও বাক্য আমার চেনা-যা একই ভাষাভাষি মানুষের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ গড়ে তোলে। ভাষার মাধ্যমেই আমরা নিজেকে অন্যের কাছে মেলে ধরতে পারি। আবার আমরা যেখানে জন্মগ্রহণ করি-তার আলো বাতাস ফুল পাখি নদী মাঠ-যার সবকিছু নিয়ে আমাদের প্রতিবেশ-আমাদের চিরচেনা। একজন কবি যখন তার অনুভূতিসমূহের রূপদান করেন-তখন মূলত তার ভাষা ও প্রতিবেশ ভিড় করে চলে আসে-যাকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। আর এভাবেই স্থান ও কাল ভাষা ও অনুভূতি একাকার হয়ে ওঠে। গভীরভাবে লক্ষ করলে অবশ্যই বোঝা সম্ভব-এই কবিতাটি কোন কালে এবং কোন স্থানে লেখা হয়েছিল। সুতরাং, এই বিবেচনায় বাংলাদেশের কবিতাকে একটি আলাদা রূপকল্প হিসাবে বিবেচনা করা মোটেও অসংগত নয়। তবে বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্য প্রান্তরের ভাষা ও জাতিসমূহ থেকে ব্যতিক্রম। কারণ বাংলাদেশ বলতে আমরা যে ভূখণ্ডকে বুঝে থাকি-বাংলাভাষার বিস্তৃতি তারচেয়ে ব্যাপক। বাংলাদেশের বাইরেও প্রায় সমান সংখ্যক বাঙালি বসবাস করেন, সাহিত্য রচনা করেন-যা বাংলাভাষী পাঠকদের পাঠ-রসনা তৃপ্ত করে। কিন্তু এর সব রচনাকে তো আমরা বাংলাদেশি রচনা বলতে পারি না। গঙ্গা-যমুনার ধারা যেমন পাশাপাশি বইলেও পানির ধারা ও জলের স্রোত মিশ খায় না; তেমনি বাংলাদেশের বাইরে বাংলা ভাষার রচনার রয়েছে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য।
তবে অবশ্য এ কথা আমাকে মানতে হচ্ছে। বাংলাদেশের কবিতা এবং বাংলাভাষী কবিতা অবশ্যই একটি রাজনৈতিক প্রকল্প। কবিতাকে একটি নির্বিষ নান্দনিক কর্মকাণ্ড মনে হলেও এর অন্তর্প্রবাহে সর্বদা রাজনীতির ফল্গুধারা প্রবাহিত। ব্যাপক অর্থে রাজনীতি ও ভূগোলের বাইরে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ সেটিও গড়ে ওঠে নিজ ভূমির উপরে। কেবল তাই নয়, আন্তর্জাতিকতাবাদের আড়ালে দুর্বল জাতীয়তাবাদ সব সময় নিগৃহীত হয়। ফলে যখন আমরা বাংলাদেশি কবিতা বলি তখন এমন একটা ভূখণ্ডকে বুঝে থাকি যার সাধারণ বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের বাইরে বাংলাভাষি জনগোষ্ঠীর চেয়ে আলাদা। আলাদা রাজনীতি ও সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস ও স্বরভঙ্গি এমনকি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানও গভীরভাবে এক নয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ-উপনিবেশের অবসানের আগে ইতিহাসের দীর্ঘ সময় ধরে বাংলা ভূখণ্ড প্রায় অবিচ্ছিন্ন ছিল। এমনকি মোগল ও ব্রিটিশ শাসনের সুবাদে বৃহত্তর ভারতবর্ষের ধারণাটিও সুসংবদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং এই সময়ের আগে পর্যন্ত বাংলা কবিতা মানেই বাংলাদেশি কবিতা। অর্থাৎ চল্লিশের দশক পর্যন্ত বাংলা কবিতাকে একটি অখণ্ড ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বিবেচনা করা সঙ্গত। পূর্ব-পশ্চিম দিয়ে এই কবিতাকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ভারত বিভাজনের ভেতর দিয়ে বাংলা কবিতায় একটি স্থায়ী বিভাজন রেখার সৃষ্টি যুগপৎ বাংলা কবিতাকে খণ্ডিত ও বৈচিত্র্যময় করেছে।
ভারত বিভাজনের আগে বাংলা কবিতার সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। গ্রহণ ও বর্জনের নানা বিতর্ক সত্তে¡ও বাংলা ভাষার কবিতাকে তাঁরা আজো এ সূত্রে গেঁথে রেখেছে। কেবল রবীন্দ্র-নজরুল নয় তাঁর আগের সব কবিতা-ই বাংলাদেশের কবিতা। ভৌগোলিক অর্থেও যেমন সত্য, রাজনৈতিক অর্থেও তেমন সত্য। কিন্তু ভারত বিভাজনের পরে সেই অখণ্ডউত্তরাধিকার বাংলা কবিতা আর ধরে রাখতে পারেনি। সুতরাং বাংলাদেশের বাইরে যে বাংলা কবিতা তা ভাষার দিক থেকে একই উত্তরাধিকার হলেও রাজনৈতিক ও ভৌগোলিকভাবে সম্পূর্ণ আলাদা। বলা চলে একই ভাষার বিদেশি কবিতা। যেমন স্পেনের কবিতা আর ল্যাতিন আমেরিকার স্প্যানিশ কবিতা। কিংবা আমেরিকা আর ইংল্যান্ডের কবিতার মধ্যে যতটুকু ফারাক; বাংলাদেশের বাইরে বাংলা কবিতা ঠিক ততটুকু পার্থক্য ধারণ করে।
তাহলে কোন সময়ের কবিতাকে আমরা বাংলাদেশের কবিতা বলব? আগেই বলেছি, ভারত বিভাজনের ফলে বাংলাভাষী ভূখণ্ডের অঙ্গচ্ছেদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কবিতার সূচনা হয়। যদিও ১৯৪৭ সালেই বাংলাদেশের আলাদা অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়নি। এই ভূখণ্ড তখন ছিল বৃহত্তর পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যেহেতু পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের সঙ্গে এর ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল হাজার মাইলেরও বেশি; ভাষা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন-ধর্ম ছাড়া আর কোনো জাতিগত ঐক্য ছিল না একই দেশের দুটি অংশে। সুতরাং ভারত বিভাজনের শুরু থেকে এখনকার বাংলাদেশ ভূখণ্ডটি পূর্ববাংলা নামে তখন অখণ্ড অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান ছিল। এ ক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আহসানের কবিতা ‘আমার পূর্ববাংলা’ দ্রষ্টব্য। ব্রিটিশরাজের ভারত ত্যাগের পরে পূর্ববাংলা এমনই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল যে উর্দুভাষি অঞ্চলকে সে কিছুতেই নিজের বলে ভাবতে পারছিল না। বাংলাভাষি ভারত অধিকৃত ‘পশ্চিমবঙ্গ’-এর সঙ্গে মিলিত হবার কোনো উপায় ছিল না। এমনকি আজকের দিনে বাংলাভাষি দুই অংশের মধ্যে যে যোগাযোগ তৈরি হয়েছে-উর্দু ও হিন্দি বলয়ের দুই বৈরি রাজনৈতিক সরকারের আমলে তা সম্ভব ছিল না। এভাবেই সাতচল্লিশ পরবর্তী বাংলাদেশ এক পরম বিচ্ছিন্নতা নিয়ে নিজের মধ্যে সংগঠিত হয়ে উঠছিল। আর এই বিচ্ছন্নতার বোবা কান্না, না পাওয়ার যন্ত্রণা; অবশেষে প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠার ভাষা কবিতায় রূপ নিতে শুরু করে। এভাবেই বাংলা কবিতা বাংলাদেশের কবিতায় পরিণত হয়। এর একটি বিভাজন রেখা আগেই- ব্রিটিশ আমলে শুরু হয়েছিল। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের চেষ্টা প্রধানত বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান মানসকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছিল। যদিও এই বিভাজন ছিল ব্রিটিশ লর্ডের কারসাজি-বিভাজনের মাধ্যমে শাসন করা; তবু হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থের এখানে পার্থক্য ছিল বিস্তর। সে-সময়ে পূর্ববঙ্গ ছিল মূলত কলকাতার বাবু শ্রেণিকে খাদ্য যোগানোর ভুখণ্ড। সুতরাং বাবুদের চাওয়া আর পূর্ববঙ্গের উঠতি কৃষক শ্রেণির চাওয়ার মিলের ঐক্য ছিল না। বাবুরা ভাবছিলেন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হলে তাদের সরবরাহের পথ বাঁধাগ্রস্ত হবে আর পূর্ববঙ্গের কৃষক ঠিক এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিজেদের স্বনির্ভরতার স্বপ্ন দেখছিলেন। বঙ্গভঙ্গ যে একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে ১৯৪৭ সালে। কারণ যে শ্রেণি তখন বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন ঠিক সেই শ্রেণিই চল্লিশ বছর পরে তার পক্ষে মত দিচ্ছে। তাই এই সময়ে রচিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের কবিতা সবটাই বাংলাদেশের কবিতার পূর্বসূরিত্ব দাবি করতে পারেনি।
তবে বিশ শতকের বিশের দশকে বিশেষ করে নজরুলের হাতে যে ব্রিটিশবিরোধী কবিতার জন্ম হয়েছিল ভারত বিভাজনের পরেও বাংলাদেশের কবিদের সেই কবিতাকে অনেক দিন অবলম্বন করতে হয়েছিল। কারণ ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও পূর্ববাংলা নতুন করে ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় চলে আসে। কেবল ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হওয়া এবং সেই সুবাদে বাংলাদেশকে বরণ করতে হয় তার পূর্বপাকিস্তানিত্ব। কিন্তু বাংলাদেশ তার একটি পরিচয়ের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেনি। পশ্চাতে দুশ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতা তাকে এখানেও বরণ করে নিতে হয়। নতুন করে শুরু হয় তার স্বাধিকার আন্দোলন। পাকিস্তানে বছর না পেরুতেই ভাষার দাবিতে তাকে রাজপথে নেমে আসতে হয়। ভারত নিয়ন্ত্রিত বাংলাভাষি অপর অংশকে ঠিক একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়নি। হিন্দির আধিপত্য মেনেই তারা বাংলাকে একটি আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়।
বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আন্দোলন ছিল তার জন্মলগ্ন থেকে। এই ভাষাটির প্রতি সেই শুরু থেকেই উচ্চবিত্ত ও শাসক শ্রেণি কুপিত ছিল। অপভ্রংশের কাল থেকে সংস্কৃত বলয়ের কোপানলে পড়তে হয়েছিল এই ভাষা ও সাহিত্যের ব্যবহারজীবীদের। ভয় দেখানো হয়েছিল এই ভাষায় কেউ রামের চরিত্র অষ্টাদশ পুরাণ রচনা কিংবা শ্রবণ করলে তাকে রৌরব নরকে পুড়তে হবে। এমনকি মধ্যযুগের সুলতানী আমলে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই ভাষার কিছু পৃষ্ঠপোষকতা করা হলেও আশরাফ মুসলমানরা তা সুনজরে দেখেননি। এ ভাষা ব্যবহারকারীদের নিম্ন মর্যাদার বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এই ভাষার বদলে যারা আরবি ফারসি ব্যবহার করেছেন- তারাই সমাজের মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। এ সব হুজ্জতি দেখে মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম এই আগাছাদের কসে গাল দিয়েছিলেন। বাংলাভাষার বিরোধিতার এই কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না; কারণ এই ভাষা ছিল সাধারণ জনগণের মুখের ভাষা এবং একমাত্র ব্যবহার্য ভাষা। বাংলাভাষাকে উচ্চবিত্তের মানুষ কখনো তাদের নিজের ভাষা বলে সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি। আর শাসক শ্রেণি এই ভাষাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে গণমানুষের মুখে ভাষা হিসাবে, তাদের শাসন করবার কৌশলগত কারণে। সুতরাং বাংলাভাষার জন্মলগ্নে মধ্যে যেমন রয়েছে সমাজের উচ্চবিত্তের অবজ্ঞা তেমনি এর টিকে থাকের জন্য রয়েছে নানা বিদ্রোহের উপাদান। এই ভাষা বিদ্রোহ হারিয়ে ফেললে তার টিকে থাকা এবং ছড়িয়ে যাবার মধ্যে একটি বিলোপনের আশঙ্কা থেকে যায়। ‘৪৭-এ বাংলা বিভাজনের ফলে পূর্ববাংলা তার বিদ্রোহ উপাদান পুরোটাই অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি ভাষা ও রাজনীতির সঙ্গে তার বিচ্ছেদের ট্র্যাজেডির সূত্রপাত হয়। একই ভাষার দুটিপথ দুদিকে বেঁকে যেতে বাধ্য হয়। ভারত বিভাজনের অব্যবহিত আগেই চল্লিশের কবিদের দ্বারা এই বিভাজনের সূত্রপাত হয়। চল্লিশের প্রধান কবিরা ছিলেন মূলত আদর্শবাদী। তিরিশের কবিদের হতাশা ও নিখিলনাস্তি থেকে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছিলেন; এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন ইতিবাচক জীবনবাদিতায়। একটি ক্ষুধামুক্ত সুষমবণ্টন ও শোষণহীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন তারা। তবে তাদের দার্শনিকভিত্তি এক রকম ছিল না। এই সময়ের কবিতায় মার্কসবাদী বীক্ষা প্রবল হলেও পাকিস্তান যেহেতু ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে এবং ইসলাম ধর্মের সারমর্মে যেহেতু মানবিকতা এবং স্রষ্টার দৃষ্টিতে যেহেতু সকল মানুষ সমান সেহেতু অনেকেই ইসলামের সাম্যবাদে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন-এ ক্ষেত্রে আমরা ফররুখ আহমদের নাম বলতে পারি। ফররুখ ছিলেন চল্লিশ দশকের এক শক্তিশালী কবি। তাঁর বিশ্বাস ছিল ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা পেলে একটি ক্ষুধামুক্ত শোষণহীন সমাজের জন্ম হবে। আর তাঁর এ বিশ্বাসের মূলে ছিল চল্লিশ দশকের পাকিস্তান রাষ্ট্রপরিকল্পনা। যদিও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আখেরে বাঙালি অধ্যুষিত পূর্বপাকিস্তানের জন্য ভালো হয়নি। ফররুখের স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কবিতায় সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তাঁর ক্ষমতা অনিন্দনীয় হলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় বাংলাদেশোত্তর তাঁর প্রান্তিক অবস্থান নির্ধারিত হয়ে আছে। বিপরীত দিকে এসময়ের কবিতায় সুভাষ মুখোপধ্যায়, সুকান্ত, গোলাম কুদ্দুস মার্কসবাদী শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় কবিতাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। তাদের কাব্যিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলেও সমগ্র বাংলা কবিতায় ইতিবাচক চেতনার ধারক হিসাবে বিবেচিত হন। এ-সময়ের অন্য কবিদের আলোচনা আমরা এখানে প্রাসঙ্গিক হিসাবে দেখছি না। বরং সৈয়দ আলী আহসান, আহসান হাবীব, কিছুটা আবুল হোসেন- যাঁরা অখণ্ড বাংলাপর্বে তাদের কাব্যিক যাত্রা শুরু করলেও প্রথম বাংলাদেশি কবিতার ভিত্তি নির্মাণে জোরালো ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসেন। এই সব কবি কলকাতা কেন্দ্রিক তাদের কাব্যজীবন শুরু করলেও দেশ বিভাগের পর ঢাকাকে বাংলা সাহিত্যের রাজধানী পরিণত করার ক্ষেত্রে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।
প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ নিজস্ব কবিদের খুঁজে পায় পঞ্চাশের দশকে। ঢাকা যদিও তখনো প্রাদেশিক রাজধানী; কিন্তু বাংলা সাহিত্যের একক রাজধানী হিসাবে তার চলেছে রীতিমতো প্রস্তুতি। জিন্নাহ’র উর্দু রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার মধ্যদিয়ে ঢাকা কুপিত হয়ে ওঠে; এবং এককভাবে বাংলার দাবিতে, বাংলাভাষার চর্চায় ভাষাকেন্দ্রিক এক জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ লাভ ত্বরান্বিত হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একচক্ষু নীতির ফলে বাঙালি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই সময়ের কবিতা তা-ই ভাষা আন্দোলন, স্বদেশ চেতনার দ্রোহ ধারণ করতে থাকে। পঞ্চাশে ঢাকা কেন্দ্রিক কবিদের সঙ্গে বাংলাভাষী ভারতীয় কবিদের চেতনায় মিল ছিল না। ভাষাকে কেন্দ্র করে জীবনদানের ঘটনা বাঙালির সমবায়ী দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো বেগবান করে তোলে। যদিও এ-সময়ের কবিরা আধুনিক নগরায়ন, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ বিবিক্তি দ্বারা তাড়িত হন; তবু দ্রোহ ও প্রতিবাদ এখানকার কবিতাকে আলাদা করে দেয়। সবচেয়ে বড় এই সময়টিতে বাংলাদেশ বেশ কিছু প্রবিভাবান কবির জন্ম দেয়- যা মূলত সহযোগিতা করে বাংলাদেশি কবিতার একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে দিতে। শামসুর রাহমান এবং আল মাহমুদ বাংলাদেশের কবিতার দুই বিশালপর্বকে একত্রে জুড়ে দিতে সহযোগিতা করেন। শামসুর রাহমান ধারণ করে নতুন গড়ে ওঠা মহানগর ঢাকার চরিত্র-চিত্রণ, ক্ষোভ, দুঃখ, একাকিত্ব- এমনকি ঢাকা কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের সংগ্রাম, স্বাধিকার আন্দোলনের বাণী। আল মাহমুদ ফেলে আসা গ্রাম- নগরে গ্রাম ঢুকে যাওয়ার গল্প। দুজনের কবিতায় বাংলাদেশটা বেশ রসিয়ে বসে। কোনো তুলনা ছাড়াই বলা যাবে তাদের কবিতার কণ্ঠস্বর কোনোভাবেই বাংলাভাষি অন্য অঞ্চলের কবিতার সঙ্গে মিলে যাবে না। তাঁরা ছাড়াও এ সময়ের বাংলা কবিতাকে ঋদ্ধি দিয়েছিলেন, আবদুল গণি হাজারী, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দিন প্রমুখ।
পঞ্চাশ দশকের এই আন্দোলন পুরো ষাটের দশক পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছিল। ষাটের কবিরা বাংলাদেশের কবিতার উপর বেশ পোক্ত হয়ে বসেছিলেন। দেশজ উপাদান আত্মস্থ করে বিশ্বের দিকে তারা তাদের ডালপালা মেলে দিতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশের কবিতার সকল দীনতা ঘুচিয়ে দিয়েছিল ষাটের কবিরা।