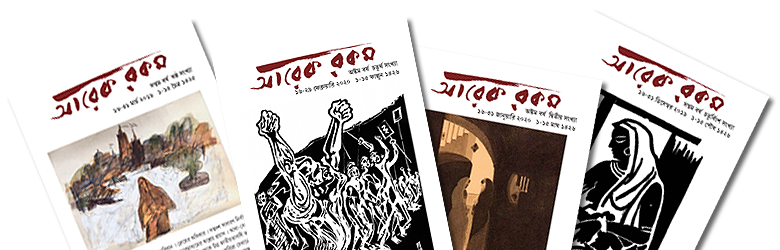আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা ● ১৬-৩০ এপ্রিল, ২০২৫ ● ১-১৫ বৈশাখ, ১৪৩২
সম্পাদকীয়
দুয়ারে আতঙ্ক
আতঙ্ক-আশঙ্কা বিরাজমান। সপ্তাহজুড়ে চলেছে অবাধ লুটপাট। ঘরবাড়ি দোকান-বাজারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েক শ’ পরিবার একবস্ত্রে ভিটেমাটি ছেড়েছুড়ে নিজের দেশেই শরণার্থী। কেউ নিজের রাজ্যে কেউ হয়তো বা পড়শি রাজ্যে।
মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি এলাকায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগ, পুলিশ নিষ্ক্রিয়। প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে ব্যর্থ। এমনকি আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করার কথাও ভাবেনি। ফলাফল, - অবাধ লুটতরাজ ও তিনজনের মৃত্যু। কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই শাসকদল রামনবমী হনুমান জয়ন্তী উদ্যাপনের ব্যস্ততা শেষে মৃতদের ধর্ম খুঁজে বেড়াচ্ছে। হিন্দু না মুসলমান - খুঁজে চলেছে রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসকদল। তারা দাঙ্গাকারী হত্যাকারীদের খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে জানা যায়নি। স্থানীয়দের মতে, - বামপন্থী পরিবারের দুই সদস্যকে বাড়ি থেকে বের করে এনে হত্যা করা হয়েছে।
আদালতের নির্দেশে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের পর রাজ্য সরকার নড়েচড়ে বসেছে। পুলিশের সর্বোচ্চ আধিকারিক ঘটনাস্থলে ঘাঁটি গেড়েছেন। সাময়িকভাবে ইন্টারনেটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। বলা হয়েছে বাইরে থেকে উস্কানিমূলক বার্তা আসা বন্ধ করতেই এমন সিদ্ধান্ত। পক্ষান্তরে ধারণা করা হচ্ছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার যে সব জায়গায় শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে তার প্রকৃত সত্য বাইরের পৃথিবীতে প্রচার বন্ধ করার জন্যই এমন বন্দোবস্ত।
এই সাম্প্রতিক ঘটনার আপাত নেপথ্যে রয়েছে নতুন ওয়াকফ আইন। ওয়াকফ মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। স্বভাবতই ইসলামের আগমনের পরে ভারতে ওয়াকফ গঠিত হয়। সুলতানি আমলে, মোঘল আমলে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাবে, মুলতানে, নিজামশাহের আমলে অবিভক্ত অন্ধ্রে, নবাবশাহী আমলে বাংলায় এবং অন্যান্য রাজ্যে বহু ওয়াকফ সম্পত্তি গঠিত হয়। এইসব ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবহৃত হতো দাতব্যমূলক কাজে এবং মুসলমান জনগণের সেবায়। ঐ অর্থে তৈরি করা হত মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কবরখানা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র। সেই ধারা এখনও অব্যাহত। মোঘল শাসনকালে 'ফতোয়াই-ই-আলমগীরি' মাধ্যমে ওয়াকফ সংক্রান্ত আইন সহ সমস্ত মুসলিম ধর্মীয় আইনগুলিকে সংহিতাবদ্ধ করা হয়। ব্রিটিশ যুগে প্রিভি কাউন্সিলের সময়কাল পর্যন্ত এই পদ্ধতি বৈধ ছিল। ব্রিটিশ ভারতে, মুসলিম ওয়াকফ বৈধকরণ আইন ১৯১৩, মুসলিম ওয়াকফ আইন ১৯২৩ প্রচলিত ছিল। এর পরে বেঙ্গল ওয়াকফ আইন, ১৯৩৪ চালু হয়। দেশ স্বাধীন হলে ভারত সরকার ঐ আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে ১৯৫৪ সালে ওয়াকফ আইন তৈরি করে। পরে ১৯৫৯, ১৯৬৪, ১৯৬৯, ১৯৮৪ সালে কিছু কিছু সংশোধন করা হয়। পরে যৌথ সংসদীয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৯৫ সালে নতুনভাবে ওয়াকফ আইন তৈরি হয়। বর্তমানে এই আইনকেই ‘প্রিন্সিপাল আইন’ বলা হয়। ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদীয় সিলেক্ট কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ওই আইনে বেশ কিছু সংশোধনী যুক্ত করে। ১৯৫৪ এবং ১৯৯৫ সালের আইনের ভিত্তিতেই রাজ্যে রাজ্যে ওয়াকফ বোর্ড গঠিত হয়। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৫ সালের আইনের উপর ৪০টির বেশি সংশোধনী এনেছে।
এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে লোকসভা ও রাজ্যসভায় সুদীর্ঘ আলোচনার পর নতুন সংশোধনী বিল সংসদীয় সংখ্যাধিক্যের সুবাদে ভোটাভুটির মাধ্যমে পাস হয়। এবং অতি দ্রুত রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরদানের পর নতুন আইন স্বীকৃত হয়।
ওয়াকফ আইন (WAQF Act)-এর বদলে নতুন আইনের নাম হয়েছে ''Unified Wakf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act''। বিলের ১৩(২এ) অংশে বলা হয়েছে বোহরা সম্প্রদায় এবং আফগানি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব রাখতে পৃথক পৃথক বোর্ড করা হবে। অর্থাৎ বিভাজনের দৃষ্টিভঙ্গি হতে মুসলিম জনসাধারণকে ভাগ করতে চাওয়া হয়েছে। বর্তমান বোর্ডগুলি সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কাজ করে।
নতুন আইন অনুযায়ী কেবলমাত্র একজন মুসলিম যিনি প্রমাণ করতে পারবেন যে তিনি কমপক্ষে পাঁচ বছর ধরে ইসলাম ধর্ম পালন করছেন তবেই তিনি ওয়াকফ-এর জন্য সম্পত্তি দান করতে পারবেন। ১৯৯৫ সালের আইনে বলা ছিল যে কোনও ব্যক্তি তা করতে পারেন। এটা তার সাংবিধানিক অধিকার। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই অধিকারকে খর্ব করতে চাওয়া হয়েছে যাতে অমুসলিমরা কেউ ওয়াকফে সম্পত্তি দান না করেন। সংশোধিত আইনের ফলে মুসলিম অমুসলিম ভ্রাতৃত্বের এই প্রকাশ আর সম্ভব হবে না।
১৯৯৫ সালের আইনে বলা ছিল কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলের সদস্যরা মুসলিম সম্প্রদায়েরই হবেন। অথচ নতুন আইনে ওয়াকফ কাউন্সিলে অন্তত দু’জন অমুসলিম থাকবেন। অমুসলিমদের ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনা থেকে নিষিদ্ধ করার ইসলামিক আদেশ সত্ত্বেও, সংশোধিত আইনে ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি মুসলমানদের ধর্ম পালনের সাংবিধানিক অধিকারের উপর আক্রমণ।
১৯৯৫-এর আইনে বলা ছিল ওয়াকফ সম্পত্তি বিষয়ে যে সব ট্রাইবুনাল গঠিত হবে সেখানে মুসলিম আইন সম্পর্কে দক্ষতা আছে এমন ব্যক্তিকে রাখতেই হবে। নতুন আইনে এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।
নতুন আইনে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলে দু’জন মহিলা সদস্য থাকবেন। অথচ ১৯৯৫ সালের আইনে বলা আছে ''at least two women members'' অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের আইনে দুইয়ের বেশি মহিলা সদস্য থাকারও সুযোগ রাখা ছিল। এখন বলা হচ্ছে দু’জন থাকবেন। এটা কেন?
আগের আইন মোতাবেক রাজ্য সরকার ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য হিসাবে সাংসদ ও বিধায়ক ক্ষেত্র থেকে মুসলিম সাংসদ ও বিধায়কদের মনোনীত করত। বর্তমান আইনে বলা হয়েছে মুসলিম হতে হবে এমন নয়, যে কোনো সাংসদ, বিধায়ক থাকতে পারবেন। মন্দির, গুরুদোয়ারা, খ্রিস্টান, জৈন, পারসি, বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের উপাসনালয় পরিচালনা পর্ষদে এই সূত্র মেনে চলা হবে কি?
নতুন আইন অনুযায়ী ওয়াকফ সম্পত্তি নির্ধারণের ক্ষমতা সার্ভে কমিশনারের কাছ থেকে সরকার নিযুক্ত রাজস্ব কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হবে। যার ফলে ওয়াকফ সম্পত্তির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করা হবে। আইনে আরও বলা হয়েছে যে কোনও ওয়াকফ সম্পত্তির নথি সহ রেজিষ্ট্রকরণ বাধ্যতামূলক এবং তা করতে হবে জেলাশাসকের কাছে। কেন এটা হবে? মৌখিক অনুমতির ভিত্তিতে বহু ওয়াকফ তৈরি (Waqf by use) হয়েছে এবং তা জারি আছে। সেগুলির তাহলে কী হবে? দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হাজার হাজার ওয়াকফ সম্পত্তির নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতামূলক নতুন আদেশটি সরকারের কোনো গোপন কর্মসূচিকেই উন্মোচিত করে। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতালাভের মাধ্যমে সরকারের কাছে বহু ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তর করার সুযোগ নতুন আইনে রয়েছে।
১৯৯৫ সালের আইনে বলা ছিল ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ তৈরি হলে রাজ্য সরকারগুলি ওয়াকফ ট্রাইবুনাল তৈরি করবে এবং ৭(১) ধারায় বলা আছে সেই ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত। বর্তমান আইনে ৭(১) ধারাকেই তুলে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে জেলাশাসকদের। প্রশাসনের কাছে বিচারব্যবস্থার ক্ষমতা প্ৰদানের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থাকে কি দুর্বল করা হল না?
নতুন আইন অনুযায়ী কোনো ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারের অধীনে থাকলে তা আর ওয়াকফ সম্পত্তি থাকবে না। তা কেন হবে? মালিকানা কেন ওয়াকফ হারাবে? বরং সরকারের দেখা উচিত যেসব সরকারি সম্পত্তির মালিকানা ওয়াকফের নামে আছে অথচ সরকার ভোগ করছে তার মধ্যে যেগুলি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব তা সত্ত্বর ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এখানে প্রশ্ন ওঠে তা হলে কি ওয়াকফ-এর রীতি ভেঙে উদ্বৃত্ত জমি-সম্পত্তি হস্তান্তর করা হবে?
নতুন আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার রেজিস্ট্রিকৃত ওয়াকফ সম্পত্তির হিসাব পরীক্ষা করার বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবে। ১৯৯৫ সালের আইনে ওয়াকফ বোর্ড এবং রাজ্য সরকার এই কাজ করত। এটা রাজ্য সরকারের কাজের উপর এবং ওয়াকফ বোর্ডগুলির ক্ষমতার উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ওয়াকফ বোর্ডগুলি তদারকি করে রাজ্য সরকার। এই বিল প্রণয়নের সময়ে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা করেনি। কৃষিনীতি (বর্তমানে বাতিল), শ্রমনীতি, এমন কি শিক্ষানীতি রচনায় কেন্দ্র একই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। এই পদক্ষেপ আসলে ভারতের সংবিধান স্বীকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপরেই আঘাত।
ওয়াকফ আইনের ৪০ ধারা বাতিল করার মাধ্যমে, ওয়াকফ বোর্ড ওয়াকফ সম্পত্তির প্রকৃতি নির্ধারণের কর্তৃত্ব হারাবে। ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি মূলত চারটি বিভাগে পড়ে: দলিল অনুসারে ওয়াকফ (নথিভুক্ত), মৌখিক ঘোষণা অনুসারে ওয়াকফ (মৌখিকভাবে ঘোষিত), ব্যবহারের মাধ্যমে ওয়াকফ (দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত), এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জমি। নতুন সংশোধনীর অধীনে, দেশের বেশিরভাগ ওয়াকফ সম্পত্তি - যা মৌখিকভাবে বা ব্যবহারের মাধ্যমে ঘোষিত - সরকারি দখলের ঝুঁকিতে পড়বে। উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং কেরালার মতো বৃহত্তম ওয়াকফ সম্পত্তি সম্পন্ন রাজ্যগুলি এই ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।
বিষয়টা মোটেই এমন নয় যে নতুন আইন প্রণয়নের আগে ওয়াকফ নিয়ে যা চলছিল তা ত্রুটিমুক্ত ছিল। সংবাদে প্রকাশ "ভারতে ওয়াকফ সম্পত্তির সংখ্যা এবং পরিমাণ নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য নেই। কারণ দেশে সে ধরনের বিজ্ঞানসম্মত কোনও সমীক্ষা হয়নি। নিবন্ধিত হয়নি এমন বহু ওয়াকফ আছে। তবে সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল সূত্রে জানা যায় সারা দেশে কমবেশি ৮ লক্ষ ৭০ হাজার ওয়াকফ সম্পত্তি আছে এবং সেগুলিতে মোট জমির পরিমাণ ৯ লক্ষ ৪০ হাজার একরের মতো। এর বাজার মূল্য ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অব ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী দেশের স্থায়ী সম্পদ বিশিষ্ট ওয়াকফের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৩২৮টি এবং অস্থায়ী সম্পদ বিশিষ্ট ওয়াকফের সংখ্যা হলো ১৬,৭১৩টি। এর মধ্যে ডিজিটাল রেকর্ডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৯৫টি ওয়াকফের। পশ্চিমবাংলায় ১ লক্ষের বেশি ওয়াকফ সম্পত্তি আছে। যার মধ্যে রেকর্ড ভুক্ত ৮০ হাজারেরও বেশি। বাম আমলে এই নথিভুক্তির কাজ হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে দেশে প্রতিরক্ষা ও রেল দপ্তরের পরে সবচেয়ে বড় জমির মালিকানা হল ওয়াকফ সম্পত্তি।"
এই বিপুল সম্পত্তির অনেকটাই বেআইনিভাবে ব্যক্তিস্বার্থে ভোগ দখল করছেন এমন কিছু মানুষ যাদের প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, আদপে ওই সম্পত্তি সাধারণ গরীব মানুষের কাজে লাগছে না। তাই আইনি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু আইন সংশোধন/সংস্কারের নামে সংবিধান প্রদত্ত ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং গণতান্ত্রিক কাঠামো ধ্বংস করার চেষ্টা হলে সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বিভাজনকারী ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবি গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে জানানো দরকার।
এতকাল ওয়াকফ-সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী ছিল মুসলমান সমাজ। সেই অধিকারে ভাগ বসানোর কাজটা নতুন আইন করে দিয়েছে স্রেফ গরিষ্ঠতার জোরে। এটা করতে গিয়ে লঙ্ঘিত হয়েছে মুসলমানদের জন্য সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার। বিল নিয়ে আলোচনার সময় যৌথ সংসদীয় কমিটিতেও বিষয়টিকে বিরোধীরা তুলেছিলেন। কিন্তু যে কমিটির চেয়ারম্যান সহ ৩১ জন সদস্যের মধ্যে ২০ জন শাসক দলের, সেখানে বিরোধী মত গুরুত্ব পাবে, তা-ও এই জমানায়, ভাবাই বাতুলতা। বিরোধীরা বিলে ৪৪টি সংশোধনী জমা দিয়েছিলেন। একটাও গ্রাহ্য হয়নি। সরকারপক্ষ থেকে জমা পড়েছিল ২৬টি। ১৪টি সংশোধনী গৃহীত হয় এবং দুই কক্ষে বিলটি পাস হয়। বিনা বাক্যেই রাষ্ট্রপতি সই করেছেন ‘ইউনিফায়েড ওয়াক্ফ ম্যানেজমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিল’-এ। এখন তা আইন। এখন দাবি, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মুসলমান সমাজের সবচেয়ে বড়ো হিতাকাঙ্ক্ষী। মুসলমানদের ভালোমন্দের ‘দায় ও দায়িত্ব’ নাকি তাঁরই। গাঁক গাঁক করে সেই প্রচার চলছে। নিরন্তর। যেমন তিন তালাক নিষিদ্ধ করে তিনিই মুসলমান নারীর মুক্তি ও কল্যাণের দরজা খুলে দিয়েছেন! পশ্চাৎপদ ‘পসমন্দা’ মুসলমানদের এগিয়ে আসতে সাহায্য করছেন! ওয়াকফ আইনও সংশোধন করা হয়েছে গরিব ও সাধারণ মুসলমানদের হিতে! ওয়াকফের অধীন বিপুল ভূসম্পত্তি ঠিকভাবে কাজে লাগালে বছরে নাকি কম করে হলেও ১২ হাজার কোটি টাকা আদায় হবে, যা গরিব মুসলমানদের কল্যাণে খরচ হতে পারে। ২০ বছর আগে সাচার কমিটির রিপোর্ট এই হিসাব দিয়েছিল। সরকারের দাবি, ওই টাকায় মুসলমানদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ভাবনা এখনই শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত প্রতি বছরই কেন্দ্রীয় বাজেটে সংখ্যালঘু সংক্রান্ত মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ কমে যাচ্ছে। এই বিষয়টিও নজরে আসছে।
রাজ্যস্তরে শিক্ষকদের কাজ হারানোর হাহাকারকে ঢেকে দিতে তাই কেন্দ্রস্তরে সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি হারানোর আশঙ্কাকে উসকে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তার জন্যই হয়তো মুর্শিদাবাদের অশান্তি। কিন্তু মুশকিল হল, আগুন নিয়ে খেলা সব ক্ষেত্রেই অত্যন্ত বিপজ্জনক। একটু এদিক-ওদিক হলেই আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না। সাম্প্রদায়িকতা এই রকমই ভয়ঙ্কর আগুন। এমনিতেই সামাজিক মাধ্যম জতুগৃহ তৈরি করে রাখে আর তাতে যদি রাজনীতি একটু আরও ঘি ঢালে, শাসক ও বিরোধী দু'পক্ষই নিজের ফুঁয়ের জোর দেখাতে থাকে, তবে রাজপথে পড়ে থাকে, কোনও সম্প্রদায়ের নয়, মানুষের লাশ।
সংসদে পাশ হওয়া আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায় শীর্ষ আদালতের সামনে, এবং সেটা তোলাও হয়েছে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যে সিপিআই এবং সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদকের তরফেও সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অন্য কিছু রাজ্যও এই পথে অগ্রসর হয়েছে। বাংলার তৃণমূল কংগ্রেস সেই পথে না গিয়ে তাদের নেতারা উস্কানিমূলক মন্তব্য করছেন, যার পালটা হিংসা ও উস্কানি দেওয়ার কাজে নেমে পড়েছে বিজেপি তথা সঙ্ঘ পরিবার। এর মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক উস্কানি এবং হিংসা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।
আপাতত যা মনে হচ্ছে দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষই নিজেদের জয়ী মনে করছে। দুই পক্ষের নেতাদের ঘটনাস্থলে যাওয়ার সময় হয়নি অথবা যেতে চাননি। অথচ পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সংসদ পর্যন্ত সমস্ত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের সকলেই রাজ্যের শাসকদলের সদস্য। গত সোমবার সিপিআই(এম) দলের রাজ্য সম্পাদক ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। নিহতদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রসঙ্গত, তিনি কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের পরাজিত প্রাথী। তার আগে/পরে কোনো জনপ্রতিনিধিকে সেখানে দেখা গেছে বলে শোনা যায়নি। তাঁরা কোথায় চা পান করছিলেন নাকী হাওয়া খাচ্ছিলেন অথবা উত্তেজনার আগুনে হাওয়া দিচ্ছিলেন তার খবর কে রাখে! বামপন্থী নেতৃত্ব যতক্ষণ ঘটনাস্থলে ছিলেন কোনো অশান্তি হয়নি। তাঁদের প্রত্যাবর্তনের পর আবার এলাকা অশান্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলি বামপন্থীদের সমীহ করে। এটা মোটেও কোনো শ্লাঘার বিষয় নয়। মানুষের বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ঐতিহ্য বামপন্থীদেরই রয়েছে। ইতিহাস তার সাক্ষী।
পক্ষান্তরে রাজ্য বিধানসভার শাসক ও বিরোধী দু'পক্ষেরই রাজনৈতিক পরিকল্পনা, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে নিজের কোলে ভোট টানা। ৩৩%-এর এক ভগ্নাংশও ছাড়া যাবে না বনাম বাকি সাতষট্টির অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ টানার খেলা। খেলা হবে, খেলা হচ্ছে আর তার দাপটে পড়ে যাচ্ছে মানুষের লাশ। মানুষ ঘরছাড়া। একবস্ত্রে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষ সঙ্গে করে আধার কার্ড, এপিক কার্ড সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র নিয়ে যেতে পেরেছেন কিনা তা জানা যায়নি। না নিয়ে যেতে পারলে আগামীদিনে নতুন কোনো বিপদের সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কাজ হারানোর হাহাকার হারিয়ে যাচ্ছে মৃত্যু আর ধ্বংসের হাহাকারে।
নতুন বঙ্গাব্দ ১৪৩২-এ কি দুয়ারে আতঙ্ক জাতীয় দুশ্চিন্তা নিয়ে একই ধারাবাহিকতায় এগিয়ে যাবে? না কি সংঘবদ্ধ শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছে সাম্প্রদায়িক বিভাজন মাথা নত করবে সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।