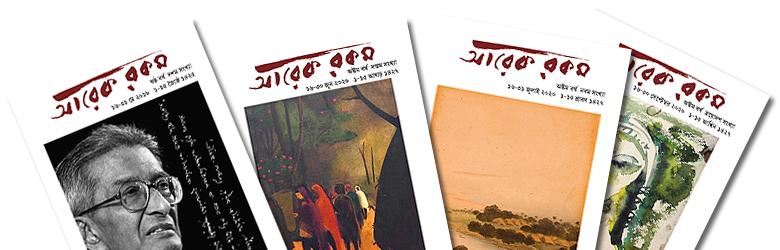আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা ● ১-১৫ এপ্রিল, ২০২৫ ● ১৬-৩১ চৈত্র, ১৪৩১
প্রবন্ধ
সোকাল কাণ্ডঃ ফান্দে পড়িয়া বুদ্ধিজীবী কান্দে রে
সায়ন ভট্টাচার্য
জ্ঞানী আর শিক্ষিতের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম তফাত আছে। শিক্ষিতদের অবচেতনে একটি অহংকারের স্রোত সদা বহমান থাকে এবং কখনও না কখনও তাদের সেই বহমান স্রোতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় জ্ঞানী ব্যক্তির সহজ সরল প্রশ্ন। আর কে না জানেন 'সহজ' বিষয়টা ঠিক ততটাও সহজ নয়। সোকাল কান্ড - এমনই একটা ফাঁদ জ্ঞানী আর শিক্ষিতের মধ্যে পাতা হয়েছিল। পেতেছিলেন বিজ্ঞানী অ্যালেন সোকাল।
১৯৯৬ সালে সংস্কৃতি চর্চা বিষয়ে বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা ‘সোশ্যাল টেক্সট’-এ একটি প্রবন্ধ জমা পড়ে, শিরোনাম 'ট্রান্সগ্রেসিং দ্য বাউন্ডারিজঃ টুওয়ার্ডস এ ট্রান্সফরমেটিভ হারমেনেউটিক্স অব কোয়ান্টাম গ্রাভিটি' (Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity), লেখক অ্যালেন সোকাল, একজন পদার্থ বিজ্ঞানী। অনেকের মনে হতেই পারে সংস্কৃতি, দর্শন বিষয়ক পত্রিকায় এমন ধারার প্রবন্ধ কেন? অবাক ঘটনা ঘটবে তো পরে, যখন এই প্রবন্ধটি শুধু মনোনীতই হলো না, ছেপে বেরোলো একটি স্পেশাল এডিশনে!
লেখার ফাঁদ ও হাটে হাঁড়ি
এরপর আসল রহস্য তো আসবে, যার জন্য শিক্ষামহল একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। রহস্য হল - আসলে বিজ্ঞানী সোকাল একটা ফাঁদ তৈরি করে এই প্রবন্ধটি পাঠান। তিনি চেয়েছিলেন সমাজবিজ্ঞানীদের বোকা বানাতেই 'ট্রান্সগ্রেসিং দ্য বাউন্ডারিজ' লেখাটির মধ্যে দিয়ে। তিনি ব্যবহার করেছিলেন কিছু অসংলগ্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য আর নানা নামকরা দার্শনিকদের, নির্দিষ্টভাবে বললে 'পোস্টমডার্ন' বুদ্ধিজীবী দার্শনিকদের, রচনা থেকে তুলে আনা ভারী ভারী শব্দ!
লেখাটা প্রকাশের পর সোকাল দিলেন হাটে হাঁড়ি ভেঙে। 'লিংগুয়া ফ্রাংকা’ পত্রিকায় আরেকটা প্রবন্ধ লিখে সেই আগের লেখার উত্তরে বললেন - গোটা প্রবন্ধে বাক্যের বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছুই ছিল না! ওর মধ্যে ইচ্ছে করেই তিনি লিখে দিয়েছিলেন নানা বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভুল ধারণা। তা ধরতেই পারেননি ‘সোশ্যাল টেক্সট’-এর 'পণ্ডিত' সম্পাদকরা, কারণ প্রবন্ধটা ভর্তি ছিল ওদের পছন্দমতো অনেক ভারী ভারী শব্দে, সেইসব শব্দ দেখতে পেয়েই হয়তো বা লেখাটাকে মূল্যবান মনে করেছেন ওঁরা, তথ্যের ভুল ধরার ক্ষমতা হয়নি। এই তো ওদের বিজ্ঞানের ওপর দখল! সোকাল মনে করেছেন, ওই স্বল্পজ্ঞান সম্বল করেই কিন্তু ওরা যখন-তখন বিজ্ঞানের ভাষ্যকার বনে যান, দিয়ে থাকেন মতামত। কিন্তু তার থেকেও যেটা বেশি করেন তা হলো বিজ্ঞানের পরিভাষার চূড়ান্ত অপব্যবহার! সোকাল সাহেবের প্রধান রাগের জায়গা এটাই।
তর্কের কুরুক্ষেত্র
এরপর কী ঘটল? যা আমাদের বাংলাতেও ঘটে - শুরু হয়ে গেল বিজ্ঞানী বনাম সমাজবিজ্ঞানী/দার্শনিকদের চূড়ান্ত কথার লড়াই! (বাংলায় যদিও এখন আর সমাজবিজ্ঞানী বা দার্শনিক থাকেন কিনা এ নিয়ে সন্দেহ আছে আমার) কিন্তু সোকাল এখানেই থামলেন না, তিনি আর আরেকজন ফরাসি বিজ্ঞানী জাঁ ব্রিকমন্ট (Jean Bricmont) মিলে লিখে ফেললেন একখানি বই, নাম - 'Intellectual Impostures'! বাংলা অনুবাদে কী বলা যায়? 'ভণ্ড আঁতেল' নাকি 'অজ্ঞ বুদ্ধিজীবীতেরা'? এই বইটি আবার ব্রিটেনে বেরোয় একটু নরম নাম নিয়ে 'Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectual's Abuse of Science!' (শৈল্পিক অজ্ঞেরা)
ধরুন এই যে আমাদের বাংলায় সেমিনার হয় ভুরি ভুরি - সেখানকার একজন বক্তাকে যদি ঘুরিয়ে বা খুঁটিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখনই দেখবেন তিনি বলেন - "এটা তো অনেক বড় আলোচনার বিষয়, সময় তো আর নেই এখানে!" 'সোকাল কান্ড' অনেকটা অ্যাসিড টেস্টের মতো - ধারণার বা পান্ডিত্যের প্রশ্নে কে সৎ আর কেইবা অসৎ।
বইটিতে আজকের দিনে চিন্তাজগতে যাঁরা খ্যাতিমান, সেই জাক দেরিদা, মিশেল ফুকো কিংবা জাঁ লাঁকা প্রমুখ নামিদামি লেখকদের ভয়াল সমালোচনা আর তাঁদের রচনার লাইনে ভুল, তার নমুনা তুলে ওদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রয়োগ বিশ্লেষণ আর তার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে! এই জিনিস আগে কখনও হয়নি চিন্তাশীল পৃথিবীতে। বিদ্বজ্জন মহলে পোস্ট-মডার্নিজম বা উত্তর-আধুনিকতাবাদের প্রচারক ওমন জাঁদরেল দার্শনিকরা এদিকে জ্ঞানচর্চার প্রতিনিধি হিসেবে প্রায় পূজিত। ওঁদের 'ভণ্ড' বলাটা কম সাহসের ব্যাপার নয়। কিন্তু, সোকাল আর ব্রিকমন্টের মতে আধুনিক খ্যাতনামা দার্শনিকরা বেশিরভাগই তাই। কেন? শুধু এই জন্যে নয় যে এঁরা আসলে দুর্বোধ্যতার পূজারী, কিন্তু সেই দুর্বোধ্যতা বজায় রাখতে এরা ব্যবহার করেছেন বিজ্ঞান এবং একেবারেই না বুঝে। বিজ্ঞানের পরিভাষাগুলো উল্টোপাল্টা ব্যবহার করে, আসলে তাঁদের উদ্দেশ্য - এইসব ভারী ভারী শব্দ ব্যবহার করে সাধারণ পাঠক এবং ভক্তকুলকে চমকিয়ে দেওয়া এবং তাদের তত্ত্ব যে বিজ্ঞানসম্মত সেই ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া! সম্ভবত এর আগে কেউ কখনও এমন করে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়নি যে, ঐসব পোস্ট-মডার্নিস্টরা বিজ্ঞানের জগৎ থেকে বহুদূরে কিন্তু তাও তারা নিজের স্বার্থে বিজ্ঞানের পরিভাষার অপব্যবহার করতে পিছপা নন।
বিজ্ঞানী বনাম সমাজবিজ্ঞানী
আসলে অনেক দিন ধরেই উত্তর-আধুনিকতাবাদের প্রচারকরা আর বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা ঠান্ডা লড়াই চলছে! এর নানা কারণ আছে তবে খুব সহজ কথায় উত্তর-আধুনিকতার সমর্থকরা মনে করেন, ‘অবজেকটিভ রিয়ালিটি' বলে কিছু হতে পারে না, অর্থাৎ ট্রুথ সাবজেকটিভ, অবজেকটিভ নয়। সত্য আসলে আপেক্ষিক। অনেকটা রচিত। যেন মনের মাধুরী। এবং তা ব্যক্তিনির্ভর! মানে 'নিরপেক্ষ সত্য' বলে কিছু নেই; অর্থাৎ, আমরা দেখি বা না দেখি, আবিষ্কার করি বা না-করি বাস্তব সত্য নিজে নিজে বিদ্যমান - এমন হতে পারে না। এখন এইরকম ভাবনা চিন্তার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা চটে যাবেন এটাই স্বাভাবিক! কারণ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন বাস্তব এবং নিরপেক্ষ সত্য বিদ্যমান এবং সেটা সবসময়ই প্রভাবের বাইরে। বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যই হল সেই সত্যকে আবিষ্কার করা। সুতরাং, উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা যদি বলেন যে সত্য আপেক্ষিক, তার চেহারা একেক জনের কাছে একেক রকম - মানে, তা নির্ভর করে কে তার দিকে কী দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকাচ্ছেন, তাহলে তো বিজ্ঞানীদের পছন্দ না হবারই কথা!
এই বিষয়ে, দার্শনিকদের এই মতকে ঠাট্টা করে সোকাল একটা চ্যালেঞ্জও ছোঁড়েন, উনি বলেন মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপারটা বিজ্ঞানীর আবিষ্কার যা বিজ্ঞানীদের মতে এক ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সত্য। কিন্তু, উত্তর-আধুনিকতাবাদ অনুযায়ী, ওটার কোনও নিশ্চিত অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক না কেন মাধ্যাকর্ষণ আছে না নেই। আমি পোস্ট-মডার্নিস্টদের আহ্বান জানাচ্ছি, ওরা কেউ এসে নিউ ইয়র্কে ২১-তলার ওপরে আমার অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে বাইরে একবার ঝাঁপ দিন। বলাবাহুল্য দুঃসাহসী সেই পরীক্ষার জন্য এগিয়ে আসেনি পোস্ট-মডার্নিস্টদের কোনও স্বেচ্ছাসেবী। বরং এই দুই বিজ্ঞানী প্রবল গালমন্দ সহ্য করেন দার্শনিকদের কাছ থেকে! বিতর্কটা কিন্তু অনেক পুরোনো দুশো বছর আগে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট লেখালেখি করেছিলেন আইডিয়ালিজম আর রিয়ালিজম-এর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নিয়ে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের যুক্তি সত্য-আবিষ্কার যদি অনুভূতি নির্ভর হয়, তাহলে বাস্তব আর কল্পনার ভেদ ঘুচবে কী করে?
চিন্তার বিষয়
এখন দুর্বোধ্যতাই উৎকর্ষের মাপকাঠি নাকি এই নিয়ে অ-বিজ্ঞানী মহলে নানা মত চালু আছে, অ-বিজ্ঞানী কথাটা আমি এখানে গুণমান বোঝাতে ব্যবহার করছি না, কারণ বিজ্ঞানই তো আর সব নয়, বরং বিজ্ঞানের বাইরে যে শিল্পী, লেখক, ইত্যাদিরা বিদ্যমান আছেন তাদের কথা বলছি! এদের অনেকেই কি আসলে মনে করেন না যে যা সাধারণ মানুষের মাথার ওপর দিয়ে যাবে সেটাই উত্তম জিনিস? সাধারণ মানুষেও কিন্তু এরকমই ভাবেন অনেকটা! কিউবিস্ট চিত্র বা অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট দেখে তার মর্ম একেকজনের মনে একেকরকম ভাবে প্রতিভাত হতে পারে, এবং তার সবগুলোই হয়তো যে দেখছেন তার কাছে সত্যি, পোস্ট-মডার্নিস্টরা এর ওপরেই ভিত্তি করে তাদের সাবজেক্টিভ ট্রুথতত্ত্ব চালান! লেখাও কিন্তু এরকম হতে পারে! বিশেষত এ তো কবেই বলা হয়ে গেছে - "কবি তব মনোভূমি, রাম জন্মভূমি অযোধ্যার চেয়ে সত্যি জেনো"! আবার ধরুন কিছুদিন আগে কয়েকটা লাইন পড়েছিলাম -
"অনেকে ভাবতেই পারেন, কোথাও এ পৃথিবীর সব মহৎ স্পন্দনই যেন অভিকেন্দ্রিক! সব আপাত-ভিন্ন মাত্রাগুলোর unification অনিবার্য তাই। সমাপতনের একক অবিচ্ছেদ্য, ঐ সংশ্লেষণেই সব পারঙ্গম্যের চূড়ান্ত সার্থকতা যে! বিশ্বাসী মন সহজেই বলে দেয় কোথায় সেই সমাপতন বিন্দু।"
- এই লাইনগুলি পড়তে সুন্দর লাগে, কিন্তু এর মানে কি নির্দিষ্ট কিছু নাকি তা একেকজনের কাছে একেকরকম হতে পারে? হতেই পারে! এবং সোকাল এবং ব্রিকমন্ট পরিষ্কার করে দিয়েছেন, বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ছবি, কবিতা বা কোনো প্রবন্ধের যথার্থতা নির্ণয় করা তাদের লক্ষ্য নয়, কারণ তা ভুল! তাদের আপত্তি হচ্ছে সেই লেখা নিয়ে যেখানে বিজ্ঞানের পরিভাষাকে একটা নতুন দার্শনিকতত্ত্ব তৈরী করতে গিয়ে একেবারে ভুলভাল ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে!
এরকম অন্য ক্ষেত্রে হলে কিন্তু তা নিয়ে প্রচুর হাসি ঠাট্টা মজা করা হয়, মনে আছে নিশ্চয় কাপড় কাচার সাবান গুঁড়োতে এক্টিভ অক্সিজেন দেওয়া বা শ্যাম্পুতে প্রোটিন মিশিয়ে চুলের পুষ্টি দেওয়া বিজ্ঞাপনগুলো!
এখন বলে রাখা ভালো অতি প্রাচীন গ্রিসে যেখানে জ্ঞানীরা আসলে বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক একসঙ্গেই দু'য়ের চর্চায় মেতে ছিলেন, তাঁরাও কিন্তু দুর্বোধ্যতাকে বেশি পছন্দ করতেন! উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে এরিস্টটল এবং টলেমি যে মহাবিশ্বের ধারণা দিয়েছিলেন তা অল্পকথায় এইরকম, আকাশে বহু চক্র আছে, এক এক চক্রে এক এক মহাজাগতিক বস্তু আছে, যেমন সূর্য একটা চক্রে, চাঁদ একটা চক্রে, কিছু তারা একটা চক্রে, এবং এগুলি একে অপরকে ঘিরে ঘুরে চলে, বিভিন্ন মহাজাগতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে দিতে এই চক্রের সংখ্যা বেড়েই চলে এবং একসময় তা ৫৬টা চক্রে গিয়ে দাঁড়ায়! পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা যখন সূর্যকেন্দ্রিক আরও সহজ তত্ত্ব দেন, তখন সেগুলো গ্রহণ না করার একটা বড় কারণ ছিল সেগুলোর তুলনামূলক সহজবোধ্যতা! হয়তো তখন থেকেই বিজ্ঞান আর দার্শনিকদের পথ আলাদা হয়ে যেতে থাকে!
'সোকাল কান্ড' উত্তর ঔপনিবেশিক ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তর্ক, বিশেষ করে আধুনিক বিজ্ঞানের নয়া ধারণা বনাম দক্ষিণপন্থী রাজনীতির রমরমা বাজার।
যদিও অবশ্যই মনে করা হয় সাংস্কৃতিক চিন্তাবিদরা দক্ষিণপন্থীদের হয়ে কথা বলে না, তাঁরা সর্বদাই গণতান্ত্রিক ও জাতি বিদ্বেষ বিরোধী অবস্থান নেয় - তবুও সোকাল কান্ডের কিছু সুচিন্তার প্রয়োগও বিপজ্জনক নয় একথা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।
বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক চর্চার এই তর্কের মাঝে ভারতীয় সমাজে উদ্ভূত হয় 'এথনো-সায়েন্স', 'হিন্দু বিজ্ঞান', 'ঐস্লামিক বিজ্ঞান' 'তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞান' ইত্যাদি বিভিন্ন অ-বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো ব্যাখার একটা অসৎ প্রচেষ্টা থাকে।
ভয়ের একটা জায়গা থেকেই যাচ্ছে সব সময়। অবৈজ্ঞানিক চর্চা দিন দিন ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান। বৌদ্ধিক পরীক্ষার যে নয়া আবিষ্কার সোকাল দেখিয়ে গেলেন সেই পদ্ধতি কোনও না কোনও ভাবে অবশ্যই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় হিংস্রতার বিরুদ্ধে।
পটভূমিকা না জানলে বইটা পড়ে পুরো মজা পাওয়া যাবে না, আমি বইটার খোঁজ পাই যেমন অনেক কিছুরই পেয়েছি, পথিক গুহর লেখা প্রবন্ধ থেকে! দার্শনিকরা কোয়ান্টাম মেকানিক্স, ডেল’স থিওরেম থেকে কেওস থিওরি এইসব নিয়ে নানা মন্তব্য করে চলেছেন! ‘ইনটেলেকচুয়াল ইমপস্টারস’ লেখার জন্য দার্শনিকদের প্রচুর গালাগালি খেয়েছেন এবং খাচ্ছেন সোকাল আর ব্রিকমন্ট। এগুলো আসলে অনেকটাই তাৎক্ষণিক বিষোদগার বা অপমানিতের ধিক্কার।