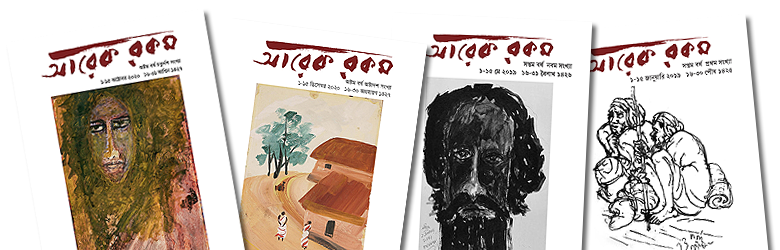আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা ● ১-১৫ এপ্রিল, ২০২৫ ● ১৬-৩১ চৈত্র, ১৪৩১
সম্পাদকীয়
তোমার বিচার করবে কে?
ভারতীয় বিচারব্যবস্থা বহু সময়েই বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছে। মাননীয় বিচারকদের কিছু রায় যা হয়ত মনে হয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উক্তি, সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এমনকি বহু রায় লক্ষাধিক মানুষের জীবনকে মুহুর্তে তছনছ করেছে এমন নজিরও অমিল নয়। রাম মন্দির নির্মাণের রায়, আসামে এনআরসি শুরু করার নির্দেশ, এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে সেবির প্রাক্তন অধিকর্তা মাধবী বুশের বিরুদ্ধে তদন্তের আর্জি খারিজ এমন বহু বির্তকিত রায় অতীতে এমনকি দেশের সর্বোচ্চ আদালত অবধি দিয়েছে। পরবর্তীতে রায়দানকারী বিচারকের কেন্দ্রের শাসকদলের কৃপায় রাজনৈতিক পুনর্বাসন বিতর্ককে কমায়নি বরং বাড়িয়েছে। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির বাড়িতে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি আদালতের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তিকে খানিক নষ্টই করেছে। এমনকি যখন বিচারপতি বলেন, ভগবানই তাকে রায় দিতে সাহায্য করেছেন তখন আস্তিক থেকে নাস্তিক, সমস্ত আমজনতারই ভরসা প্রায় নড়ে ওঠে। তবুও আজও মানুষ শেষ ভরসা বলতে আদালতই বোঝেন। মনে করেন, রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি তার কথা না শোনে, তবে আদালতে গেলে হয়ত ন্যায় মিলবে। কিন্তু যদি দেখা যায় আদালতের ন্যায় বাজারে মালের দরে বিক্রি হচ্ছে, তাহলে এই বিরাট জনতার আস্থাহীনতা যে সামাজিক অস্থিরতার জন্ম দেবে তা বিলক্ষণ।
এমন ঘটনা অবশ্য না চাইলেও ঘটে যায়। বিগত ১৪ই মার্চ, দিল্লী হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মা'র সরকারি বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের পর বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার হয়। সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, পরের দিন অর্থাৎ ১৫ই মার্চ দিল্লী হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি কে উপাধ্যায় এই ঘটনা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে জানান। কিন্তু বিতর্ক তৈরী হয় সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম বিষয়টি নিয়ে ২০শে মার্চ অবধি চুপ করে থাকায়। ঘটনা যখন ২০ তারিখে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পায় তখন দ্রুততার সাথে কলেজিয়াম বৈঠক করে বিচারপতি ভার্মাকে দিল্লী হাইকোর্ট থেকে বদলি করে এলাহাবাদ হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেয়, যেখান থেকে তাঁকে আগে দিল্লীতে বদলি করা হয়েছিল। ঘটনায় কোনো অভিযোগ পুলিশের কাছে নথিবদ্ধ হয়নি। এমনকি কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডিকেও এ বিষয়ে তদন্ত করতে বলা হয়নি। কেবল সুপ্রিম কোর্ট তিন বিচারপতির একটি তদন্ত দল গড়ে দিয়ে কাজ সেরেছেন। আর কেন্দ্রের সরকার সুপ্রিম কোর্টের এই বদলির সুপারিশে সম্মতি জানিয়ে দিয়েছে। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও এফআইআর দায়ের করার অনুরোধে মামলা দাখিল হয় গত ২৮শে মার্চ। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এই মামলা খারিজ করে জানিয়েছেন যে এই পদক্ষেপ এখনই নেওয়া উচিত নয়। তারা তদন্ত কমিটির ওপর আস্থা রাখতে বলেছেন।
সর্বোচ্চ আদালতের এই বিষয়ে প্রতিটি পদক্ষেপই এখনও অবধি মানুষকে বিরূপই করেছে। গত ২৭শে মার্চ দেশের ৬টি হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন বিচারক ভার্মার এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির নির্দেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। এলাহাবাদের হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন স্পষ্টই দাবী জানিয়েছে যে এলাহাবাদ আদালত আস্তাকুঁড় নয়। কিন্তু এখনও অবধি সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম তাঁদের সিদ্ধান্তই বলবৎ রেখেছেন।যদিও কলেজিয়াম অভিযুক্ত বিচারপতিকে কোনো মামলার সাথে যুক্ত করতে বারণ করেছে। এই সুযোগে কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি নতুন করে তামাদি হয়ে যাওয়া 'জাতীয় বিচারক নিযুক্তকরন কমিশন' (NJAC)-কে নয়া রূপে ফেরত আনতে চেয়ে বিতর্ক তুলেছে। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর এই আইন কার্যকর করা নিয়ে বক্তব্য রেখে বিতর্ক শুরু করেছেন। এই আইনে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে বিচারপতিদের নিয়োগ একটি ছয় সদস্যের কমিটির মাধ্যমে করা হবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন ভারতের প্রধান বিচারপতি। এই কমিটিতে আরও থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের দুই শীর্ষস্থানীয় বিচারপতি, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এবং দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল একটি প্যানেলকে, যেখানে সদস্য হিসেবে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি এবং লোকসভার বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতা। স্বাভাবিকভাবেই দলীয় রাজনীতির প্রভাব, বিশেষত ক্ষমতাসীন দলের হাতে বিচারপতি নিয়োগের লাগাম চলে যাওয়ার আশঙ্কায় সুপ্রিম কোর্ট এই আইন খারিজ করে দেয়। পরিবর্তে কলেজিয়াম ব্যবস্থাই তারা চালু রাখে। বর্তমান বিতর্কের জেরে বিজেপি আবারও এই আইন আনতে চায়। তাদের চাহিদা অবশ্য বরাবরই বিচার ব্যবস্থাকেও গিলে খাওয়ার। কিন্তু এতদিন যে চাহিদা জনমানসে সমর্থন পায়নি, আজকের পরিস্থিতি ঠিক তার বিপরীত আবেগের জন্ম দিচ্ছে।
আদতে বিচারকদের সম্পর্কে জনগনের অনাস্থা দীর্ঘ লালিত এবং তা নিতান্তই অমূলক নয়। অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের মতো বিচারকদের জন্য তাদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা এটি প্রকাশ করেননি। এই পরিস্থিতি বিচারকদের সম্পদ ও দায়-দেনা প্রকাশের দাবিকে আরও জোরালো করছে। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জে এস ভার্মার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সুপ্রিম কোর্ট একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যেখানে বলা হয়েছিল, “প্রত্যেক বিচারককে নিজের নামে, জীবনসঙ্গীর নামে বা তাদের উপর নির্ভরশীল অন্য কারও নামে থাকা সম্পত্তি ও বিনিয়োগের ঘোষণা প্রধান বিচারপতির কাছে দাখিল করতে হবে।” তবে এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার আহ্বান ছিল না; এটি কেবলমাত্র প্রধান বিচারপতির কাছে জানানোই ছিল মূল উদ্দেশ্য। পরে, ২০০৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ বিচারকদের সম্পদ কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে উল্লেখ করা হয় যে এটি 'সম্পূর্ণ স্বেচ্ছার ভিত্তিতে' করা হচ্ছে। ঐ বছর নভেম্বর মাসে এই ঘোষণাগুলো ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়, এবং পরে কয়েকটি হাইকোর্টও এই ধারা অনুসরণ করে। তবে, সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটটি ২০১৮ সালের পর থেকে আপডেট করা হয়নি। বর্তমানে ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র ৩৩ জন বিচারকের মধ্যে ২৮ জনের নাম তালিকাভুক্ত আছে, যারা তাদের সম্পদের বিবরণ প্রধান বিচারপতির কাছে দাখিল করেছেন। এছাড়া, সাবেক বিচারকদের ঘোষণাগুলিও ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে বিচারকদের ব্যক্তিগত সম্পদ ও দায়-দেনা 'ব্যক্তিগত তথ্য' নয়। এই রায়ের ভিত্তি ছিল ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে তথ্য অধিকার (RTI) কর্মী সুভাষ চন্দ্র আগরওয়ালের একটি আবেদন, যেখানে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, ১৯৯৭ সালের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিচারকরা আসলেই তাদের সম্পদের বিবরণ প্রধান বিচারপতির কাছে জমা দিয়েছেন কি না। ২০২৪ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত দেশের সব হাইকোর্ট মিলিয়ে মোট ৭৭০ জন বিচারক রয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র ৯৭ জন বিচারক (যারা দিল্লি, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মাদ্রাজ, ছত্তিসগড়, কেরালা এবং কর্ণাটক হাইকোর্টের) তাদের সম্পদ ও দায়-দেনা প্রকাশ করেছেন। যা মোট হাইকোর্ট বিচারকদের মাত্র ১৩%-এরও কম।
এরই সাথে যখন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রাজ্যসভার শাসকদল মনোনীত সাংসদ হয়ে যান বা রামের মতো কাল্পনিক পৌরাণিক চরিত্রের জন্মস্থানের দাবীকে মেনে নিয়ে বাবড়ি মসজিদ ভেঙে ফেলায় অভিযুক্তদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন, সমাজকর্মীদের ইউএপিএ-এর মতো দানবীয় ধারায় বছরের পর বছর আটক থাকার বিষয়ে মামলার নিষ্পত্তি না করা অথচ শাসক ঘনিষ্ট সাংবাদিকের এক দিনে জামিনের রায় দিয়ে দেন তখন মানুষ বিচারকদের আয়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারকে দুর্নীতির সাথে মিশিয়ে দেখতে থাকেন এবং সমাজে বিচার ব্যবস্থার প্রতি এক গভীর অনাস্থা তৈরী হয়। মানুষ ভাবতে থাকেন যে বিচারপতি হয়ত অর্থের বিনিময়ে রায় দিচ্ছেন। ফলে আইন ব্যবস্থা আমজনতার নয়, কেবল প্রতিপত্তিশালীর, এই ধারণা জনমানসে প্রোথিত হয়ে যায়। একই সাথে তা উৎসাহিত করে সমাজে দুর্নীতির তল্পীবাহকদের। তারাও মনে করতে থাকে বিচারপতির নিরপেক্ষতা কেবল একটি আষাঢ়ে গল্প। আদতে বিচার কেবল অর্থের জোরেই কিনে ফেলা যায়। ফলে সব মিলিয়ে রাষ্ট্রের এই তৃতীয় স্তম্ভের প্রাসঙ্গিকতা হারায়।
এমতাবস্থায় দেশের সচেতন নাগরিকদেরই দায়িত্ব নিতে হবে এই ত্রুটি সংশোধনে। বিচারব্যবস্থা জনগণের উর্দ্ধে থাকা কোনো ব্যবস্থা হতে পারেনা। জনগণকে নিরপেক্ষ ন্যায় দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। কিন্তু প্রতিষ্ঠান কোনো বিমূর্ত অবয়ব হতে পারেনা। নির্দিষ্ট দায়ভুক্ত প্রতিনিধি দিয়েই প্রতিষ্ঠান চলে। যেভাবে অভয়া বা নির্ভয়া কাণ্ডে ন্যায় দেওয়ার দায় সংশ্লিষ্ট সরকারের দায়, সেভাবেই বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নির্ভর করে বিচারকদের ব্যক্তিগত দায়ের উপর। তাদের জনগণের চেয়েও উপরের আসনে প্রতিষ্ঠা করলে তা কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতিরই পালিকা হবে। ফলে এই গোটা বিতর্কের সুষ্ঠু বিশ্বাসযোগ্য সমাধানের দায় যেমন সুপ্রিম কোর্টের তেমনই বিচারকদের জনতার কাছে দায়বদ্ধ রাখতে তাদেরও লোকপালের এক্তিয়ারে আনা আজ সময়ের দাবী। বিচারকদের ব্যক্তিগত আয় প্রকাশিত না হলেও অন্তত জনতা নির্বাচিত কোন সংস্থার কাছে তা নথিভুক্ত হতে হবে। তবেই বিচারব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে মানুষের সহায়ক হবে। নয়ত এমন বিতর্ক তৈরী হতেই থাকবে, যা কাম্য নয়।