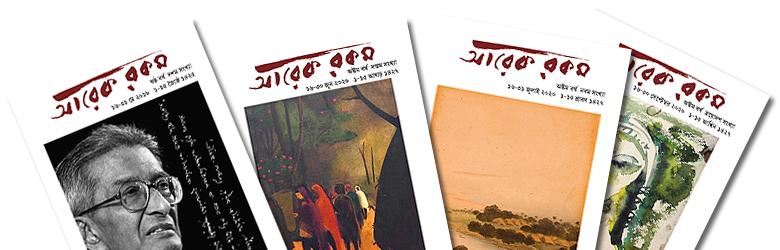আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ● ১৬-৩১ মার্চ, ২০২৫ ● ১-১৫ চৈত্র, ১৪৩১
প্রবন্ধ
ভাষার আধিপত্য: হিন্দি, ইংরেজি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা
পবিত্র সরকার
১. 'আতিথেয়তা' থেকে
সম্প্রতি তামিলনাডুর মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্ট্যালিনের হিন্দি ভাষার আধিপত্যের বহু উদ্যোগ সম্বন্ধে নানা সমালোচনা কাগজে টেলিভিশনে প্রকাশিত হচ্ছে, ফলে বিষয়টা নিয়ে আবার একটু নাড়াচাড়া পড়ছে, মানুষ বুঝতে চাইছেন ব্যাপারটা ঠিক কী হচ্ছে, বা কেন হচ্ছে। পাঠকদের বলি, বহুভাষিক দেশে প্রশাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতির নানা স্তরে নানা ভাষার ভূমিকাতে কোথাও কোথাও আধিপত্যের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা হতে বাধ্য। শুধু বিদেশি শাসন নয়, ভাষার ছোটত্ব, বড়ত্ব, গুরুত্ব, লঘুত্ব, জনগোষ্ঠীর ঘনতা, বিচ্ছিন্নতা, অভিবাসন ইত্যাদি নানা কারণে কোনও ভাষাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। একটা আধিপত্য ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়, তাতে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্পষ্ট সচেতন প্রয়াস নাও থাকতে পারে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মিলে যে ব্যবস্থা বা সিস্টেম গড়ে ওঠে, তারই ফলে ওই আধিপত্য।
এর একটা পরম্পরাগত উদাহরণ হল ভারতীয়দের হিন্দুধর্মের নানা ক্রিয়াকর্মে সংস্কৃত ভাষার আধিপত্য। বা মুসলমান ধর্মে আরবি ভাষার আধিপত্য। এ রকম একটা ভিত্তিহীন বিশ্বাস বহুদিন আগে ভারতের জাতপাত-কণ্টকিত হিন্দুসমাজে চারিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে সংস্কৃত ‘দেবভাষা’, অর্থাৎ দেবতারা স্বর্গে বলত, তাই হিন্দু পূজা-আচার ব্রাহ্মণের উচ্চারিত সংস্কৃত মন্ত্রে সিদ্ধ না হলে তার কোনও মূল্য নেই। বিশ্বাসের যে কোনও শক্তপোক্ত চিকিৎসা নেই তা তো আমরা সাম্প্রতিক কুম্ভমেলাতেও দেখলাম, ধর্মের নানা উদ্যমে সর্বত্রই দেখি। তার ফলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণির প্রশ্নহীন আধিপত্য দীর্ঘদিন হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রেণির আধিপত্য ভাষার আধিপত্যের চেহারা ধরেছে, যদিও বেশিরভাগ ভারতীয় যাজক ব্রাহ্মণ সংস্কৃতে অশিক্ষিত এবং ভুল উচ্চারণে সংস্কৃত আউড়ে থাকে। ভাষার আধিপত্য অনেক সময় মানুষের শোষণের চেহারা নিয়ে জারি থাকে।
ভারতে হিন্দিরও একটা সামাজিক ও ‘সাংস্কৃতিক’ উপস্থিতি দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে। এ দেশের সর্বত্রই প্রখরভাবে উদ্যমী হিন্দিভাষীরা, বা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দিভাষী মানুষেরা ব্যবসা ও শ্রমের লক্ষ্যে ছড়িয়ে পড়েছেন, যদিও, মনে হয়, দক্ষিণে তাঁদের প্রভাব তুলনায় ততটা ছড়ায়নি। অন্য সব জায়গায় তাঁরা, অনেকে মূলে হিন্দিভাষী না হলেও (রাজস্থানি, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি ভাষার মানুষ হয়তো) হিন্দি ভাষাকেই তাঁরা দেশের অন্যত্র বহন করে নিয়ে গেছেন। ফলে হিন্দি ভাষাটির সঙ্গে অন্য ভারতীয়রা পরিচিত হয়েছে। এই সামাজিক প্রক্রিয়া একদিকে চলেছে। এটা কতটা আধিপত্যের চেহারা নিয়েছে তা জানি না, কিন্তু কলকাতার বড়বাজারে গেলে দোকানে দরাদরিতে আমরা ভাঙা হিন্দিতে কথা বলতে বাধ্য হয়েছি, ট্যাক্সিতে পাঞ্জাবি ড্রাইভারের সঙ্গে, বা রিকশোচালকদের সঙ্গেও, গড়িয়াহাটের বাজারে ঝুড়িওয়ালার সঙ্গে। এটা আধিপত্য বলব না আতিথেয়তা (accommodation) বলব, তা অবস্থার ওপর নির্ভর করে। কারণ আতিথেয়তা কখন তাঁবুর মধ্যে সেই উটটির মতো আধিপত্যের চেহারা নেয় তা বোঝা খুব মুশকিল। তবে ভারতের নানা ক্ষেত্রে আমরা এই আংশিক ‘দ্বিভাষিকতা’ মেনে নিতে বাধ্য হই। এটা ততক্ষণই ভালো যতক্ষণ এর একটা ভাষা আর-একটা ভাষার ঘাড়ে চেপে তাকে দমিয়ে বা বদলে দেবার চেষ্টা না করে।
তারপর অন্যদিকে হিন্দি বা ওর কাছাকাছি ভাষার তথাকথিত ‘সাংস্কৃতিক’ উপস্থিতি। উত্তর ভারতীয় মার্গসংগীত — ধ্রুপদ, খেয়াল, ভজন, ঠুংরি ইত্যাদির চর্চায় বাঙালিও হিন্দি বা তার সগোত্রীয় ভাষার আধিপত্য মেনে নিয়েছে, যদিও উনিশ শতকে বাংলাতে টপ্পা প্রচুর রচিত হয়েছে, আর কিছুদিন হল কবীর সুমন খুব উদ্যম নিয়ে বাংলা খেয়ালকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে হিন্দি সিনেমার গানের অপ্রতিহত প্রাধান্য আমরা সর্বত্রই লক্ষ করেছি, এমনকি দক্ষিণেও। আমি বালককালে যে শহরে থাকতাম সেই খড়্গপুরে দক্ষিণের তেলুগুভাষীদের বিপুল প্রাধান্য ছিল। তাঁদের উৎসব-অনুষ্ঠানে সর্বত্রই মাইক্রোফোনে হিন্দি ফিল্মের গান বাজত, এমনকি শ্মশানযাত্রাতেও তাঁরা হিন্দি ফিল্মের গানের সুর বাজিয়ে বাদ্যভাণ্ডের মিছিল করে যেতেন। বাঙালিরাও এই ‘আতিথেয়তা’য় কম যেত না। বেশ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত কলকাতার পুজো-আচ্চায় হিন্দি গান বাজত মাইকে। বামফ্রন্টের আমলে তার দাপট কমে আসে। তবে এখন ডিস্ক-জকি সংস্কৃতিতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় তার রমরমা আমরা দেখি না তা নয়। সংস্কৃতির সমাজবিজ্ঞানী গবেষণা করে এই আতিথেয়তা-আধিপত্যের ঐতিহাসিক বিবর্তন আর এখনকার অনুপাত আমাদের দেখাতে পারেন। টেলিভিশনে মোবাইলেও এখন হিন্দি ছবি ও প্রোগ্রাম দেখার অঢেল সুযোগ হয়েছে। গানের বা ফিল্মের মধ্য দিয়ে ভাষা আমাদের ভাষাতেও এসে পৌঁছায়। পথেঘাটে কমবয়সি ছেলেদের সংলাপে হিন্দি বুকনি চলে আসে ফিল্মের সংলাপ থেকে - যেমন ‘শোলে’ ছবির কোনও নাটকীয় সংলাপ — "অব তেরা কেয়া হোগা রে কালিয়া?" গোছের। বয়সের কারণে আমার উল্লেখ কিছু পুরোনো, কমবয়সিরা নিশ্চয়ই আরও অনেক নতুন উপাদান যোগ করতে পারবেন।
এ অংশে আমরা বলবার চেষ্টা করেছি যে, ভারতের মতো বহুভাষী দেশে মানুষ নানা কারণে দ্বিভাষী হয়, আর তাতে অন্য ভাষার প্রতি আতিথেয়তার একটা সূত্র থাকে। এখানে আমি ভারতের বড় ভাষাগুলির কথাই বেশি করে বলছি। ছোট ভাষাগুলি বাধ্য হয়ে আধিপত্য স্বীকার করে, সেগুলির কথা পরে আলাদা করে বলব।
এখানে পাঠকদের ভাবনাকে স্বচ্ছ করার জন্য যে কথাটি যোগ করব তা হল, ভাষাবিজ্ঞানে কোনও দুটি ভাষার মধ্যে — ছোট হোক, বড় হোক — কোনও রকম গুণগত, অর্থাৎ ভালোমন্দের তারতম্য করা হয় না। তার কথা হল — any language is as good as any other language [১] অর্থাৎ সম্ভাবনার দিক থেকে সব ভাষাই সমান। কিন্তু ইতিহাসের যোগাযোগে বা তার অভাবে তাদের গুরুত্ব কমবেশি হয়। বাংলা ভাষার একটা সংস্কৃত উত্তরাধিকার ছিল, তার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার সম্বল যোগ হল, ফলে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় এ ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। ইংরেজরা সাঁওতালি ভাষা এলাকায় রাজধানী স্থাপন করলে সাঁওতালি বাংলার আগে সমৃদ্ধ আধুনিক ভাষা হয়ে উঠতে পারত। ভাষা সমৃদ্ধ হওয়ার কারণগুলি হল — শিক্ষা, প্রশাসন, সাহিত্য, প্রযুক্তি, আইন ইত্যাদিতে তার ব্যাপক ব্যবহার। খুব ছোট (কম লোকসংখ্যা বলে, নানা রাজ্যে ছড়িয়ে আছে, লিখিত হয়নি ইত্যাদি) ভাষায় এ সব ব্যবহারের অসুবিধা আছে, তাই সেগুলিকে অন্য ভাষার আংশিক আধিপত্য মেনে নিতে হয়।
২. আধিপত্যের বৈধ ব্যবস্থাপনা
সবাই জানি যে, ১৮৩৫ সালে মেকলের সুপারিশে ইংরেজি আমাদের 'রাজভাষা' হয়েছিল, শিক্ষারও ভাষা হয়েছিল। তার সুফল ও কুফল বহু আলোচিত। আমরা নীচে একটু কুফলের উল্লেখ করেছি। তবে ভারতের স্বাধীনতার পরে ১৯৫০ সালে যখন আমাদের সংবিধান প্রচারিত হল, তখন ওই সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাবের ওপর একটা সাংবিধানিক মাত্রা যোগ হল। ভাষার আধিপত্যের পুনর্বিন্যাসও হল। যেহেতু ভারত বহুভাষিক দেশ, আর অনেকগুলি রীতিমতো সাহিত্যওয়ালা সম্ভ্রান্ত ভাষা — তাই বড় ভাষাগুলির অমর্যাদা না হয়, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা, কংগ্রেসের রাজনৈতিক কাজকর্ম ও প্রতিশ্রুতির ভাষা হিন্দিও যোগ্য মর্যাদা পায়, সেই সঙ্গে এতদিন ধরে শিক্ষা আর প্রশাসনিক কাজে আধিপত্যকারী ভাষা ইংরেজিকেও, কিছুটা নাচার হয়ে, স্বীকৃতি দেওয়া হয় — এই রকম একটা ক্ষমতা বিন্যসের চেষ্টা হল সংবিধানে। তাই ক্ষমতা বিভাজন ও স্তরায়ণ ভারতীয় ভাষাগুলির ক্ষেত্রে, একটু সরল করে, এইভাবে হল —
১. ভারত রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ভাষা: দেবনাগরি লিপিতে হিন্দি, ইংরেজি।
২. অষ্টম তপশিলের ভাষা: প্রথমে ১৪ ছিল, এখন ২২টি। অধিকাংশ প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক প্র-শাসন, শিক্ষা (এমনকি আংশিকভাবে উচ্চশিক্ষা) ইত্যাদির ভাষা — অসমিয়া, বাংলা, মারাঠি, ইত্যাদি। এদের মধ্যে সিন্ধি, বোড়ো, সাঁওতালি, উর্দু [২] এরকম কয়েকটি ভাষা আস্ত কোনও প্রদেশের প্রশাসনিক ভাষা নয়, আর সংস্কৃতকে এখানে কেন রাখা হয়েছে তার যুক্তি অস্পষ্ট।
৩. অন্যান্য ভাষা, যেগুলির লিপি ও সাহিত্য আছে এবং শিক্ষার সর্বস্তর না হলেও স্কুল স্তর পর্যন্ত [৩] ব্যবহৃত হয় — কখনও বাহন ও বিষয় দু-হিসেবেই, কখনও শুধু বিষয় হিসেবে। সংবাদ সাময়িকপত্রে ব্যবহৃত হওয়া কিছু ভাষা। সব শেষে
৪. স্থানীয় গৌণ ভাষা, যার লিপি নেই, সাহিত্য শুধু মৌখিক।
আমরা বলেছি যে, ২-এর ভাষাগুলোর কিছুটা ব্যাপক স্বীকৃতি আছে, প্রাদেশিক প্রশাসন, শিক্ষা, আইন ইত্যাদির ভাষা হিসেবে। এগুলির সমৃদ্ধ সাহিত্যও আছে। হয়তো সে সংক্রান্ত গর্বও পোষণ করেন এই সব ভাষার বক্তারা। অন্য ভাষাগুলির মধ্যে যেগুলি গৌণ সেগুলি নানাভাবে দুর্বল। একটি কারণ এই যে, বক্তার সংখ্যা এক জায়গায় যথেষ্ট নয় বলে, আর লিপি নেই বলে তাদের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কিন্তু সংবিধানের প্রস্তাবনায় (preamble) ভারতীয় নাগরিকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে তা করতে হবে নিজের মাতৃভাষাতেই। বক্তা সংসদে বা বিধানসভায় তাঁর মাতৃভাষায় মত প্রকাশ করতে পারবেন, সে যে ভাষাই হোক, এবং সরকার তা অন্যদের কাছে বোধগম্য করে তোলার (অনুবাদের মাধ্যমে) দায়িত্ব নেবেন। ৩৫০ ধারাতে ভারতের নাগরিক তাঁর ব্যবহৃত যে-কোনও ভাষায় অভিযোগ করতে এবং তার প্রতিবিধান চাইতে পারবেন।
যাঁরা সমাজভাষাবিজ্ঞান (sociolinguistics) সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন তাঁরা জানেন যে, ভাষার এই ক্ষমতাবিন্যাসের মানবিক প্রকল্পের নাম ‘ভাষা-পরিকল্পনা’ বা language planning। ভাষার ‘ভূমিকা’ পরিকল্পনা বা status planning তার প্রথম কাজ, যা স্থির করে দেয় ভাষাটিকে কোন্ কাজে লাগাতে হবে। দু-নম্বর, ভাষাটিকে ওই সব কাজে লাগানোর জন্য তার কী পরিচর্যা করতে হবে তার নাম হল উপাদান-পরিকল্পনা বা corpus planning. নানা কমিশন, কমিটি, সংস্থান গড়ে দিয়ে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা আন্তরিকভাবে দু-রকম চেষ্টাই করে গেছেন। [৪]
এ রকম আরও অনেক অনুশাসন সংবিধানের ৩৫৩ থেকে ৩৫১ ধারাতে দেওয়া আছে, তা এখানে আলোচনার অবকাশ নেই। [৫] এতে আমরা আগে যে ‘আতিথেয়তা’র কথা বলেছি, ভাষাগুলির পরস্পরের মধ্যে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রত্যেকের ভূমিকা নির্দেশ করে। তবে পরবর্তী ইতিহাস দেখলে বোঝা যাবে যে, মূলত হিন্দিভাষীবহুল শাসকদের কার্যকলাপে, ‘হিন্দুত্ব’ না হোক, তথাকথিত ‘দেশপ্রেম’-এর প্রচ্ছন্ন যুক্তিতে বারবারই ইংরেজিকে সরিয়ে হিন্দিকে আনার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু দক্ষিণি রাজ্যগুলির প্রতিবাদে সে চেষ্টা স্থগিত রাখতে হয়েছে। ফলে এখনও পর্যন্ত সংবিধানের ৩৪৩ ধারাতে আমাদের প্রশাসনিক ভাষা দুটি, দেবনাগরি বর্ণে [৫] হিন্দি, আর ইংরেজি। দেশপ্রেমের যুক্তিটি সরল — ইংরেজি বিদেশি ভাষা আর আমাদের পরাধীনতার স্মৃতিবাহী ভাষা। কিন্তু তাতে আবার এই ঐতিহাসিক সত্যটিও অস্বীকার করা হয়েছে যে, একমাত্র ইংরেজি ভাষাই উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম ভারতের নানা দিগন্তের ‘শিক্ষিত’ মধ্যবিত্ত মানুষদের মধ্যে একটা বৌদ্ধিক ও মননভিত্তিক আলোচনার যোগসূত্র তৈরি করেছে। হিন্দি এই স্তরে সেটা পারেনি। হয়তো মৌখিক স্তরে হিন্দি কিছুটা ছড়িয়েছে, কিন্তু মৌখিক ও লিখিত দুই স্তরে সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে ইংরেজি যেমন বিস্তার পেয়েছে হিন্দি তেমন পায়নি। হিন্দি ভারতে ব্যাপকতমভাবে ব্যবহৃত ভাষা, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে — অন্তত মৌখিকভাবে, এ তথ্য ভুল না হলেও। লেখার স্তরে হিন্দি ভারতের সর্বত্র যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, যেটা ইংরেজি হয়েছে।
তা ছাড়া ইংরেজির ‘সম্ভ্রম-মূল্য’ (prestige factor), ‘সুযোগ-মূল্য’ (opportunity factor) ইত্যাদিতে হিন্দি বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষা বেশ একটু পিছিয়ে। সেগুলি গত অর্ধশতক ধরে বহুচর্চিত, তা নিয়ে এখানে বাগ্বিস্তার করার দরকার নেই।
৩. ইংরেজির আধিপত্য ওরফে তার প্রতি আতিথেয়তা প্রত্যাহারের চেষ্টা
উপরের বিষয়গুলি অস্বীকার করে ভারতের শাসকেরা, বিজেপি শাসকেরা আগেকার শাসকদের তুলনায় একটু বেশি করে ইংরেজিকে গৌণ করে হিন্দিকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। তাদের যুক্তি নানা রকমের। এক, 'দেশপ্রেম' (!)। ইংরেজি ‘বিদেশি’ ভাষা এবং আমাদের পরাধীন ইতিহাসের ভাষা, ফলে তাকে যত তাড়াতাড়ি বিদায় দেওয়া যায় ততই ভালো। অন্তত তার স্থান সংকুচিত হোক।
তাদের পক্ষে আছে এই ঘটনাগুলি যে, পৃথিবীর বহু দেশ বহুলাংশে নিজেদের ভাষা দিয়েই কাজ চালায়। যেমন চিন, জাপান, রুশ, ইন্দোনেশিয়া থেকে ছোট ভিয়েতনাম পর্যন্ত। তার তালিকা গুগলে পাওয়া যাবে। ইংরেজি তারা শেখে না তা নয়, কিন্তু তার জন্য একটি বিশেষজ্ঞের গোষ্ঠী তারা স্থির করে রেখেছে, যারা নানা জ্ঞান ও ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য ইংরেজি থেকে তাদের ভাষায় অনুবাদ করে নেয়। তা ছাড়া চিনে, ভিয়েতনামে, জাপানে শুনেছি হাতের মোবাইলেই ইংরেজি থেকে অনুবাদ হয়ে যায়, বহিরাগত কেউ ইংরেজি লিখলে তা স্থানীয় ভাষায় তৎক্ষণাৎ লব্ধ হয়। তখন মোবাইলই দোভাষীর কাজ করে। এছাড়া ল্যাপটপ, ট্যাব ইত্যাদি তো আছেই। তাদের সর্বস্তরের শিক্ষাও হয় তাদেরই ভাষায়, ইংরেজিতে নয়, এ কথাটা মনে রাখা দরকার। ভারতের মতো এমন ইংরেজি লিখিত মুদ্রিত কথিত রূপের উপস্থিতি ও প্রাধান্য তাদের দেশে কোথাও নেই।
ভারতে এই ব্যবস্থাটা চালু (নিজের ভাষায় শিক্ষা সহ) চালু হওয়ার একটা অসুবিধে এই যে ভারত বহুভাষী দেশ। তাতে, যেমন বলেছি, নানা ভাষীদের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে এতদিন ইংরেজি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। শুধু মৌখিক বিনিময় নয়, লিখিত বিনিময়। লিখিত উপস্থিতি বিপুল। প্রথমত ইংরেজি ভাষায় বিপুল পরিমাণ বই ও সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়ে এসেছে, যেগুলির পাঠক সব ভাষার মধ্যবিত্তদের মধ্যেই বহু। তার একটা আভিজাত্য বা এলিট মূল্যও আছে। ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যও তৈরি হয়ে গেছে উন্নত মানের, এবং ভারতে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষারও বিপুল প্রসার ঘটেছে। স্বাধীনতার আগেকার চেয়েও সম্ভবত। তার ওই একই কারণ — ইংরেজি বিপুল সুযোগের ভাষা, তাই মর্যাদার ভাষা। অর্থাৎ একটা বিপুল আমানত তৈরি হয়েছে ইংরেজি ভাষার। আমাদের উল্লিখিত দেশগুলিতে সমান্তরাল কোনও দৃষ্টান্ত নেই ইংরেজির এই ব্যবহার ও প্রভাবের। আমরা এর আগে আমাদের নানা লেখায় দেখিয়েছি যে, ভারতে ইংরেজি শিক্ষা ‘বাবু’ আর ‘না-বাবু’ এই দু-ভাগে ভাগ করে দিয়ে ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে একটি মর্মান্তিক সামাজিক বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। বাবুদের কাছে না-বাবুরা প্রায় অবমানবের মতো গণ্য হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা হয়েছে ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণির অভিজ্ঞান। যারা ইংরেজি জানে না, তারা ভদ্রলোক নয়, ‘অশিক্ষিত’, ‘ছোটলোক’ ইত্যাদি। কিন্তু ভারতের ‘বাবু’ শ্রেণি এই বিষয়টা হয়তো খেয়ালই করেন না, বা খেয়াল করার যোগ্য মনে করেন না। তাই তাঁরা এই বিচ্ছেদ নিয়ে খুব-একটা উদ্বিগ্ন নন, তাঁরা এর প্রতিবিধানের কথা যেমন ভাবেন না, তেমনই ইংরেজির মধ্য দিয়ে প্রাপ্য সুযোগ ও সম্মানকে বর্জন করতে চান না। এটাকে আমরা সমালোচনা করতেই পারি, কিন্তু বাস্তবে ইংরেজির এই বিপুল বস্তুগত ও মানসিক ‘আমানত’কে রাতারাতি উবিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।
রাষ্ট্রের এখনকার বিজেপি প্রধানরা চান এই ইতিহাস অস্বীকার করে, ইংরেজিকে তার অবস্থান থেকে সরিয়ে হিন্দিকে তার জায়গায় বসানো হোক। সে চেষ্টা তাঁরা প্রায়ই নানা ছলছুতোয় করে চলেছেন। মনে রাখতে হবে, সংবিধানে ইংরেজিকে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে মাত্র পনেরো বছর (১৯৬৫ পর্যন্ত) রাখা হবে প্রথমে ভাবা হয়েছিল। তার পরে তাকে সরানোর নানা চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কোনও চেষ্টাই সফল হয়নি এ পর্যন্ত। এখন তাঁদের যুক্তি একটু ঘুরপথ ধরেছে, তারা ‘মাতৃভাষা’য় [৬] সমস্ত শিক্ষার জন্য ওকালতির সূত্রে ইংরেজির বিদায় চাইছেন। এই চাওয়াটা অন্যায় নয়, তথাকথিত মাতৃভাষায় শিক্ষা হলে যথার্থ শিক্ষা (জ্ঞানলাভ, ডিগ্রিলাভমাত্র নয়) হয় এ কথা সকল বিশেষজ্ঞই স্বীকার করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে শাসকশ্রেণির যে দ্বিচারিতাও আছে তাও লক্ষ করতে হবে। কী ২০১৯-এর খসড়ায়, কী ২০২০-র চূড়ান্ত শিক্ষানীতিতে তাঁরা কোথাও এ সম্বন্ধে কোনও প্রস্তাব দেননি। এ প্রস্তাব দিলে তাঁদের যে দায়িত্বগুলি নিতে হত তা এই — এক, শিক্ষানীতিতে ধাপে ধাপে ‘মাতৃভাষা’র মাধ্যমে শিক্ষার প্রস্তাব দেওয়া, দুই, অন্য মাধ্যমের স্কুলকে স্বভাষা মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া — অর্থাৎ, সব কমিটি-কমিশন যা নেই বলে আক্ষেপ করেছে সেই common school system-এর ব্যবস্থা করা (ধাপে ধাপে), তিন, সর্বস্তর আর সর্ব বিষয়ের জন্য ‘মাতৃভাষা’য় প্রচুর পাঠ্যবই প্রস্তুত ও অনুবাদ করা, চার, ইংরেজিতে শিক্ষিত শিক্ষকদের ‘মাতৃভাষা’ পড়ানো ও পরীক্ষা নেওয়াতে প্রশিক্ষিত করতে হবে (সকলে মাতৃভাষায় তেমন সড়গড় নাও হতে পারেন) — তার সঙ্গে শিক্ষা ও অন্যান্য প্রশাসনে ‘মাতৃভাষা’ চালু করতে হবে। সেই সঙ্গে দেশের এলিটদের ইংরেজির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর কঠিন এক প্রচার-প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। বলতে হবে যে, ইংরেজি (ভাষা, সাহিত্য নয়) আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যপাঠ্য থাকবে, কিন্তু বিষয় আমরা শিখব ‘শি-মাতৃভাষা’য়। ইত্যাদি ইত্যাদি। জানি না, এই কাজে তাঁরা কবে অগ্রসর হবেন বা আদৌ হবেন কি না।
ততদিন সংবিধানের যে বিকল্প আছে তার অধিকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য বজায় রাখা উচিত। অর্থাৎ যারা চাইবে, ইংরেজি ব্যবহার করবে, কেন্দ্রীয় সরকারও তাদের সঙ্গে ইংরেজি ব্যবহার করতে বাধ্য থাকবে। এর মধ্যে পার্লামেন্টারি ও অন্যান্য কমিটিতে হিন্দিতে কেন্দ্রীয় সংস্থা — আইআইটি, পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউট, এআইএমএস ইত্যাদিতে পড়াশোনা ও গবেষণা চালানোর, ফাইল তৈরির যে চেষ্টা চলেছে তা আমরা অনৈতিক বলেই মনে করি। এতে হিন্দি মূলভাষীদের অন্যদের তুলনায় সুবিধে বেশি হবে, হয়তো চাকরির সুযোগও বাড়বে। ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ হিসেবে ইংরেজি সব জায়গাতেই রাখা হোক। রাজ্যের শিক্ষা ও অন্যান্য সংস্থাগুলিতে রাজ্যের ভাষা ও ইংরেজি বিকল্পের সুযোগ থাক, যারা সে বিকল্প চাইবে। হিন্দিভাষী রাজ্যেও ইংরেজি বিকল্প থাকা উচিত, অন্য ভাষার মানুষের সমান সুযোগের জন্য।
৪. নিজেদের ভাষার প্রতি আমরা কতটা অতিথিপরায়ণ?
কিন্তু স্ট্যালিন এবং অন্যদের এ কথাটা নিশ্চয়ই ভাবা উচিত, ভাবেন কি না জানি না, যে, ইংরেজিও ইতিহাসে বিশ্ববিখ্যাতভাবে একটি ‘খুনি ভাষা’ (killing language), যা পৃথিবীর বহু ভাষার বিলোপের কারণ হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়। ভারতে সে তা পারেনি, তার কারণ আমরা অন্যত্র বলেছি। কিন্তু তার প্রতি অতিভক্তি আর অত্যাসক্তি আমাদের ভাষাগুলিরও ক্ষতি করতে পারে, সেটা আমাদের যেমন, তেমনই আমাদের নেতাদেরও খেয়াল রাখতে হবে। এ কথা আমরা বলি ইংরেজি শিক্ষার ফলে আমাদের বাংলা বা ভারতীয় অন্যান্য ভাষাও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে — এই ঋণ সকৃতজ্ঞভাবে স্মরণে রেখেই। সেই সমৃদ্ধির অহংকার মনে রেখেই ‘বাংলিশ’ শুনে আমাদের গদগদ হওয়ার সুযোগ যেমন কম, তেমনই শহর অঞ্চলে ইংরেজি-মাধ্যম ভক্ত অভিভাবকদের বাংলাটা ভুলিয়ে বা নিজের ভাষাকে তুচ্ছতায় ঠেলে ইংরেজি শেখানোর প্রবণতাতেও সুখী হওয়ার কোনও কারণ দেখি না। আমরা জানি বাংলায় যেমন 'বাংলিশ' চলে, হিন্দিতেও তেমনি 'হিঙ্গ্লিশ' বা তামিলে 'টামলিশ' বলে একটি খিচুড়ি ভাষা চলে। ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও এর হাজিরা ভালোই আছে। এই খিচুড়ি ভাষা ভাষার একটি ব্যাধি, তা 'ইউনেস্কো'র নিদানে আছে। তা ইংরেজির দক্ষতা যেমন প্রমাণ করে না, তেমনই নিজের ভাষা সম্বন্ধে অবহেলাকেও প্রমাণ করে। স্ট্যালিন মশাই সে বিষয়টি নিয়ে ভাবিত কি না তা জানতে পারলে ভালো লাগত।
সকলে মানবেন কি না জানি না, আমাদের মতে এই খিচুড়িব্যাধির নিরাময়ের একমাত্র উপায় 'শি-মাতৃভাষা'র মাধ্যমে সবরকম লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে, পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাটাকে খুব ভালো করে শেখানো। তাতে মাতৃভাষাকে আমরা মূল্যবান মনে করে সম্মান করতে শিখব। স্কুল স্তর থেকেই, এবং স্কুল স্তরেই। দশ বছরে যদি একটা বিদেশি ভাষা ভালো করে বলতে পড়তে লিখতে শেখাতে না পারি তবে আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনায় গলদ আছে ধরতে হবে। ভাষাশিক্ষকেরা কী বলেন? [৭]
টীকা:
১. দ্র. Halliday, M. A. K., Angus McIntosh, Peter Stevens-এর কথা — "Essentially, any language, in the sense that every language is equally well-adapted to the use to which the community puts it”. Fishman, Joshua (সম্পা.), 1968, Readings in the Sociology of Language, (The Hague, Mouton) বইয়ে তাঁদের প্রবন্ধ “The Users and Use of Language”, (p. 160).
২. উর্দু আর হিন্দি ব্যাকরণগতভাবে দুটি আলাদা ভাষা কি না সন্দেহ। দুটি এক সময় মুখে ‘হিন্দুস্থানি’ নামে একইভাষা হিসেবে গণ্য হত। পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাশীর পণ্ডিতেরা তাতে আরবি-ফারসি শব্দ বাদ দিয়ে সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়ে তার ‘শুদ্ধিকরণ’ করে আর ভাষার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদও তৈরি করে। আর দেবনাগরি লিপি ব্যবহার করতে শুরু করে। এই ভাষা যে আরবি লিপিতেও লেখা হত তার প্রমাণ হিন্দি ভাষার প্রখ্যাত লেখক প্রেমচন্দের অভ্যাস। তিনি তাঁর প্রথম কয়েকটি গল্প আরবি লিপিতেই লিখে ছাপিয়েছিলেন।
৩. আগ্রহী পাঠক আমার 'ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ' (দে’জ, ২০১৮) বইয়ের ১৬৫-১৯২ পৃষ্ঠার আলোচনা দেখতে পারেন।
৪. পুনরপি, আগ্রহী পাঠকেরা ‘ভাষা-পরিকল্পনা’ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানের জন্য আমার 'ভাষা দেশ কাল' বইটি (মিত্র ও ঘোষ) দেখতে পারেন।
৫. দেবনাগরি অক্ষরে হিন্দি কথাটি সংবিধানকে যে বলতে হল, তাতেই আমাদের ২ নম্বরের পর্যবেক্ষণের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এটা প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করা হয় যে, হিন্দিও এক সময় উর্দু/আরবি হরফে লেখা ও ছাপা হত। ‘হিন্দুস্থানি’ নামে ওই ভাষাটিই ছিল হিন্দি-উর্দুর যুগ্ম রূপ।
৬. যাকে আক্ষরিক অর্থে ‘মাতৃভাষা’ বলে তা যে সব সময় শিক্ষায় ব্যবহৃত হয় না, এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা 'নানা ভাষা নানা মত' (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০২৫) বইটি দ্রষ্টব্য। আমরা সে জন্য ‘শি-মাতৃভাষা’ কথাটি ব্যবহার করেছি।
৭. আমরা বহুবার বলেছি, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা হবে আমাদের লক্ষ্য, সাহিত্য নয়। আধুনিক ইংরেজি শেখার জন্য যেটুকু ইংরেজি সাহিত্য প্রয়োজন তা নিশ্চয়ই ব্যবহার করা হবে। কিন্তু লক্ষ্যটা আসলে ভাষাশিক্ষা, সাহিত্যশিক্ষা নয়। সেটা বিশেষ পাঠ্য, তা যারা পড়তে চাইবে তারা পরে কলেজ স্তরে পড়তে পারবে। আর এ কথাও ক্রমশ স্বীকৃতি পাচ্ছে যে, শুধু ইংরেজি সাহিত্য কেন, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কেন আমরা পড়ব না? নিজের ভাষায়, ইংরেজিতে, মূল ভাষায়?