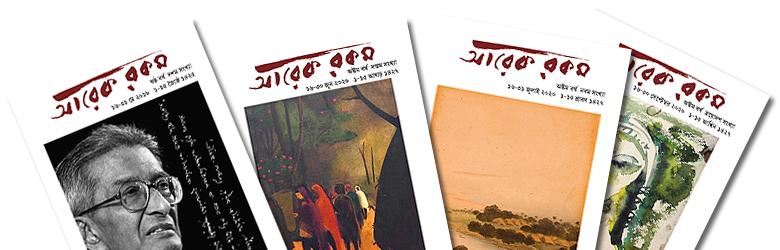আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা ● ১-১৫ মার্চ, ২০২৫ ● ১৬-২৯ ফাল্গুন, ১৪৩১
প্রবন্ধ
নব্য উদার অর্থনীতি ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতি
গৌতম সরকার
২০০২ সালে জোসেফ স্টিগলিজের লেখা একটা বই, ‘গ্লোবালাজেশন অ্যান্ড ইটস ডিসকন্টেন্টস’, যেখানে সাম্প্রতিক বিশ্বায়ন সম্পর্কে ক্রমাগত বাড়তে থাকা অসন্তোষ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাপারটি বেশ বিস্ময়কর, কারণ কয়েক দশক আগেই অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্বায়নকেই অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নের একমাত্র টোটকা হিসেবে পরামর্শ দিয়েছিল। রুশভেল্ট ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক-গবেষক স্ট্যানলি গ্রিনবার্গ এবং তাঁর সহকর্মীদের একটি গবেষণাপত্র থেকে জানা যায়, বেশিরভাগ আমেরিকানদের কাছে বিশ্বায়নের প্রতি অনীহার মূল কারণ হল উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, একই ছবি পরিলক্ষিত হয় ইউরোপের ক্ষেত্রেও।
এখন কথা হল, কি এমন ঘটল যার ফলে মাত্র কয়েক দশক আগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দাওয়াই উল্টো ফল দিতে শুরু করল? নয়া উদারবাদী অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য, মুক্ত বাণিজ্যের দুনিয়ায় মানুষ আগের থেকে অনেক ভালো আছে, এটা হয় তারা বুঝতে পারছে না, নয়তো বুঝতে চাইছে না। তাঁদের মতে সমস্যাটা মোটেই আর্থিক নয়, বরং মানসিক। কিন্তু বৈশ্বিক আয়-সংক্রান্ত তথ্য বলছে, উন্নত দেশগুলিতে আয়ের নিরিখে নিচের তলার ৯০ শতাংশ মানুষের উপার্জন বিগত চার দশক ধরে একই জায়গায় আছে। একজন পূর্ণ সময়ের শ্রমিকের গড় প্রকৃত আয় গত ৪২ বছরের তুলনায় বাড়েনি, বরঞ্চ কমে গেছে। নিচের তলার মানুষদের প্রকৃত আয় ষাট বছর আগের প্রকৃত আয়ের সমতুল। ব্রাঙ্কো মিলানোভিচ তাঁর নতুন বই, 'গ্লোবাল ইনইকুয়ালিটিঃ অ্যা নিউ অ্যাপ্রোচ ফর দ্য এজ অফ গ্লোবালাইজেশন'-এ ১৯৮৮-২০০৮ এই দুই দশকে আয়ের নিরিখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিজয়ী ও বিজিতদের চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে সমাজের উপরতলার মাত্র এক শতাংশ প্রভাবশালী ও সম্পদশালী ব্যক্তিগণ (প্লুটোক্র্যাটস) হচ্ছেন আসল লাভবান আর পরাজিতের দলে, যাদের কপালে আর্থিক সংস্কার বা উদার অর্থনীতির প্রসাদ কণামাত্র বা কিছুই জোটেনি তারা হল উন্নত দেশগুলোর নিচের তলার আপামর দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রমিক সম্প্রদায়। বিশ্বায়ন হয়তো এই হয়রানির একমাত্র কারণ নয়, তবে অন্যতম কারণ তো বটেই। তাই সমস্যার শিকড় অতি গভীরে প্রোথিত সন্দেহ নেই।
সম্প্রতি পৃথিবী জুড়ে একটা ফ্যাসিবাদী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদিও এই প্রবণতাকে উদারবাদীরা ভুলেও ফ্যাসিজম বলেননা, এই নয়া ঢেউকে নতুন নতুন নামে সম্বোধিত করা হচ্ছে, যেমন - জাতীয়তাবাদী, উগ্র জাতীয়তাবাদী, কিংবা পপ্যুলিস্ট, ডানপন্থী পপ্যুলিস্ট ইত্যাদি। এদের কখনই 'ফ্যাসিস্ট' বলে উল্লেখ করা হয়না, যদিও এই মুহূর্তে সারা বিশ্বজুড়ে চলতে থাকা ফ্যাসিজমের প্রবণতাকে খাতায় কলমে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ইতালিতে মেলোনি, জার্মানিতে অল্টারনেটিভস ফর জার্মানি, তুরস্কের এর্দোয়ানে, যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, এমনকি ভারতের নরেন্দ্র মোদিজীকেও এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক করা যায়। বিষয়টি একটু খোলসা করা যাক।
১৯৩০-এর মহামন্দার দশকে ফ্যাসিজমের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেত, সেসব বিভিন্নরূপে বিভিন্ন দেশে এখনও বিদ্যমান। ফ্যাসিজমের বৈশিষ্ট্য হল, কোনও একটি সংখ্যালঘু দূর্বল সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করে হেনস্থা করা। এই চিহ্নিতকরণ ধর্ম, জন্ম কিংবা চামড়ার রঙের ভিত্তিতে হতে পারে। মূল উদ্দেশ্য হল উদ্দিষ্ট দুর্বল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ক্ষেপিয়ে তুলে বিভিন্ন দিক দিয়ে আক্রমণ করা। অর্থাৎ ফ্যাসিজমের মোড়কে একটা দমনমূলক স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার সুচতুর ব্যবস্থা। দমনের স্বার্থে এরা কেবলমাত্র রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ব্যবহারের উপর ভরসা করে না, ফ্যাসিবাদী গুণ্ডাবাহিনীর এক সুবিশাল চক্র অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রশক্তির আস্তিনে লুকোনো থাকে। এছাড়া ফ্যাসিবাদ হল একচেটিয়া পুঁজি সৃষ্টির অন্যতম লাভজনক ব্যবসা। সবকিছু ঠিকঠাক চললে পরিশেষে একজন স্বঘোষিত অতন্দ্র ক্ষমতাশালী নেতার উত্থান ঘটে, যার হাত ধরে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের সলিলসমাধি ঘটে ফ্যাসিজম চূড়ান্ত রূপ পায়। এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভারতের নরেন্দ্র মোদিজীর সাথে আরও অনেকের নাম উঠে আসে।
আমেরিকাকে পুনর্বার দুনিয়ায় একনম্বর করার লক্ষ্যে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে শাসনভার গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই মসিহার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কঠিন অভিবাসন নীতি, শুল্ক যুদ্ধ, সংকুচিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, দেশীয় সম্পদ ও শক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার ইত্যাদি নীতিগুলি তারই পরিচয় বহন করে। এমনটা আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও সত্যি। নানা-ভাষা নানা-মত নানা-পরিধানের দেশ ভারতে বিজেপির উত্থানের মূল কারণ হিসেবে আদবানির রথযাত্রাকে উল্লেখ করা হয়, তেমনি নরেন্দ্র মোদির দলের প্রধান হয়ে ওঠার পিছনে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাকে অস্বীকার করা যায়না। এই ব্যাপারে ইউরোপের দেশগুলিও পিছিয়ে নেই। ওই মহাদেশের তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতি ইতালির দিক চোখ ফেরালে দেখা যাবে তাদের নির্বাচিত মুসোলিনির কট্টর সমর্থক প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ফ্যাসিবাদী উত্তরাধিকার বহন করছেন। মুসোলিনির রোম দখলের ঠিক সত্তর বছর বাদে মেলোনি নির্বাচনে জয়ী হন। এবার ইতালি ভূখণ্ড ছেড়ে আরেকটু এগিয়ে গেলে এইরকম আরও অনেক লক্ষণ চোখে পড়বে। ফ্রান্সে এতদিন যে সংগঠনকে সবাই 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' বলে চিনত তারাই এখন 'ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স' বলে পরিচিতি লাভ করেছে। সেই দলের নেত্রী মারিয়েল লাপেল উগ্র দক্ষিণপন্থী দলের প্রতিভূ। জার্মানিতে 'অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি' দলটি নির্বাচনে ১৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এখানে তুরস্কের কথাও উঠে আসে, সেখানে মসনদ আলো করে বসে আছেন রিসেপ ত্যাগিপ এর্দোয়ান। ওদিকে স্পেনের সংসদ নির্বাচনে তৃতীয় বৃহত্তম দলটি একইরকম রাজনৈতিক লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। সুইডেনেও এই ধরনের একটি রাজনৈতিক দল মাথাচাড়া দিচ্ছে। এরা সকলেই নয়া ফ্যাসিবাদী ধাঁচের পার্টি, যারা কোথাও কোথাও সরকার গড়েছে, আবার কোথাও কোথাও দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে থেকে বাইরে থেকে দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে সরকার গড়তে সমর্থন যুগিয়ে নিজেদের অস্তিস্ত্ব জাহির করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
দক্ষিণপন্থা রাজনীতি নতুন কিছু নয়। তবে নয়া দক্ষিণপন্থার সাথে সাবেক দক্ষিণপন্থার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সাবেক দক্ষিণপন্থীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমাজে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখে শাসক শ্রেণির কায়েমী স্বার্থকে ধরে রাখা। অন্যদিকে আজকের দক্ষিণপন্থা যেটিকে উগ্র দক্ষিণপন্থা আখ্যা দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, মানুষের মনোভাবকে ক্রমশ প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। নয়া উদারবাদের ধাক্কায় ইউরোপে সাবেক শ্রমিকশ্রেণি ইতিমধ্যেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এর উপরে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির দাপটে ইউরোপ থেকে ভারী শিল্প অনেকটাই হারিয়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তনের কারণে অনেক কাজকর্মই উন্নয়নশীল দেশের মাটিতে চলে যাচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল উদার অর্থনীতিতে মুনাফার সন্ধানে লগ্নিপুঁজির অবাধ পরিচলন।
এভাবেই জনজীবনে ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়। সেইসব দিশেহারা মানুষগুলোর দুর্গতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদের মধ্যে ফ্যাসিজমের বা উগ্র দক্ষিণপন্থার বীজ পুঁতে দিতে সুবিধা হচ্ছে। একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে দেশের সমস্ত দুর্দশার জন্য তাদের দায়ী করা হয়। ভারতে অতি দক্ষিণপন্থার আক্রমণের মূল লক্ষ্য হল ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। এই রাজনৈতিক আদর্শ মূলত দেশের জনগণের সংখ্যাগুরু অংশের জাতিগত, ধর্মীয় ও সংস্কৃতিগত পরিচয়কে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল, তার থেকে বর্তমান সরকারের জাতীয়তাবাদের মূল তফাৎ এখানেই। হিন্দুরাষ্ট্রের ধুয়ো তুলে বাকিদের বহিরাগত বলে দাগিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পটভূমি তৈরি করে সাধারণ মানুষকেও লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছে, সরকারের অপারগতা নিয়ে জনসাধারণ কম সন্দিহান হচ্ছেন, ফলে সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে সেটা ভাবার পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। এটা শুধু ভারত নয় সামগ্রিক বিশ্বের জন্য খুব বড় বিপদের সংকেত।