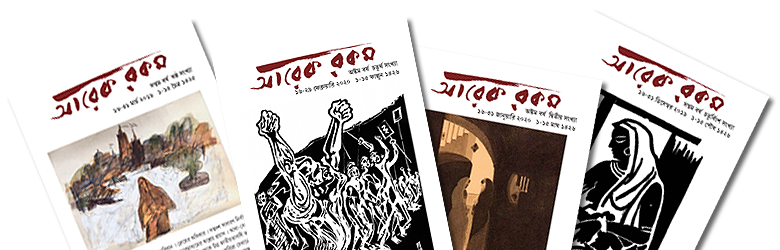আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ● ১৬-২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ● ১-১৫ ফাল্গুন, ১৪৩১
প্রবন্ধ
দ্য ভেজিটেরিয়ানঃ এক সাধারণ নারীর অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প
গৌতম সরকার
একদিন এক ব্যক্তি কাজ থেকে বাড়ি ফিরে দেখল, তার স্ত্রী একটা গাছে পরিণত হয়ে গেছে। ব্যাপারটা লোকটিকে ভীষণভাবে পীড়িত করল। কী করবে ভেবে না পেয়ে গাছটিকে পরম যত্নে একটা টবে বসালো। নিয়মিত পরিচর্যায় গাছটিতে ফুল ধরল, সেই ফুল থেকে ফল হল। ফল পরিণত হলে তার বীজ আরেকটি টবে পুঁতে দিল। সেই বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটল, একটা চারাগাছ জন্মালো। আলো, বাতাস পেয়ে চারাগাছটি আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন পর কোনও এক অজ্ঞাত রোগে শিশুগাছটি জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে মরে গেল। প্রায় তিরিশ বছর আগে 'দ্য ফ্রুট অফ মাই উওম্যান' অর্থাৎ 'আমার মেয়েমানুষের ফল' নামক ছোটগল্পটি কোরীয় ভাষায় লিখেছিলেন হান কাং। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে এই গল্পটির পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত রূপদান করেন ‘দ্য ভেজিটেরিয়ান’ উপন্যাসে। ২০১৫ সালে এই উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ বেরোনোর পর বিশ্বের সাহিত্যিক মহলে হান কাং-এর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর স্বকীয়, গভীর কাব্যময় গদ্যের স্টাইল সাহিত্য বোদ্ধা ও পাঠকমহলে রীতিমতো সাড়া ফেলে। ২০২৪ সালে সেই হান কাং 'সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার' লাভ করে তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পেলেন।

‘দ্য ভেজিটেরিয়ান’ হল এক কোরীয় রমণী ইয়ং হাইয়ের ‘মেটামরফসিস’-এর গল্প। গল্প শুরু হয় ইয়াং হাইয়ের মাংস খেতে অস্বীকার করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের শুরুর লাইনটি পাঠককে গল্পটি সম্বন্ধে আগ্রহী করে তোলে, যেখানে ইয়ং হাইয়ের স্বামী বলছেন, "আমার স্ত্রী মাংস না খাওয়ায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমি তাকে সবসময় সবদিক থেকে অতি সাধারণ মনে করতাম"। ইয়ং হাইয়ের গতানুগতিক জীবন হঠাৎ করে এক পরিবর্তনের বাঁকে এসে উপস্থিত হওয়ার পিছনে আছে একটি স্বপ্ন। যে দুঃস্বপ্ন রাতের পর রাত তাকে এক অন্ধ আবর্তে তাড়া করে ফেরে। একটা কসাইখানা, যেখানে আলোর চেয়ে অন্ধকার অনেক বেশি, সারি সারি মাংস ঝোলানো রয়েছে, কাঁচা মাংস থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরছে, আর সেই রক্তে ইয়ং হাইয়ের হাত, পা, মুখ, মুখগহ্বর মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। কাঁচা রক্তের রং, তাজা গন্ধে ইয়ং হাইয়ের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই প্রায়ান্ধকার স্লটার হাউসে সে ছাড়া আর কোনও জনপ্রাণী নেই। শুধু সে আর রাশি রাশি কাটা মাংস৷ ভীষণ আতঙ্কে ইয়ং হাই কসাইখানা থেকে বেরোনোর দরজার সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না। এই স্বপ্ন সাতাশ বছরের তরুণীকে একটা সত্যে পৌঁছে দেয়, নিছক বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অন্যের জীবননাশ যেমন অহেতুক তেমনি অন্যায়, ফলে বেঁচে থাকাটাই তার কাছে আস্তে আস্তে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।
‘দ্য ভেজিটেরিয়ান’-এর পথ ধরেই হান কাং-এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, আবার সেই স্বীকৃতির পথ ধরেই নোবেল পুরস্কার লাভ। তাঁর লেখনী ইতিহাসের যন্ত্রণাদগ্ধ ঘটনাকে উপজীব্য করে মানবজীবনের ভঙ্গুরতাকে পরতে পরতে উন্মোচন করে, জীবনের উত্থান-পতন, হাসি-বেদনা, অনুভূতি-উপলব্ধি, সামাজিক অনুশাসন ও ট্রমা নিরীক্ষাধর্মী ও কাব্যময় গদ্যে এক ব্যতিক্রমী সংযোজন ঘটিয়ে তাঁর সাহিত্যকে এক অনন্য স্তরে পৌঁছে দেয়। হান কাং-এর সমস্ত কাজ বিভিন্ন ধরনের শৈলীকে একত্র করে নতুন কিছু সৃষ্টি করেছে। তাঁর লেখনী নৃশংসতা, শোক ও পিতৃতন্ত্রের মতো বিষয়গুলোকে উন্মুক্ত করে, জীবিতের সাথে মৃতের, পার্থিবের সাথে অপার্থিবের এক বৌদ্ধিক সংযোগ ঘটিয়ে ছকে বাঁধা সাহিত্যের গণ্ডি কাটিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে অন্য মার্গে পৌঁছে দেয়।
লেখিকা সমগ্র উপন্যাসকে তিনটি সুবিন্যস্ত পর্যায়ে ভাগ করেছেন।। প্রথম পর্বের নাম, ‘দ্য ভেজিটেরিয়ান’, এখানে ইয়ং হাইয়ের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তাঁর স্বামী, বাবা, মা, বোন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম, ‘মঙ্গোলিয়ান মার্ক’, যেখানে তাঁর জামাইবাবু তাকে একজন সন্তের প্রশান্ত রূপের সাথে তুলনা করেন এবং সুচতুরভাবে নিজের প্রয়োজনে ইয়ং হাইকে ব্যবহার করেন এবং শেষ পর্বটির নাম, ‘ফ্লেমিং ট্রিস’, এই পর্বে লেখিকা তাঁর মূল চরিত্রের সর্বোচ্চ ত্যাগের মধ্যে দিয়ে মোক্ষলাভ ঘটিয়ে একটি গাছে রূপান্তরণের ছবি এঁকেছেন।
প্রথম পর্বঃ দ্য ভেজিটেরিয়ান
ইয়ং হাইয়ের রাতারাতি নিরামিষাশী হয়ে ওঠার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে তাঁর স্বামীকে। এখানে লেখিকা স্বামীকে একজন স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব, হৃদয়হীন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই সিদ্ধান্তে স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক পরিণতি নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত না হয়ে সমাজ তাঁর স্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে কীভাবে নেবে, তার জন্য নিজের সামাজিক সম্মান কতটা ক্ষুণ্ণ হবে, বাড়িতে মাংস রান্না বন্ধ হয়ে গেলে তিনি কী খেয়ে বেঁচে থাকবেন এই সমস্ত ভাবনাগুলো তাঁকে পাগল করে তুললো। এর সাথে আরেকটি ব্যাপার ঘটল, ওই ঘটনার পর ইয়ং হাই ব্রা পরা ছেড়ে দিল, এটি তার স্বামীর কাছে নতুন করে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াল। সামাজিক এবং পারিবারিক জমায়েতে স্বামীর একমাত্র চিন্তা জামার ওপর দিয়ে তার স্ত্রীর স্তনবৃন্ত দেখা যাচ্ছে কিনা। ওদিকে ইয়ং হাইয়ের বাবা-মা মেয়ের নিরামিষাশী হয়ে ওঠার সিদ্ধান্তে যারপরনাই বিচলিত হলেন। এক পারিবারিক জমায়েতে মাংস খেতে অস্বীকার করায় তার মা চিৎকার করে বলে উঠলেন, "এই জগতে হয় তুমি মাংস খাবে নয়তো এই জগৎ তোমাকে খেয়ে ফেলবে"। মেয়ের জেদ সহ্য করতে না পেরে একবগ্গা, কর্তৃত্ববাদী বাবা জোরপূর্বক মেয়ের মুখে একটুকরো মাংস ঢুকিয়ে দেয়। এই জবরদস্তিতে ইয়ং হাই পাগলের মতো আচরণ শুরু করে, এমনকি একসময় ব্লেড দিয়ে হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করে।
এখানে ইয়ং হাই-এর মায়ের প্রতিক্রিয়াটি প্রণিধানযোগ্য। "তুমি খাদক হবে নয়তো তুমি খাদ্যে পরিণত হবে", এই বোধ কোরীয় সমাজের এক নগ্ন চেহারা তুলে ধরে। আসলে ‘দ্য ভেজিটেরিয়ান’ গল্পটি নিছক এক মানুষের নিরামিষাশী হয়ে ওঠার গল্প নয়, এটি সনাতন সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের শর্তে বাঁচতে চাওয়ার পরিণতি কতটা যন্ত্রণাদগ্ধ হতে পারে তা’র গল্প। এটি এক উপলব্ধির গল্প যেখানে বেঁচে থাকার অপরিহার্যতাকে না মেনে জীবন থেকে সরে আসার গল্প। ইয়ং হাইয়ের গল্প মাংস খাওয়া বন্ধ থেকে শুরু হলেও উপন্যাস যত এগোয় আস্তে আস্তে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ত্যাগের পথে এগোতে থাকে।
দ্বিতীয় পর্বঃ মঙ্গোলিয়ান মার্ক
কোরীয় সংস্কৃতি হল প্রশ্নহীনভাবে সামাজিক রীতিনীতি আদব-কায়দাকে অনুসরণ করা। মানবজীবনের সারসত্য হল ভোগ; নিজস্ব সম্পদ, ক্ষমতা ও সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার ঘটিয়ে সর্বোচ্চ আনন্দ ও সুখ উপভোগ জীবনের মোক্ষ। সেই স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা বা স্বাভাবিকতার পথে না চলে নিজের মতো পথচলা পরিবার, সমাজ মেনে নেবে না। সেই অচলায়তনের সুউচ্চ প্রাচীরের বাইরে এসে স্বাধীন পথ চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘরে-বাইরে তুমুল অসন্তোষ ও অশান্তি যখন ইয়ং হাইকে তার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারল না, বরঞ্চ সার্বিক বিরোধিতা তাকে ত্যাগ ও মোক্ষের জগতে আরও কয়েক পা এগোতে সাহায্য করল, তখন ওই টালমাটাল মানসিক পর্বে ইয়ং হাইয়ের জীবনে উপস্থিত হলেন তাঁর বড়দিদি ইন হাইয়ের স্বামী, যাকে লেখিকা কোনো নামে সম্বোধন করেননি; যিনি উপন্যাসে 'তিনি', 'তার' ইত্যাদি সর্বনামে সম্বোধিত হয়েছেন। এখান থেকেই কাহিনীর দ্বিতীয় পর্ব শুরু।
দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়ং হাইয়ের আমিষ গ্রহণে অনীহা থেকে বেঁচে থাকার অনীহায় রূপান্তরণ। প্রথম পর্বের শেষে তাঁর পরিবারের লোকেদের সতর্কবাণী ছিল, একজন সংসারত্যাগী সাধুপুরুষকেও দীর্ঘ অভ্যাস, সাধনা ও যোগসাধনার মধ্যে দিয়ে নিরামিষাশী হয়ে ওঠার প্রয়াস চালাতে হয়। সেইসময় তার জামাইবাবু তার মধ্যে সাধ্বীর প্রশান্ত রূপ আবিষ্কার করেন যেটা ইয়ং হাই বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং ত্যাগ এবং তিতিক্ষার মার্গে আরও বেশি এগিয়ে যায়। কেউ কেউ এই পর্বে ইয়ং হাইয়ের মধ্যে বৌদ্ধিক প্রশান্তি খুঁজে পান। বৌদ্ধধর্মে কষ্ট বা যন্ত্রণার মূল কারণ হিসেবে পার্থিব কামনা-বাসনাকে চিহ্নিত করা হয়। এটি ওই ধর্মের চারটি সত্যের মধ্যে একটি। এই কাহিনীতে যেহেতু ইয়ং হাই নিজেকে পার্থিব কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পেরেছিল, তাই একজন পাঠক এই কাহিনীকে তার বোধিসত্ত্বে উন্নীত হওয়ার গল্পের আখ্যান হিসেবে ধরে নিতে পারে। তবে এরপরও ইয়ং হাই নিস্তার পেল না, তার অস্থির মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজের জামাইবাবু তার সাথে যৌনখেলায় মেতে উঠলেন৷
ভদ্রলোক একজন আর্টিস্ট, বিশেষ করে ডানাযুক্ত প্রাণী তাঁর আঁকার মূল বিষয়বস্তু। তিনি শ্যালিকার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ইয়ং হাইয়ের বিবর্তিত বিক্ষিপ্ত মানসিকতার সুযোগে তাঁর নগ্ন শরীরে ছবি আঁকতে এবং সমগ্র বিষয়টি ভিডিও রেকর্ডিং করাতে রাজি করান। একসময় নিজের শরীরও একইরকম চিত্রবিচিত্রে রাঙিয়ে লাইভ ক্যামেরার সামনে দুজনে যৌনমিলনে রত হন। এই ঘটনা ইয়ং হাইয়ের মনে চূড়ান্ত আঘাত আনে এবং সেখান থেকেই তার মেটামরফসিসের দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় স্তরে স্থানান্তর ঘটে আর একই সাথে লেখিকা দ্বিতীয় পর্বের যবনিকা টেনে পাঠককে তৃতীয় পর্বে নিয়ে যান।
তৃতীয় পর্বঃ ফ্লেমিং ট্রি’স
প্রথম পর্বে ইয়ং হাই একজন অতি সাধারণ মানুষ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে, বিশেষ করে তাঁর স্বামীর কাছে সে ছিল এক এলেবেলে মহিলা যাকে আলাদা করে খেয়াল রাখা বা যত্ন নেওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই সাধারণ মহিলার সাধ্বী রূপে রূপান্তরণ পেরিয়ে তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সে নিজেকে একটা বৃক্ষ বলে মনে করতে শুরু করে। সারা শরীর ফুলের ছবিতে রঞ্জিত হওয়ার পর ইয়ং হাই কসাইখানার সেই ভয়ানক স্বপ্ন থেকে মুক্তি পায় এবং বিশ্বাস করতে শুরু করে তার নিরামিষাশী হয়ে ওঠার কারণেই এটা ঘটেছে। সারা শরীর জুড়ে লতাপাতা ফুলফল নিয়ে ইয়ং হাই তাঁর কল্প পৃথিবীতে আস্তে আস্তে একটা গাছে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাদের ‘পেইন্টেড সেক্স’-এর ভিডিও জনসমক্ষে এলে মানসিকভাবে অসুস্থ মহিলার সাথে যৌনমিলনের কারণে ভদ্রলোকের হাজতবাস হয় এবং ইয়ং হাইকে মানসিক হাসপাতালের আবাসিক বিভাগে ভর্তি করা হয়। সেই হাসপাতাল থেকে একদিন সে হারিয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায়, অবিরাম বৃষ্টিধারা তার সারা শরীর জুড়ে বয়ে চলেছে, আর সেই গম্ভীর নৈঃশব্দের মধ্যে সে একটি বৃক্ষের মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে।
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইয়ং হাই খাবার খাওয়া এবং কথাবলা একদম বন্ধ করে দিল। তার বোন একদিন তাকে হাসপাতালে দেখতে এলে ইয়ং হাই ফিসফিস করে বলল, "আমার আর খাবার লাগবে না, শুধু একটু জল আর সূর্যের আলো পেলেই হবে"। উপন্যাসের শেষে লেখিকা দিদি ইন হাইয়ের যন্ত্রণা ও ত্যাগের ছবিটিও দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন৷ স্বামীর সাথে বোনের যৌনমিলনের ভিডিও দেখার পরও তাঁর মনে বোনের জন্য বেশ কিছুটা এবং স্বামীর জন্য অল্পবিস্তর করুণা ও সহানুভূতি ফিরে এসেছিল। শেষ সময়ে ইয়ং হাইয়ের পাশে ছিলেন, যখন হসপিটাল স্টাফেরা পাশবিক বলপ্রয়োগে তাকে তার বোনকে খাওয়াতে এবং ইনজেকশন দিতে চেষ্টা করছে এবং ইয়ং হাই আতঙ্কে শব্দহীন জান্তব আওয়াজ করছে তখন সে চিৎকার করে সবাইকে সরিয়ে বোনকে আঁকড়ে ধরছে। হয়তো সে ইয়ং হাইয়ের মত প্রত্যাহার ও ত্যাগের পথে হেঁটে বোধিসত্ত্বের চূড়ায় পৌঁছতে পারেনি, কারণ তাকে বাস্তবের মাটিতে পা রেখে নিজের সন্তান ও অসুস্থ বোনের দেখভাল করতে হয়েছে, সমস্ত লজ্জা, অপমান ও যন্ত্রণা ভুলে বারবার বোনের টানে হাসপাতালে ছুটে যাওয়া সংসারে টিকে থেকে মোক্ষলাভের আরেক রূপ, সেটি লেখিকা ছোট পরিসরে ইন হাই চরিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছেন। এখানে পাঠকের অজান্তে কখন যেন দুই বোন সমান্তরাল হয়ে ওঠে।

লেখিকা হান কাং
হান কাং-এর ‘দ্য ভেজিটেরিয়ান’ উপন্যাসের মূল উপজীব্য হল, কোরীয় দর্শনে সামাজিক সামঞ্জস্য ও স্বাভাবিকতা ধরে রাখতে যে নিরলস এবং আপোসহীন শোষণ চলে আসছে তার বিরুদ্ধে এক নির্ভীক সমালোচনা। এই অচলায়তনের ঢক্কানিনাদ সমস্ত সমাজে কমবেশি শোনা গেলেও কোরীয় সমাজে এর উপস্থিতি খুব বেশি প্রখর। কোরীয়ানরা সামাজিক রীতিনীতির অন্ধ আনুগত্যে বিশ্বাসী, নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে বিশ্বাসযোগ্য থাকাই তাদের শিক্ষা, সে রীতি যতই অমানবিক বা দমনমূলক হোক না কেন। এই বিশ্বাস বা অনুসরণের অন্যথা ঘটলেই সমাজের কাঠামোগত সহিংসতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং প্রয়োজনে নিষ্ঠুরতার চূড়ান্তে পৌঁছে বিদ্রোহী চিন্তাভাবনাকে দমন করতে সচেষ্ট হয়। এই সহিংসতা জানতে-অজান্তে পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্রে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক ভাঙতে থাকে। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ যতক্ষণ কয়েকজন ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তথাকথিত প্রতিষ্ঠানিক সহিংসতা খুব সহজেই প্রতিবাদের আগুন নেভাতে পারে, ঠিক যেমন এখানে ইয়ং হাইয়ের ক্ষেত্রে ঘটেছে। তার প্রতিবাদ ছিল একক, দুর্বল, ক্ষীণ, তাই সেটা কোনোভাবেই সমাজের শাশ্বত কাঠামোকে নাড়া দিতে পারেনি, সেই প্রতিবাদের আগুন নেভানোর কাজ তার পরিবারের লোকজনই করে দিয়েছিল৷ তাই শেষমেষ গল্পটা ইয়ং হাইয়ের গল্প হয়েই রয়ে গেল, সমাজ বা জাতির বা দেশের গল্প হয়ে উঠতে পারল না। এখানে লেখিকা তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে সিদ্ধ হয়েছেন না হননি সেটা পাঠকই বিচার করবে।
তবে একথা সর্বজনগ্রাহ্য, এই উপন্যাসে লেখিকা কোনো ভণিতা না করে পাঠককে এক নগ্ন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন, যেখানে পাঠক এক উদ্ভট অস্বস্তি আর বিকৃত মনের দোদুল্যমানতায় ভুগতে থাকেন; আবার একইসাথে বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হন। এটা এমন একটা অবস্থা যেখানে বেশিক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে আবার পাঠকেরা পালানোর পথও খুঁজে পান না। এখানেই এই উপন্যাসের সার্থকতা, জিত।