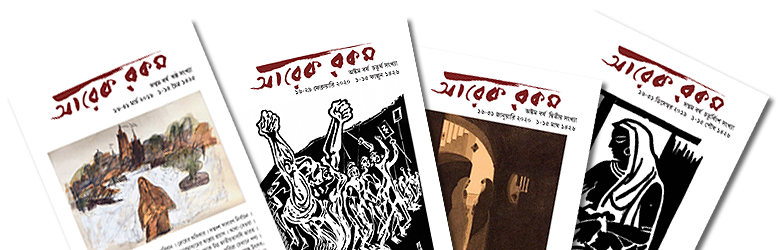আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ● ১৬-২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ● ১-১৫ ফাল্গুন, ১৪৩১
সম্পাদকীয়
কেন্দ্রীয় বাজেট ও বিকল্প আর্থিক নীতি
মিডিয়া, কর্পোরেট পুঁজি তথা রাষ্ট্রযন্ত্রকে পকেটে রাখার পরেও কিছু সত্য আছে যা চেপে রাখা নরেন্দ্র মোদী সরকারের পক্ষে অসম্ভব। যেমন দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার করোনা অতিমারির পর থেকে খুব বেশি বাড়েনি। এমনকি কোভিডের পরে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও বেশ কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে আয় কোভিড পূর্ববর্তী পরিস্থিতির তুলনায় বাড়েনি। দেশে কর্মসংস্থান কমছে, বিশেষ করে মাস মাইনে পাওয়া শ্রমিকের অনুপাত কোভিডের পর থেকে লাগাতার কমছে, বাড়ছে স্বনিযুক্ত শ্রমিক, যা একপ্রকার প্রচ্ছন্ন বেকারত্বেরই নামান্তর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবার ভারতে আর্থিক বৈষম্য বিপুলভাবে বেড়েছে। অর্থনীতিবিদ চ্যান্সেল ও পিকেটি তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে বর্তমান ভারতে যে পরিমাণ আর্থিক বৈষম্য রয়েছে তা ব্রিটিশ জমানাতেও ছিল না।
আর্থিক বৃদ্ধির শ্লথ গতি এবং বেকারত্বের সংকটের সমস্যা যে ২০২৫ সালে শুরু হল তা নয়। নরেন্দ্র সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে এই সমস্যা বেড়েছে। কিন্তু সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে কেইন্সীয় অর্থনীতির প্রয়োজন, অর্থাৎ সরকারী খরচ বাড়িয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি, তাতে তারা বিশ্বাস করেন না। তাই নানা সময়ে নানা টোটকা ব্যবহার করা হয়েছে আর্থিক বৃদ্ধির হারকে বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। ২০২৫ সালের বাজেটের আগে সরকারী আর্থিক নীতির দুটি প্রধান অস্ত্র ছিল। প্রথমত, পরিকাঠামোগত খরচ বাড়ানো। পরিসংখ্যান বলছে যে ২০১৪-১৫ সালে যেখানে মোট সরকারী খরচের প্রায় ১২ শতাংশ পরিকাঠামোগত খাতে খরচ হত, তা ২০২৪-২৫ সালে বেড়ে হয় প্রায় ২২ শতাংশ। কিন্তু এই পরিকাঠামোগত খরচ বাড়লেও মোট খরচের পরিমাণ কোভিডের পর থেকে আসলে কমেছে। মোট খরচের পরিমাণ যদি জিডিপি-র অনুপাতে না বাড়ে তাহলে মোট অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ে না। অতএব মোট খরচের মধ্যে পরিকাঠামোগত খরচের অনুপাত বাড়লেও তা দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়ানোয় সক্ষম হয়নি।
তাই সরকারকে অন্য পথের সন্ধান করতে হয়। সরকার ভরসা রেখেছিল তার দ্বিতীয় অস্ত্রের উপর - কর্পোরেট ক্ষেত্রকে ব্যাপক কর ছাড় দেওয়া। ২০১৯ সালে নির্মলা সীতারমণ কর্পোরেট কোম্পানিদের ব্যাপক কর ছাড় দেন। ২০১৮-১৯ সালে জিডিপি-র অনুপাতে ভারতের কর্পোরেট করের পরিমাণ ছিল ৩.৫ শতাংশ যা ২০২০-২১ সালে কমে হয় ২.৩ শতাংশ যা ২০২৪-২৫ সালে বেড়ে হয়েছে ৩ শতাংশ যা এখনও ২০১৮-১৯ সালের থেকে কম। কিন্তু একই সময় জিডিপি-র অনুপাতে ব্যক্তিগত আয় কর ২০১৮-১৯ সালে যেখানে ছিল ২.৫ এখন তা বেড়ে হয়েছে ৩.৮ শতাংশ। অর্থাৎ বর্তমান ভারতে ব্যক্তিগত করের পরিমাণ কর্পোরেট করের থেকে বেশ অনেকটাই কম। সোজা বাংলায় এর মানে দাঁড়ায় এই যে সাধারণ চাকুরিজীবীদের তুলনায় বড়ো বড়ো কোম্পানিরা কম কর দিচ্ছে সরকারকে।
তুলনামূলকভাবে কম কর দেওয়ার পরেও কর্পোরেটদের বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি। অতএব এত কিছু করেও সরকার দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়াতে পারেনি। তাই ২০২৫ সালের বাজেটে নতুন আরেকটি পন্থা সরকার অবলম্বন করল, তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে কর ছাড় দেওয়া। নতুন আয় কর নিয়ম অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির আয় যদি বছরে ১২ লক্ষ টাকার কম হয়, তাহলে তাকে কোনো কর দিতে হবে না। এই নীতির ফলে সরকারী কোষাগারে মোট ১ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হবে বলে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। এই বিপুল পরিমাণ কর ছাড় দেওয়া ভারতের ইতিহাসে নজিরবিহীন, এই নিয়ে কোনো সংশয় নেই। প্রশ্ন হল এই যে সরকার কি এই নতুন নীতির মাধ্যমে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে সক্ষম হবে?
একদিকে সরকার যখন কর ছাড় দিচ্ছে, অন্যদিকে তারা বাজেট ঘাটতি তথা মোট সরকারী খরচ জিডিপি-র অনুপাতে কমানোর কথা বলছে। যদি আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়াতে হয় তাহলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাণ বাড়াতে হবে। কিন্তু সরকারী খরচ সংকুচিত করা হলে, দেশে চাহিদার পরিমাণ আসলে কমবে। এর ফলে আর্থিক বৃদ্ধির হার আসলে কমবে। আবার অন্যদিকে মধ্যবিত্তদের কর ছাড় দেওয়া হলে তারা খরচ বাড়াবে, তাতে চাহিদা বাড়বে এবং আর্থিক বৃদ্ধির উপরে এর প্রভাব ইতিবাচক হবে।
কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ২০২৩-২৪ সালের হিসাব অনুযায়ী আমাদের দেশে ১৫ লক্ষ টাকার কম রোজগার করা মোট আয়করদাতার পরিমাণ মাত্র ৭ কোটি, যার মধ্যে ছোট কোম্পানিরাও আছে। এদের মধ্যে বছরে চার লক্ষ টাকার কম উপার্জন করেছেন ২ কোটি ব্যক্তি। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে যে প্রায় ৫ কোটি মানুষ রয়েছেন যারা নতুন কর নীতির আওতায় আসবেন। ১২ লক্ষ টাকা বছরে আয় করা মানে হচ্ছে মাসে এক লক্ষ টাকা আয়। সরকারী তথ্য জানাচ্ছে যে ২০২৩-২৪ সালে একজন গড় বেতনভুক্ত কর্মচারী মাসে ২০,০০০ টাকা আয় করেছেন। অর্থাৎ দেশের বিপুল সংখ্যক বেতনভুক্ত কর্মচারী বছরে ১২ লক্ষ টাকার থেকে অনেক কম টাকা রোজগার করে। অর্থনীতির একটি মৌলিক নিয়ম হল এই যে যাদের আয় কম হয়, তাদের আয়ের অনুপাতে খরচের পরিমাণ আসলে বেশি হয়। তাই যদি একজন গরীব মানুষকে ১০০ টাকা দেওয়া হয়, তাহলে তার থেকে সে যা খরচ করবে, একজন ধনী মানুষ তার তুলনায় অনেকটাই কম খরচ করবে। অতএব যদি বেশি টাকা গরীব মানুষদের উন্নয়নে খরচ করা হয় তাহলে তার অভিঘাত আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেশি হবে। তাই ১২ লক্ষ টাকা অবধি শূন্য করের নীতির তুলনায় ১০০ দিনের কাজে টাকা খরচ করলে আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। মনে রাখতে হবে যে এই বছরের বাজেটে ১০০ দিনের কাজ অথবা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মত ক্ষেত্র যার সঙ্গে গরীব মানুষের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে তাতে টাকার পরিমাণ প্রায় বাড়ানোই হয়নি।
তাহলে কি কোনো বিকল্প পথ আছে কর সংগ্রহ করে গরীব মানুষের জন্য খরচ করার? আমাদের মনে হয় বিকল্প অনেক পথই রয়েছে। তার মধ্যে একটি বিকল্প নীতি আমরা প্রস্তাব হিসেবে রাখতে চাই। বর্তমানে ভারতে এমন মানুষ যাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১০০ কোটি ডলারের বেশি, তাদের সমস্ত সম্পত্তি যোগ করলে হয় ১ লক্ষ কোটি ডলারের বেশি। যদি ধরে নেওয়া যায় যে ডলারের বিনিময় মূল্য ৮০ টাকা প্রতি ডলার, তাহলে আমাদের দেশের সর্বাধিক ধনীদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৮০ লক্ষ কোটি টাকা। সরকার যদি মাত্র ২ শতাংশ সম্পত্তি কর এই ধনীদের উপর চাপায়, তার মোট পরিমাণ হবে ১ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা। এই টাকা দিয়ে ১০০ দিনের মজুরি যদি বাড়ানো যায়, এবং তার সঙ্গে অন্যান্য উন্নয়নমূলক খরচ যদি বাড়ানো যায়, তাহলে তার প্রভাবে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ চাহিদা তথা উৎপাদন বাড়বে, অন্যদিকে আর্থিক বৈষম্য অল্প হলেও কমবে।
কিন্তু এতে কি ধনীদের বিশাল কোনো ক্ষতি হবে? আসলে তাদের বিপুল কোনো ক্ষতি হবে না, কারণ মাত্র ২ শতাংশ কর ধার্য করা হবে। এবং তাদের ভোগ ব্যয় তথা বিনিয়োগ তাদের সম্পত্তির ২ শতাংশ কমে গেলেও উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে না। অন্যদিকে গরীব মানুষের আয় বাড়বে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ধনীরা এই নীতি পছন্দ করবেন না। তাদের পোষ্য রাজনীতিকরা তাদের সম্পত্তির উপর কর চাপাবে এটাও আসলে হবে না। তাই এই আর্থিক নীতি প্রণয়ন করতে হলে আসলে চাই রাজনৈতিক আন্দোলন যা এমন একটি সরকার কেন্দ্রে বসাবে যা ধনকুবের নয়, দেশের গরীব মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ। সেই লড়াই লড়ার ক্ষেত্রেও বিকল্প অর্থনৈতিক নীতির ভাবনা মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যোগাবে। দেশের বামপন্থী শক্তিদের বিভিন্ন বিকল্প আর্থিক নীতির ভাবনা মানুষের মধ্যে প্রচার করতে হবে আকর্ষণীয়ভাবে। তাহলে একটি বিকল্প রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ভাবনার জন্ম হবে যা আপাতত ভারতের রাজনৈতিক আখ্যানে খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না।