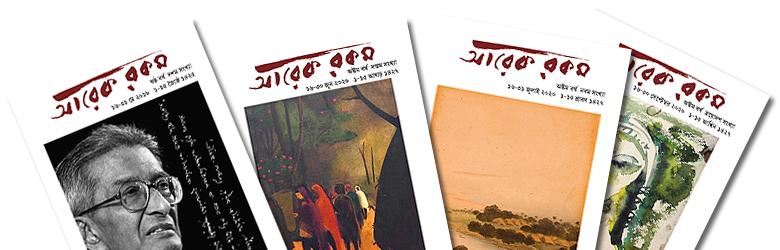আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ● ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ ● ১৬-২৯ পৌষ, ১৪৩১
প্রবন্ধ
অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচীঃ আমাদের মাস্টারমশাই
উত্তম ভট্টাচার্য

অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচী (১৯৩৬-২০২৪), আমাদের স্যার, আমাদের মাস্টারমশাই। তিনি এক মাস হলো (গত ২৮শে নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে), আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। বিগত, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তাঁর ৮৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হলো। মৃত্যুর মাস চারেক আগেও তিনি অনেক কর্মদক্ষ ছিলেন। যে রাতে অভয়া কান্ড ঘটে, ঘটনাচক্রে সেদিন হঠাৎ তিনি কিছুটা অসুস্থ হয়ে এক মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি হন। কথা ছিল আমাদের অর্থনীতি বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত বই 'দি ইন্ডিয়ান ইকনমি অ্যাট ৭৫' (রুথলেজ, ২০২৪), অর্থনীতি বিভাগে গিয়ে উদ্বোধন করবেন এবং বইটির বিষয়ে কিছু বলবেন ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে। হঠাৎ অসুস্থতার কারণে স্যারকে সেই বই প্রকাশ অনুষ্ঠান, অনলাইনে সারতে হয়। তারপর ক্রমাগত স্যারের শরীরে নানা সমস্যা দেখা দেয়। অবশেষে ২৮শে নভেম্বর ২০২৪, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যায় আমাদের মাস্টারমশাই আমাদের ছেড়ে দূরে পাড়ি দিলেন। সেদিন ছিল আমেরিকার 'থ্যাংক্স গিভিং'-এর মতো অনুষ্ঠান।
ইতিমধ্যে, 'আরেক রকম' পত্রিকা (দ্বাদশ বর্ষ, চতুর্বিংশ সংখ্যা)-তে, স্যারকে নিয়ে সুন্দর একটি সম্পাদকীয় লেখা প্রকাশ হয়েছে। এবং তাঁর স্মরণে, শ্রী প্রসেনজিৎ বসুও অসাধারণ এক স্মৃতিচারণ করেছেন। এছাড়া ভারতবর্ষের এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু দৈনিক পত্রিকাতে অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচীর নিজের লেখা বইপত্র, তাঁর লেখা একাধিক বিদগ্ধ প্রবন্ধ নিয়ে, শিক্ষা জগতে, তাঁর অসামান্য অবদান নিয়ে, এবং সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে, তাঁর নানান মার্কসীয় বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেস', ক্যালকাটা, গবেষণা কেন্দ্রের এক সময়ের (১৯৮৮-১৯৯৭ সালে) অধিকর্তা বা ডিরেক্টর হিসেবে তাঁর বিশেষ অবদান উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর, কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের আরেক উল্লেখযোগ্য গবেষণা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, 'ইনস্টিটিউট অফ ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ', কলকাতা (আইডিএসকে) তৈরিতে (২০০১-২০০২) এবং সেই গবেষণা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক অধিকর্তা বা ডিরেক্টর হিসাবে, তাকে বড় করে তুলতে, সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে, অধ্যাপক বাগচীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, একথাও একাদিক্রমে, সেইসব লেখাতে স্বীকার করা হয়েছে।
আগামীদিনেও, অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচীর লেখা, দর্শন এবং বিশ্লেষণ বহুভাবে চর্চিত হবে। তিনি কেমনভাবে, আমাদের কাছে, শিক্ষা জগতের অভিভাবক 'বটবৃক্ষ' স্বরূপ ছিলেন, আমাদের এক ভীতিপ্রদ 'স্যার' এবং একই সাথে, এক অত্যন্ত ভালোবাসার মানুষ, 'অমিয়দা' হিসাবে আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন তা নিয়ে নানা মহলে চর্চা চলতেই থাকবে। তাঁর কাছে শিক্ষা নেওয়া এবং তাঁর সান্নিধ্যে বড় হওয়া অনেক ছাত্র এবং ছাত্রীরা, শিক্ষা জগতে আজ সুপ্রতিষ্ঠিতও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের বিচারে উল্লেখযোগ্য মানুষ হিসেবে গণ্য।
আমি নিজেও অধ্যাপক অমিয় বাগচীর সাহচর্য পেয়েছি দীর্ঘ প্রায় আটচল্লিশ বছর। সেই যবে, (১৯৭৫-৭৬ সালে) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের এক অতি সাধারণ ছাত্র হয়ে প্রবেশ করি, এবং পরে তাঁর রিসার্চ প্রজেক্ট-এর রিসার্চ কর্মী, এবং উত্তরকালে, 'আইসিসিআর'-এর স্কলার হয়ে অধ্যাপক বাগচীর অধীনে ভারতের 'মেশিন টুলস' শিল্প নিয়ে গবেষণা শুরু করি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শেষ শিক্ষাগত ডিগ্রি অর্জন করি। একসময় অধ্যাপক বাগচীর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা তথা গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'আইডিএসকে'-র একজন গবেষক এবং শিক্ষক হিসেবে যোগ দিই, এবং ২০১৬ সালে অবসর গ্রহণের পরও অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচীর সাথে আমার যোগাযোগ অক্ষুন্ন রয়ে যায়। তাঁর এক গুণমুগ্ধ শিষ্য স্বরূপ আজও আমি রয়ে গেছি। তথাকথিত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ডের বিচারে আমি স্যারের অধীনে থেকেও, উচ্চভাবে সফল বা কৃতকার্য এমন দাবি কখনও করি না। আমি তাঁর, অন্যতম উৎকৃষ্ট ছাত্র একেবারেই নই। নিতান্তই 'লেগে থাকা' এক সাধারণ ছাত্র মাত্র আমি। অধ্যাপক বাগচীর বাগানে বা 'মালঞ্চে', তবু নিশ্চয়ই, নিতান্তই 'মালাকার' হিসাবে মান্যতা পেতে পারি। এখানে আমি স্যারের বেশ কিছু (সরাসরি) ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধি হিসেবে, তাঁদের কাছ থেকে আহরণ করা তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং আমার নিজের কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে মিশিয়ে কিছু কথা ভাগ করে নিতে চাই।
আমরা কয়েকভাবে, এখন অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচীকে দেখতে চেষ্টা করব।
এক, প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষক হিসেবে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাস-এর শিক্ষক হিসেবে।
দুই, 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেস', ক্যালকাটা-র এম.ফিল. (বা সেদিনের কথাতে, রিসার্চ ট্রেনিং প্রোগ্রাম, বা আরটিপি-র) শিক্ষক হিসেবে।
তিন, পিএইচডি-র কাজে বা গবেষণা কাজের সুপারভাইজার হিসেবে।
এবং চার, বিভিন্ন জনসভা বা মঞ্চে, জনগণের কাছে বক্তা বা পাবলিক স্পিকার হিসেবে।
পাঁচ, একজন সুদক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাতা ও অধিকর্তা হিসেবে এবং সেইসঙ্গে, কলকাতা অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র বা 'অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন'-এর মাননীয় সদস্য হিসেবে, যার সাথে তাঁর যোগাযোগ শেষ অবধি থেকে গেছে।
অধ্যাপক বাগচী ১৯৫৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে থেকে দক্ষতার সাথে উচ্চস্থান অধিকার করে গ্রাজুয়েট বা স্নাতক হন এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে ১৯৫৭ সালে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন। ছাত্রজীবনে তাঁর আদর্শ শিক্ষক ছিলেন, অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত। তাঁর প্রায় সমসাময়িক ছিলেন, অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক অমর্ত্য সেন।
স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে, কর্মজীবন শুরু করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট শিক্ষক হয়ে। তিনি সেখানে যোগ দেন ১৯৫৮ সালে। এরপর ১৯৫৯ সালে ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা ও সেখানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন। রিচার্ড গুডউইন-এর তত্ত্বাবধানে লেখা থিসিস পরে, 'প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৭২ সালে প্রকাশিত) নামে এক অসাধারণ মানের বই হিসেবে গন্য হয়। অধ্যাপক বাগচী ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল অবধি প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এর মাঝে কিছু সময়, কেম্ব্রিজ-এর জেসাস কলেজ, এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন।
এক অর্থে অধ্যাপক বাগচী, আমাদের মাস্টারমশাইদের মাস্টার। অধ্যাপক অসীম কুমার দাশগুপ্ত-র কাছে শোনা, যে, স্যার প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতিতে মূলত গাণিতিক অর্থনীতির শিক্ষক হিসেবে পড়াতেন, এমনকি 'গেম থিওরি'ও পড়াতেন।এবং সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে সপ্তাহে দুই দিন পড়াতে আসতেন। সেখানে তিনি মূলত 'প্ল্যানিং টেকনিক' পড়াতেন এবং দেশজ উদাহরণ দিয়ে অর্থনীতি বোঝাতেন। অধ্যাপক দাশগুপ্ত, প্ল্যানিং-এ, তখন 'ক্যালকুলাস অফ ভেরিয়েশনস্' শেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন ও তা শেখেন অধ্যাপক বাগচীর কাছে। অধ্যাপক দাশগুপ্তের কথাতে, অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচী ছাত্র-ছাত্রীদের "স্নেহের উষ্ণতা দিয়ে ঘিরে রাখতেন"।
অধ্যাপক রতন খাসনবিশের সময়কালে অধ্যাপক বাগচী 'লিনিয়ার ইকনমিকস', 'স্যাডো প্রাইস' ইত্যাদি পড়াতেন। তিনি শিখিয়েছিলেন, "পিওর ইকনমিকস বলে কিছু হয় না"। অধ্যাপক খাসনবিশের বামপন্থী অর্থনীতি আদর্শপাঠ অনেকটাই অধ্যাপক বাগচীর কল্যাণে। সমাজ হতে ভয়ঙ্কর অসাম্য ঘোচানো, অসাম্য ও দারিদ্র্য মুক্ত সমাজের প্রয়োজনীয়তা পাঠ অধ্যাপক বাগচী কাছেই পাওয়া।
অধ্যাপক সুগত মার্জিতও অধ্যাপক বাগচীর স্মৃতি সভায় জানান, ভারতীয় অর্থনীতি পাঠ কীভাবে করতে হয় তা তিনি অধ্যাপক বাগচীর ভারতীয় অর্থনীতির ক্লাসে শেখেন।
আর এক ছাত্রের কাছে শোনা, ভারতীয় অর্থনীতি পাঠ দিতে গিয়ে তিনি অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ ফেডরিক হ্যায়েক-এর 'মুক্ত অর্থনীতিবাদ' বিষয়ক লেখা (১৯৪৪ সালে), 'দি রোড টু সার্ফডম' বই-এর বক্তব্যের আদ্য-শ্রাদ্ধ করেন যুক্তি দিয়ে, পুরো ক্লাস ধরে। ভারতীয় অর্থনীতির বর্ণনা কোথায় তখন! পাঠ্য সিলেবাস বলে কিছু থাকত না তখন। এক সময় আমাদের 'প্রাক্তনী সংসদ'-এর পত্রিকাতে স্যার লেখেন, "শুধু তত্ত্ব দিয়ে সমাজ বিজ্ঞান হয় না।... শুধু মনন দিয়ে শাস্ত্রচর্চা করতে গেলে, হাজার যুদ্ধের সম্ভার বানানো বিজ্ঞানী হবে..."। তিনি প্রশ্ন করেন, "ভারতের হতদরিদ্র চাষী মজুরের স্বেদ ও প্রাণের বিনিময়ে কি শুধু এই ধরনের হৃদয়হীন স্তাবক অর্থশাস্ত্রের চর্চা হবে?" ('অর্থনীতি পঠনপাঠনের তিরিশ বছর', 'অর্থনীতি ভাবনা, ভাবনায় পরিবর্তন'; একিউড, ২০০৩)।
এর পরের কথা বলতে গেলে মনে আসে, এম.এ.-তে আমাদের স্পেশাল পেপার 'ইকনমিক হিস্ট্রি'র কথা এবং 'সেন্টার'-এ যখন রিসার্চ ট্রেনিং প্রোগ্রাম পড়ি সে সময়ের কথা। তখন অমিয়বাবুর 'পলিটিক্যাল ইকনমি অফ আন্ডারডেভলপমেন্ট' বই লেখা চলছে, পরে যা কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৮২ সালে বই আকারে প্রকাশ করে। সেখানে তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দাপটে, কীভাবে এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে, তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এক এক করে।
বাংলার দুর্ভাগ্য যে সেই বই এখানে গভীরভাবে চর্চা হয় না। একই ধারায় চর্চা, মানব উন্নয়নের মাপকাঠিতে অনুন্নত দেশগুলোর পিছিয়ে পড়া নিয়ে অনেক উঁচুস্তরের গবেষণা প্রসূত বই, 'পেরিলাস প্যাসেজ এন্ড দি গ্লোবাল এসেনডেন্সি অফ ক্যাপিটাল' (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫)-ও আমাদের মধ্যে তেমনভাবে বহুল আলোচিত হল কই!
'বিশ্বায়ন' সমস্যা নিয়ে, অধ্যাপিকা ঈশিতা মুখার্জি এবং অন্য কিছু সমাজবিজ্ঞানীর সংকলিত অন্যতম বাংলা বই, 'বিশ্বায়নঃ ভাবনা-দুর্ভাবনা (২০০২ সালে, 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সি' প্রকাশিত বই), যার সমগ্র বৌদ্ধিক পরিকল্পনার প্রাণকেন্দ্রে ছিলেন অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচী (তিনিই সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি), সে বইও গভীরভাবে চর্চিত হল না এই বঙ্গে। এর সাথে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া-র প্রারম্ভ হতে, ক্রমাগত বিবর্তন নিয়ে দীর্ঘ সামাজিক অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার কাজ (১৯৮৭, ১৯৮৯, ১৯৯৭) এবং সেই বিষয়ে, স্থায়ী মহাফেজখানা বা আর্কাইভ তৈরি করার মতন গুরুত্বপূর্ণ অবদান।
এরপর কিছু আলোচনা দরকার, অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচীর অবদান একজন পিএইচডি সুপারভাইজার হিসেবে। প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ জন (যথাযথ তথ্য উদ্ধার করা হয়ে ওঠেনি) ছাত্র-ছাত্রী তাঁর অধীনে গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয়-এর সর্বোচ্চ পিএইচডি ডিগ্রি পান। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার বিষয়বস্তু, নানা ধরনের। কৃষি, শিল্প, মেসিন টুলস্, রাষ্ট্রীয় ইলেকট্রনিক শিল্প, ব্যাংক, চা শিল্প ও শ্রমিক, কোম্পানি মার্জার ও অধিগ্রহণ সংক্রান্ত, উপনিবেশ বা কলোনী সময়কালে (১৮৭১-১৯৪১) পূর্ব ভারতে শিল্প অবস্থা ইত্যাদি কত না, অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞানচর্চাই সেখানে মুখ্য।
এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করতে হয়। অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচীর অধীনে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের (কখনও কখনও আরও তাদের বাইরেও অনেকের) অনেক ধরনের আর্থিক সমস্যা আর অভিযোগ সমাধানে স্যার বিশেষভাবে সচেষ্ট হতেন। স্যারের অধীনে এক পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত, অধুনা লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষক, আমাকে জানিয়েছেন, স্যার তাঁকে কতভাবে সাহায্য করেছেন, দিল্লি থেকে আইসিএসএসআর-এর বৃত্তি না পৌঁছলে, বিপদে উদ্ধারের চেষ্টা করতেন তিনি।
এছাড়া দেখেছি, সুন্দরবন অঞ্চলের এক দুঃস্থ ছাত্রকে প্রজেক্ট করার সময়, নিয়মের উর্দ্ধে উঠে অগ্রিম অর্থ সাহায্য করতে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য, তিনি কোনও রিসার্চ-কর্মী নিয়োগ করলে, তাদের এমন যত্ন নিতেন যাতে, সেই ছাত্র অথবা ছাত্রী সঠিক সময়ে উচ্চ গবেষণা কাজে যুক্ত হতে পারেন। যাতে তাদের নিছক গবেষক-কর্মী হয়ে না জীবন শেষ করতে হয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় তা বাস্তব সত্য।
এরপর উল্লেখ করতে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচীর ভূমিকার কথা। বিশ্বায়নের ঢেউ-এর সাথে সাথে সেন্টারে একবার তীব্র আর্থিক সংকট তৈরি হয়। নানাভাবে তদারকি করে, অধ্যাপক বাগচী এবং আরও কিছু শিক্ষক সে সময় সেন্টারকে আর্থিক সমস্যা থেকে উদ্ধার করেন। আমি তখন সেই প্রতিষ্ঠানে।
এরপর পশ্চিমবঙ্গে ২০০০-২০০১ সালে, নানা ভাবনাচিন্তা করে, নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা ও উচ্চ পঠনপাঠনের লক্ষ্য নিয়ে এক নতুন গবেষণা কেন্দ্র, 'আইডিএসকে' তৈরি হয়, তৎকালীন বাম সরকার-এর সহায়তায়।
এখানে এক উল্লেখযোগ্য বিষয় মনে রাখা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক অসীম দাশগুপ্ত স্পষ্টভাবে জানান যে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার সময়ে একটা ব্যাপার পরিষ্কার ছিল যে, 'আইডিএসকে'র গবেষণা এবং পঠনপাঠনের কাজে, কোনওভাবেই সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। অধ্যাপক বাগচী, তাঁর নিজের মতন সাজিয়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণামূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন। অধ্যাপক বাগচী এখানে মুক্তমনে স্বাধীনভাবে কাজ পরিচালনা করেছেন আজীবন। অবৈতনিক অধিকর্তা হিসেবে দু'বার কার্যভার বহন করার পর, তিনি নিয়মমতো সরে আসেন। পরে সেখানে তিনি 'এমেরিটাস অধ্যাপক' হয়ে যুক্ত ছিলেন আমৃত্যু।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায়, বিশেষ করে, সেই সময়ের ভারতের প্রধানমন্ত্রী, শ্রী মনমোহন সিং-এর সৌজন্যে ও অর্থানুকূল্যে, 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' (ইউজিসি) অনুমোদিত, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব প্রকর্ষ চর্চা কেন্দ্র' গবেষণা কাজ শুরু করে, এই আইডিএসকের অধীনে। সেখানে মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে নতুন কাজের সুযোগ ঘটে। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর মতো গবেষক তখন যুক্ত হন এই কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রের গবেষণার উদ্দেশ্য বলতে, অধ্যাপক বাগচী উল্লেখ করতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের বহু পঠিত কবিতা "এবার ফিরাও মোরে", "...এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে/ দিতে হবে ভাষা - এই সব শান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে/ ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা - ডাকিয়া বলিতে হবে -/ মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে,/ যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,/ যখনি দাঁড়াবে তুমি তখনই সে পালাবে ধেয়ে।" আরও বলতেন, "অন্ন চাই প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,/ চাই বল, চাই স্বাস্থ্য আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।/ সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।" নানা কারণে অবশ্য এই কেন্দ্রের কাজ স্থগিত হয়ে আছে।
পৃথিবীর বৃহৎ অঙ্গনে, 'ইউনাইটেড নেশনস্'-এর বিভিন্ন মঞ্চে অধ্যাপক অমিয় বাগচীর নানা বক্তৃতা, তাঁর মার্কসীয় দর্শন, আগামীদিনে নিশ্চয়ই আমাদের পথ দেখাবে। পৃথিবীতে যত দিন অসাম্য, দারিদ্র্য, অনাহার, শোষণ চলবে ততদিন, অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচীর ও তাঁর কাজের গুরুত্ব অক্ষত থাকবে। প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায়, তাঁর জ্ঞান বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। এ প্রসঙ্গে ২০০৯ সালে অধ্যাপক বাগচীর, জর্ডনে হওয়া 'পাথওয়ে টু রিকনসিলিয়শন সামিট'-এ বক্তৃতা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। (সেটি এখন ইউটিউব-এ অধ্যাপক বাগচীর বক্তৃতা উল্লেখ করলে শোনা যায়। লিঙ্কঃ https://youtu.be/uGMZIpKReBE?si=JR2I4j8ODqKAdSLn)। সেখানে বলা হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে 'সুবর্ণ যুগ' বলে কিছু নেই। আছে, অগণিত মানুষ নিধনের ঘটনা, আছে অসহনীয় অসাম্য, শিশু অপুষ্টির ঘটনা, দারিদ্র্য, রাষ্ট্র পরিচালিত ন্যায়নীতি বর্জিত কার্যকলাপ, কার্বন নির্গমন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নিধনলীলা। এসব হতে ব্রহ্মান্ডকে রক্ষা করার জন্য চাই ক্রমাগত লড়াই।
অধ্যাপক বাগচী ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে, এই বাংলায়, এক নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাবিদ। অনেক প্রলোভন থাকলেও তিনি কখনও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়েননি। বাংলার গ্রাম ও মাটি হতে উঠে আসা এক সংগ্রামী বুদ্ধিজীবী, এক করুণাময় মানুষ হয়ে আজীবন তিনি রয়ে গিয়েছেন এ বঙ্গে।
অধ্যাপক বাগচী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে, গ্রামসীর ভাষাতে উল্লেখ করেন, "অর্গ্যানিক ইন্টেলেকচুয়াল" বলে। আমাদের কাছে, অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচী নিজেও তেমনই এক চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, অর্গ্যানিক ইন্টেলেকচুয়াল।
আলোচনা শেষ করব কোভিড-১৯ প্যানডেমিককালে, দেশজুড়ে লাগাতার কার্ফু বা টোটাল লক-ডাউন শুরু হবার কয়েকদিন আগের এক ঘটনার উল্লেখ করে। তখন অধ্যাপক বাগচী সবে তাঁর ছোট কন্যার কর্মস্থল নেদারল্যান্ডস থেকে মার্কস বিষয়ে এক কনফারেন্স সেরে দেশে ফিরে এসে সম্পূর্ণ গৃহবন্দি রয়েছেন। আমি গিয়েছিলাম সেদিন স্যারকে, কলকাতা এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে। কোনো সূত্রে সংবাদপত্রে পরের দিন খবর হয়, "অধ্যাপক অমিয় বাগচী বিদেশ থেকে ফিরেছেন"। সৌভাগ্য ঘটনাটা নিয়ে তেমনভাবে হৈচৈ পড়েনি। তবে ভয়ে ছিলাম, পাছে সরকার নির্বাসন-এ পাঠায় স্যারকে। সে এক মহা দুশ্চিন্তায় ছিলাম।
এ সময়, স্যারের বড় কন্যা এবং ছোট কন্যা অনলাইন-এ ভিডিও কলের মাধ্যমে স্যারের দিনযাপন চালিয়ে যেতে যথাসম্ভব সাহায্য করে। সেটা আমার কাছে এক কল্পনাতীত অভিজ্ঞতা ছিল। আমি সাধ্যমতন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করার চেষ্টা করতাম। পরে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হলে, তখন স্যারকে ভ্যাকসিন দেওয়ানো হয়। লাইন দিয়ে সবার সাথেই ভ্যাকসিন নেন স্যার। পরে এ নিয়ে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'-র বুলেটিনে তিনি লেখেন। এই আতঙ্কজনক সময়ে স্যারকে কখনও মূহ্যমান হয়ে পড়তে দেখিনি, কখনও অবসাদে ভুগতে দেখিনি। তিনি সেসময় অনেক কমবয়সী মানুষের থেকে অনেক বেশী পরিশ্রম করতেন, ঘরের মধ্যে অনেক হাঁটাচলা করতেন, কপালভাতি বলে এক প্রাণায়াম করতেন। আর অনেক অনেক সময় দিতেন পড়াশোনা এবং কম্পিউটারে লেখালেখি করতে। সেসময় অনেক বুক রিভিউ করেছেন অনবরত। তাঁর এই কর্মদক্ষতা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সকলের কাছে। আমাকেও বিভিন্ন শারীরিক ব্যায়াম করতে বলতেন। আমি অবশ্য, হাঁটাহাঁটি বাদে অন্য কোনো ব্যায়াম করতাম না। স্যারের অতি প্রিয় স্ত্রী, অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে এক চিকিৎসাগত বিভ্রাটে, ক'বছর আগে। সেই বিরাট শোকধাক্কা তিনি অনেক বেদনা নিয়ে কাটিয়ে ওঠেন, অনেকটা নিজের মনের জোর এবং আশেপাশে, অধ্যাপক অশোক মিত্র, অধ্যাপক নবনীতা দেবসেন, অধ্যাপিকা মালিনীদি, মিহিরদা, সুনন্দাদির মতন বন্ধুদের সাহচর্যে। এছাড়া গানের জগৎ ও দুই কন্যার অনবরত যোগাযোগ-এর কল্যাণে। স্যার আমাকেও উপদেশ দিতেন, "গান শুনো, অবসাদ মিটবে..."।
আমাদের মতন শিষ্যবৃন্দের কাছে অধ্যাপক বাগচী সমস্ত ধরনের সমাজ বিজ্ঞান চর্চার বিষয়ে, সামাজিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের পথে, এক উজ্জ্বল আলোরবর্তিকা, আমাদের কাছে এক চিরকালীন প্রজ্ঞাময় পথপ্রদর্শক তিনি। আমাদের তিনি এক অন্যতম মার্কসীয় দর্শন শিক্ষক। অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচী, আমাদের কাছে আমৃত্যু আলোরবর্তিকা হয়েই থাকবেন।