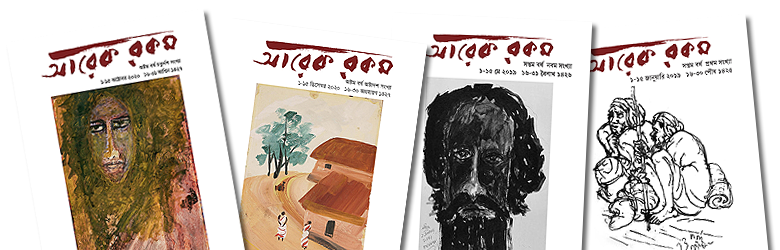আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ● ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ ● ১৬-২৯ পৌষ, ১৪৩১
প্রবন্ধ
দেশভাগ, বাংলার নারী আন্দোলন এবং মণিকুন্তলা সেন
অশোক ভট্টাচার্য
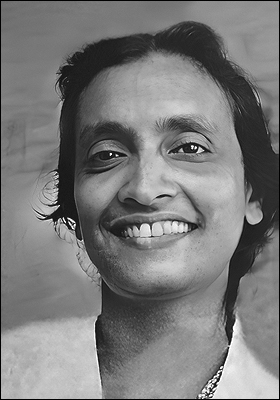
বাংলার রাজনীতিতে ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব ঘটেছিল ’৪০-এর দশকে পরাধীন ভারতে কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের। ১৯১০ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বরিশাল শহরে এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। স্নাতক স্তর পর্যন্ত বরিশালেই ছিল তাঁর শিক্ষা। ১৯৩৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হন। থাকতেন কলকাতার একটি হোস্টেলে। এম.এ. পাস করে তিনি একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন।
রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি যুক্ত হন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্টির সঙ্গে। তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তাঁর যাতায়াত ঘটে। সেখানে তিনি সংস্পর্শে আসেন কমিউনিস্ট নেতা মুজফফর আহমদ, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখের। এর পরে তিনি যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। তিনি ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পাটির সদস্য পদ অর্জন করেন।
১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করলে তিনি যুক্ত হন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ও সমাজতন্ত্র রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে পার্টির প্রচার আন্দোলনে। সেই সময়ে তিনি বিভিন্ন সভায় যে বক্তৃতা দিতেন তা অচিরেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৪২ সালে একদিকে জাপানের আক্রমণ, কলকাতায় বোমা বর্ষণ, '৪৩-এর মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষ। মণিকুন্তলা সেন এমন আবহাওয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন। ইস্তফা দেন স্কুলের চাকরি থেকে। সেই সময়ে তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে পেতেন মাত্র ২০ টাকা মাসিক ভাতা। থাকতেন মহিলাদের একটি কমিউনে। পার্টির দেওয়া নানা দায়িত্বে যেমন দেশরক্ষা ও রিলিফের জন্য গঠিত জনরক্ষা সমিতি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, পিপলস্ রিলিফ কমিটি, গণনাট্য সংঘ, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন।
কলকাতায় এক সম্মেলনের মাধ্যমে ১৯৪৩ সালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। তিনিই ছিলেন এই সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শুরু করেন একের পর এক গ্রাম, জেলা, শহর সফর। গড়ে তুললেন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র বিভিন্ন শাখা সংগঠন। যে সময় বাংলার মহিলারা বাইরে আসার কথা ভাবতেই পারতেন না, সেই সময় মণিকুন্তলা সেন এই মহিলাদের বাইরে এনে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার মতো কঠিন কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।
সেই সময় এমন ব্যাপক গণআন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বাংলা, তেমনি জোয়ার উঠেছিল গণসংস্কৃতিরও। একই সময়ে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এর বিজন ভট্টাচার্যের উদ্যোগে 'নবান্ন' নাটকে তিনি একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শোভা সেনও।
এর পরেই তিনি যুক্ত হন তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি ছিলেন কলকাতাতে। বহু ঝুঁকি নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলনে যুক্ত হন। বিভিন্ন ধর্মের আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র সদস্যদের নিয়ে ত্রাণ বন্টনে উদ্যোগী হন। সেই সময়ে বাংলার বহু গ্রামে তেভাগা আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মণিকুন্তলা সেন।
চোখের সামনে দেখেছেন একাধিক ভয়াবহ দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষে রাস্তায় পড়ে থাকা ক্ষুধার্ত নারী, পুরুষ, শিশুর মৃতদেহ।
১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার পরে পরেই পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে তৎকালীন রাজ্য সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই সময়ে তিনি ছদ্মবেশে যান বহু গ্রামে। এমনকী, উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু চা বাগানেও তিনি গিয়েছিলেন। খড়গপুর ধর্মঘটে রেল শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। পার্টি বেআইনি ঘোষণা হওয়ার পরে এবং তারপরেও তিনি বহুবার গ্রেফতার হন। বিনা বিচারে প্রায় ২ বছর ছিলেন আলিপুর ও প্রেসিডেন্সি জেলে।
মণিকুন্তলা সেন ছিলেন বাংলার এক কিংবদন্তি কমিউনিস্ট নেত্রী। বাংলায় তখন এমন বাগ্মী নেত্রী কমই ছিলেন। যদিও তাঁর রাজনৈতিক জীবনকাল ছিল মাত্র ২৫ বছর। সেই বিষয়ে আমি আসব পরে। ১৯৮৩ সালে তিনি লিখেছিলেন তাঁর জীবনকথা ‘সেদিনের কথা’।
আমার খুব ছোটবেলায়, আমি তখন চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র, সেই সময়ে আমার এক জ্যাঠামশাইয়ের কাছে মণিকুন্তলা সেনের কথা শুনেছিলাম। নবপত্র প্রকাশনের 'সেদিনের কথা' বইটি সংগ্রহের চেষ্টা করছিলাম। ২০১০ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিধানসভায় তাঁর দেওয়া কয়েকটি ভাষণ। আর রয়েছে তাঁর সম্পর্কে একটি পুলিশ রিপোর্ট, এছাড়াও তাঁকে নিয়ে বিশিষ্টজনের লেখা।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কমিউনিস্টদের উপরে কীরকম অত্যাচার হয়েছিল তা ‘সেদিনের কথা’ বইটি থেকে জানা যায়। ১৯৫০ সালে কলকাতা হাইকোর্টের এক আদেশবলে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে বেআইনি ঘোষণা প্রত্যাহার করা হল। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লোকসভা ও রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা ভোট ঘোষণা হল। কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মোট ১০০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার মধ্যে কালীঘাট কেন্দ্র থেকে ছিলেন মণিকুন্তলা সেন।
এই ভোটকে মণিকুন্তলা সেন কীভাবে দেখেছিলেন সে সম্পর্কে কিছু কথায় আসছি।
তিনি ছিলেন সেবার পার্টির একমাত্র মহিলা প্রার্থী। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন আরও মহিলাদের কেন প্রার্থী করা হল না! কালীঘাট কেন্দ্রটি ছিল তাঁর কাছে অচেনা তবুও তিনি সেখান থেকে বিজয়ী হন। ২৮টি আসনে জিতেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরা। কংগ্রেস বিরোধী প্রার্থীরা সর্বমোট ৪১টি আসনে জিতেছিলেন। বিধানসভায় জ্যোতি বসু হন বিরোধী দলনেতা। মণিকুন্তলা সেন হন ডেপুটি লিডার। ১৯৫২ সালের ভোটে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ১০.৭৬ শতাংশ।
তাঁর বইতে মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন, “একটি মুসলমান পল্লির ভোট আমাদের পাওয়ার আশা ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁরা বিগড়ে গেছে। কারণ খুঁজতে গিয়ে আমি মহিলাদের নিয়ে বসলাম। আমার কথা শোনারও যেন সময় তাদের নেই। কিছুতে মুখ খোলাতে পারছি না। অবশেষে এক মহিলা বলে উঠলেন, তোমাদের ভোট দেব কী করে! তোমরা ধর্ম মানো না। আল্লার চাঁদ, ঈদের চাঁদ, সেখানে তোমরা কুকুর পাঠিয়ে দিয়েছো। এমন পাপ কেউ করে!” সোভিয়েতের 'স্পুটনিক' তখন লাইকা নামক কুকুরটিকে মহাকাশে পাঠিয়েছিল।
এরকমই একটি অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিখেছেন জলপাইগুড়ির একটি নির্বাচনী সভার। লোকসভায় হিন্দু কোড বিলের পক্ষে জনসমর্থন সংগ্রহ করার অভিযান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "এই বিলে মেয়েদের বিয়ের বয়সসীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শিশু বিবাহ, বহু বিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। অসবর্ণ বিবাহকে হিন্দু বিবাহে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কতগুলো নির্দিষ্ট কারণ থাকলে মেয়েদের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারও স্বীকার করা হয়েছে। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের সমানাধিকারের ভিত্তিতে পৈতৃক সম্পদে মেয়েদেরও সমান অধিকার স্বীকৃত। অর্থাৎ নারী সমাজকে পরিপূর্ণ আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা রয়েছে এই আইনে।"
'সেদিনের কথা' বইতে তিনি লিখেছেন, "কিন্তু আগে কি জানতাম এই বিলের বিরোধিতায় নামবেন বড় বড় নামজাদা সব লোকেরা। স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী প্রমুখ অনেক রথী-মহারথী আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। হিন্দু সমাজে গেল গেল রব উঠল। যদিও বিলটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের।"
তিনি লিখেছেন, "তাঁদের ধারণা ছিল কংগ্রেস দায়িত্ব নেবে বিলটি পাস করাতে। কিন্তু কংগ্রেস দলের অনেক রক্ষণশীলরা এই বিল সংসদে অনুমোদিত হোক চাইছিলেন না। এমনকী, বহু সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের পক্ষ থেকেও আপত্তি করা হয় বিল নিয়ে। কারণ, অনেকেই চাইছিলেন না বাড়ির মেয়েরা সম্পত্তির অধিকার পাক।" তিনি তাঁর বইয়ে লিখেছেন, "সমাজের চিরাচরিত নীতি ও সংস্কারে ঘা দিয়ে বোঝা গেল আমাদের প্রগতিশীলতা পরিধি কতটুকু!"
১৯৫৭ সালের ভোট প্রচারের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "তাঁকে অনেক ভোটদাতা ভোট দেবেন জানিয়ে অনুরোধ করেন, তিনি যেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে বেশি কিছু না বলেন।" মণিকুন্তলা সেন তাঁদের বলে দেন, "আপনাদের ইচ্ছে হলে আমাকে ভোট দেবেন, না হলে দেবেন না, আমাকে সাম্প্রদায়িকতার, সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে বলতেই হবে।" সেবারও কালীঘাট কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হন তিনি। ওই কেন্দ্র হিন্দু মহাসভার প্রার্থী পেয়েছিলেন মাত্র ২ হাজার ভোট। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' হিন্দু কোড বিলের পক্ষে, পণপ্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। পুরোভাগে ছিলেন মণিকুন্তলা সেন।
১৯৫৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ১ পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি করতে ট্রাম কোম্পানিকে অনুমতি দিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে বড় আন্দোলন হয়। তার নেতৃত্বের প্রথম সারিতে ছিলেন মণিকুন্তলা সেন। ১৯৫৪ সালে শিক্ষক আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল তাঁর। বিধানসভাতেও শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে জোরাল ভাষণ দেন তিনি। বিধানসভায় পুলিশমন্ত্রীকে সেদিন জুতো দেখিয়েছিলেন মণিকুন্তলা সেন ও জ্যোতি বসু। পরে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। সঙ্গে ছিলেন আরেক মহিলা নেত্রী পঙ্কজ আচার্য।
দেশভাগ ও স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিত হয় বাস্তুহারা বা উদ্বাস্তু আন্দোলন। বিশেষ করে, পুনর্বাসন ও জবরদখল কলোনিগুলির স্বীকৃতির দাবিতে। বিভিন্ন জেলার উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলিকে বসবাসের উপযোগী করা, উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্য বা আন্দামানে না পাঠানো, পাকিস্তানে ফেরতের চেষ্টা বন্ধ করার দাবিতে আন্দোলন ছিল সেটি। তিনি যুক্ত হন উদ্বাস্তু আন্দোলনের সংগঠন 'ইউসিআরসি'-র সঙ্গে। তাতে তাঁকে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার করা হয়। উদ্বাস্তুদের দাবির স্বপক্ষে আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন জ্যোতি বসু।
১৯৫৮ সালে মণিকুন্তলা সেন উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে বিধানসভায় এক জোরালো ভাষণ দেন। তখন পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। তিনি তাঁকে ব্যর্থ মন্ত্রী হিসেবে আখ্যা দেন। উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলির শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করেন সেই বক্তৃতায়। তিনি অভিযোগ করেন, মহিলাদের জন্য সরকার উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলিকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পরিণত করেছে। তিনি ওই ক্যাম্পগুলিকে যুদ্ধকালীন অপরাধীদের রাখার ক্যাম্প হিসেবে তুলনা করেন। তিনি বলেছিলেন, "আপনারা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পকে করেছেন মহিলাদের আশ্রয়স্থল। যারা এই মেয়েদের ভিখারি করে ইমমরাল ট্রাফিকের খোরাক জুগিয়ে দেন তারা করবেন পুনর্বাসন?"
১৯৫২ সালের ৪ জুলাই বিধানসভায় শিশু স্বাস্থ্য ও নারীদের সমস্যা বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "যে কোনও দেশের সরকারের চরিত্র ও প্রকৃতি এবং উন্নতি বোঝা যায়, সে দেশের সরকারি ব্যবস্থায় মেয়েরা কতটা উন্নতি লাভ করেছে এবং সে দেশের সরকার শিশুদের কী চোখে দেখে তা থেকে। পিছিয়ে পড়া দেশের অগ্রগতি বুঝতে এ দুটোই কষ্টিপাথর।" ওই ভাষণে মণিকুন্তলা সেন উল্লেখ করেন, দেশভাগের পরের হিসেব ধরলে পশ্চিমবঙ্গে ১০ লক্ষ বাস্তুহারা শিশুর মধ্যে ২ লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বাকিদের কীভাবে বাঁচিয়ে রাখবেন সে কথা তিনি সরকারের কাছে জানতে চান।
১০ বছর তিনি বিধানসভার সদস্য ছিলেন। বিধানসভায় তিনি যত বক্তৃতা দিয়েছেন, তার অধিকাংশই মহিলা, শিশু, স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা সঙ্কট, উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন, খাদ্য, শিক্ষা, জীবিকা ইত্যাদি বুনিয়াদি পরিষেবা নিয়ে।
১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনের উপরে বিধানচন্দ্র রায়ের পুলিশের নৃশংস ও নারকীয় আক্রমণ ও তাতে ৮০ জন কৃষককে হত্যার বিরুদ্ধে তিনি বিধানসভায় একটি ভাষণ দিয়েছিলেন ওই বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর। তাতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, “প্রায় ২০ হাজার কৃষক এসেছিল এবং সেই কৃষকদের মধ্যে খুব কম করে ধরলেও এক-তৃতীয়াংশ ছিল মেয়ে এবং মিছিলের পুরোভাগে মেয়েরাই ছিল। এই মিছিলকে যেভাবে চারদিক থেকে ঘেরাও করা হয়েছিল তাতে এই কথা আজ অস্পষ্ট নয় এবং কোনও সন্দেহ নেই যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সেই মিছিলের ওপর আক্রমণ করা হয়েছিল।” তিনি আরও বলেন, “এদের কীভাবে পিটিয়ে মারা হযেছিল জানেন? তাদের পিটিয়ে মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।” সেদিন যারা নিহত ও আহত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল মহিলা।
কিংবদন্তি কমিউনিস্ট ও নারী আন্দোলনের নেত্রী মণিকুন্তলা সেন যেমন স্বাধীনতার আগে বহু অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন, তেমনি হয়েছিলেন স্বাধীনতার পরেও।
তাঁর রাজনৈতিক জীবন ছিল মাত্র ২৫ বছরের। তার পর ‘সেদিনের কথা’য় কৈফিয়ৎ লিখেছিলেন, “হঠাৎ একদিন নিজের কক্ষপথ ছেড়ে ছিটকে পড়া তারার মতোই হারিয়ে গেলাম। স্বেচ্ছা নির্বাসনও বলা যায়।”
তিনি যেমন দেশভাগকে মানসিকভাবে মেনে নিতে পারেননি, তেমনি মেনে নিতে পারেননি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভাগকেও। তিনি যেমন সমাজের সমস্ত ধরনের, বিশেষ করে নারী সমাজের সার্বিক উন্নয়নের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি পার্টির মধ্যেও মহিলাদের জন্য আরও সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে অংশগ্রহণের কথা বলেছিলেন।
১৯৫২ সালে যখন তাঁকে কালীঘাট কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় প্রার্থী মনোনীত করে পার্টি, সে দিন পার্টির মধ্যে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি, কেন তিনি একা মহিলা প্রার্থী হবেন! কেন কনক, ইলা বা পঙ্কজও প্রার্থী হবে না!
তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে নারী-পুরুষেরা সমান অধিকার নিয়েই থাকবে। কিন্তু নারীদের মধ্যে থাকে একটি স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক বোধ ও নারীসুলভ সামাজিক অনুভূতি। সেই রকম সামাজিক অনুভূতি পুরুষদের মধ্যে থাকতে পারে না, যা আছে একমাত্র মহিলাদের মধ্যেই। মহিলাদের পার্টির মধ্যেও দিতে হবে আরও মর্যাদা। মহিলাদের যেমন থাকবে একটি রাজনৈতিক জীবন, তেমনি আছে সামাজিক জীবনবোধ।
১৯৮৭ সালে কলকাতার কড়েয়া রোডের বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। নারী আন্দোলনের কিংবদন্তি নেত্রী মণিকুন্তলা সেনকে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ গণ্য করেছিল একজন বিপজ্জনক নারী হিসেবে। এ জন্য তাঁকে রাখা হত নজরদারির মধ্যে। স্বাধীনতার পরের অভিজ্ঞতাও মণিকুন্তলা সেনের ক্ষেত্রে প্রায় একই।
‘সেদিনের কথা’ বইয়ের শেষের দিকে শেষ কথায় তিনি লিখেছেন, “সন্দেহ নেই নারী সমাজের নবজাগরণ শুরু হয় স্বদেশি আন্দোলনের হাত ধরে। বস্তুত, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু দেশমুক্তির ব্যাপার নয়, তা নারীমুক্তিরও ধাত্রী। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েই নারী সমাজ স্বাধীন চিন্তা ও আত্মপোলব্ধির প্রথম স্বাদ গ্রহণ করে।”
এই আত্মোপলব্ধির কারণে আজ নারীবাদ ও লিঙ্গসাম্যের প্রশ্নটি বিশেষভাবে সামনে আসছে। এই সময়ে মণিকুন্তলা সেনকে নতুন করে স্মরণ করা ভীষণ প্রয়োজন। এই লেখা সেই উদ্দেশ্যেই।