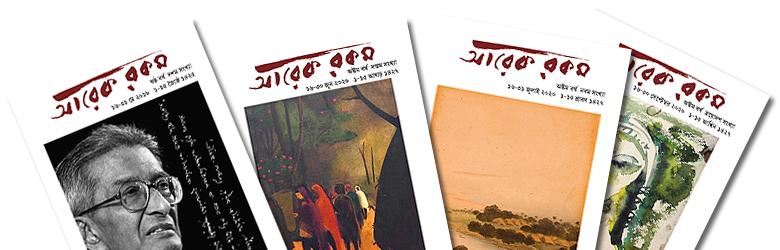আরেক রকম ● ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ● ১-১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ ● ১৬-২৯ পৌষ, ১৪৩১
সমসাময়িক
ফিরে দেখা
গোটা বছরটা পেছনে ফেলে এসে একবার পিছন ফিরে দেখা বোধহয় ভালো। অস্থির অশান্ত সময়ে বিগত দিনের অভিজ্ঞতা আগামীর আরও আঁধারে হয়ত কিছু সুবিধা করে দিতে পারে। কে জানে! বাঙালি যে ঠিক কখন থেকে স্বকীয়তা ছেড়ে অনুকরণপ্রিয় হয়ে উঠেছে, ভাবতে বসলে তাল কেটে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তবু, অনুসন্ধিৎসু মন কিছু কাটাছেঁড়া না করে কি ক্ষান্ত দেবে? কে জানে! সচেতন মন বহু কিছু বলে যেতে চায়। তবে সমাজের সেসবে আদৌ কোন আগ্রহ আছে কিনা, সময়ই তার বিচারক। অবশ্য আজকাল বিচার চেয়েও খুব শান্তিতে থাকা যায়না। বিচারের বাণী আজও তো অশ্রুতই। আর্থিক বা সামাজিক প্রতিপত্তি ছাড়া বিচারের দেবীর কৃপাদৃষ্টি স্বাধীনত্তোর ভারতে আমার আপনার জুটেছে, ইতিহাস এরকম স্বাক্ষী বিশেষ রাখেনি। তবুও আশায় বাঁচে চাষা। তবে সময় হয়ত আজও নিরপেক্ষ বিচারক। সে আদালতে দিনকে রাত করার নিদর্শন নেই। সেই অমোঘ কালচক্রের দরবারে মামুলি কলমচি খেরোর খাতা লিখে রেখে যায়। ভবিষ্যৎ পাঠক হয়ত তার দায়বদ্ধতার কদর করবে, এই আশা।
দেশভাগের স্মৃতি বুকে নিয়ে বাংলা হয়েছিল পশ্চিমবাংলা। আর তারই নাড়ির একটা অংশ কেটে হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। রাজনীতির কানাগলি পেরিয়ে, নিজের সংস্কৃতির জোরে বাংলার সেই অংশ নিজেকে মুক্ত করে প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশ নাম নিয়ে। রক্তাক্ত ইতিহাসের পথ বেয়ে দ্বিতীয়বার বাঙালিকে খুঁজে নিতে হয়েছিল নিজের দেশ। কিন্তু বিগত পাঁচ মাসে আবারও বাংলার এই অংশ উত্তাল। আবারও সীমান্তের ওপারে বাঙালি খুঁজতে চাইছে টিকে থাকার নতুন শর্ত। এক বিরাট পরিবর্তন নিজের দেশে তারা সাধন করেছেন। যদিও তা প্রগতির পথে না বিপরীতে সময় বলবে। তবে ওপার বাংলা ৫৩ বছর পর নতুন করে এক স্বাধীনতা খুঁজতে নেমেছে। কিন্তু সেই নির্মাণ কেবল আর তার সীমানায় আটকে নেই। বিশ্বায়িত দুনিয়ায় তার প্রতিবেশী দেশ ভারতেও সেই কম্পনের অনুরণন এসে পড়ছে। ভারতীয় সমাজে কোণঠাসা পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালি দ্বিধাবিভক্ত। নতুন এই দুর্বিপাকে পক্ষ নিতে তার হিমশিম দশা। আসলে বাজারে তার নিজের কোন পক্ষ আর নেই। ফলে বিকোতে থাকা দুটি পক্ষের কোন দলে নাম লেখালে একটু নিশ্চিন্তে থাকা যায়, এপারের বাঙালি সেই বিতর্কেই জেরবার।
সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা মেনে অধুনা (যতদিন বলা যাচ্ছে) বাংলাদেশে একটি বিপ্লব হয়েছে বটে। তা নিয়ে তর্ক করার উপায় নেই। ফলে ইতিহাসের ধারা মেনেই বিপ্লবের পর সমাজ কার দখলে যাবে সেই উতরোল চলছে, পারস্পরিক সংঘাত ঘটে চলেছে। পুরোনো শাসক ও ভাবি শাসকের সম্মুখ সমরে উলুখাগড়াদের জান মাল নিরাপদ নেই। কিন্তু সেই সমস্যা সমাধানে কোন উদ্যোগ না নিয়ে সীমান্তের দু'পারেই শুরু হয়েছে মিথ্যাচার আর যুদ্ধজিগির তোলার প্রতিযোগিতা। যেহেতু এ দফায় ক্ষমতার দাবিদার ধর্মীয় মৌলবাদ, অতএব ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন চালিয়ে শক্তি জাহিরের প্রক্রিয়া জারি আছে সীমান্তের ওপারে। এই গোটা অরাজকতার সুফল ভোগ করছে ভারতের সংখ্যাগুরু মৌলবাদীরা। ফলে সীমানার এ পারেও জীবন মোটেই আর শান্ত নয়। পুতিগন্ধময় যে পরিবেশ জনসঙ্ঘ চেয়েছিল, আজ পশ্চিমবঙ্গকে তা গিলে খাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আজ বাঙালির সহজাত সম্প্রীতির চেতনাকে অনেকটাই বিগড়ে দিতে পেরেছে।
অবশ্য এটা হওয়াই বোধহয় স্বাভাবিক গতি ছিল। স্বাধীনতার মূল্য চোকাতে বাঙালিকে কেবল নিজের সন্তানদেরকেই হারাতে হয়নি, তার জমি, সংস্কৃতির একটা আড়াআড়ি বিচ্ছেদকেও মেনে নিতে হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্তস্নাত বাঙালি যে ১৯৪৭-এর পর উপর্যুপরি দাঙ্গায় না জড়িয়ে খাদ্যের দাবিতে, জমির দাবিতে লড়ে গেছে তা যে নেহাতই তৎকালীন বাম নেতাদের অসাধারণ কৃতিত্বের ফল তা অস্বীকার করা যায় না বটে। তবে আজ সেই ধারাবাহিকতা আর নেই। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত বাঙালি সমাজ যেন তার অতীতের চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন। পশ্চিমবঙ্গে বাম রাজনীতির অবসান এবং বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উত্থান এই দুই বাংলার বাঙালির মননে বড়সড় এক শূন্যতা তৈরি করেছে।
বিগত এক দশকের বেশী তৃণমূলী রাজত্ব এই রাজনৈতিক সঙ্কটকে আরও তীব্র করেছে। রাজনীতির যে নয়া কাঠামোটি তারা বাংলার বুকে প্রতিষ্ঠা করে দিতে পেরেছে সেখানে মতাদর্শগত কোনও দায়বদ্ধতার জায়গা নেই। যে কোনওভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং তার জন্য সবই ন্যায়সঙ্গত - এই হল তাদের রাজনীতির মূলমন্ত্র। ফলে বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে তাদের নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক মত নেই। বিজেপি যতক্ষণ ক্ষমতার দাবিদার ততক্ষণ তৃণমূল দলটি, বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই আশঙ্কা না থাকলে উভয়ের গলা জড়িয়ে ‘আয় ভাই, বুকে আয়’ বলতেও কোন সমস্যা নেই। ফলে বিগত এক দশকে এই রাজ্যে স্বয়ংসেবকেরা কলেবরে বেড়েছে। আজকে সীমান্তের ওপারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিপীড়িত হলে, এই সেবকেরাই এপারে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিচ্ছে, এমনকি দাঙ্গা লাগানোর মতো পরিকল্পনাও করছে। সীমান্তের দু'পারেই আজ ধর্মীয় মৌলবাদীরা বলীয়ান। বস্তুত দেশভাগের পর এতদিনে সীমান্তের দু'পারেই এই মৌলবাদীরা নিজেদের পছন্দের পরিবেশ পেয়েছে যা তারা ৪৭ সালেই পেয়েছিল। তাই ঘটনাবলীর প্রবাহ আজ তাদের নির্ধারিত খাতেই বইছে। বিদ্বেষের বিষ, সাম্প্রদায়িক ঘৃণা আজ বাঙালিকে খণ্ডিত করতে পেরেছে, সব অর্থেই। সেই ভাবনা এতই তীব্র যে দুর্নীতি, হত্যা, সামাজিক নিপীড়নের মতো জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা আজ বাঙালির কাছে তুচ্ছ। ধর্মীয় পক্ষের কোন দলে তার অবস্থান, সেই ঠিক করতেই তারা আজ হিমশিম! ডান থেকে বাম সব পক্ষই এই খেলায় আজ হেরে গিয়েছে।
অথচ এমনটি তো হওয়ার কথা ছিলনা। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের বাংলায় ধর্ম নিয়ে এমনতর চুলোচুলি চলবে, এ কে কবে ভেবেছিল। নবজাগরণের যে সামাজিক বিপ্লব বাঙালিকে মুক্ত করেছিল মনুবাদের গ্রাস থেকে, সেই বাঙালি আজ কোথায় পথ হারালো? নাকি জন্মলগ্ন থেকেই তার সুফল ছিল কেবল সামাজিক এলিটদের কব্জায়। আজ রাজনীতির সাপলুডো খেলায় বাঙালি এলিট জলসাঘরের বিশ্বম্ভর। ফলে বাঙালির অন্ত্যজ, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা অংশ, চেতনায়, মননে একেবারেই অন্য সংস্কৃতির বাহক, যেখানে নীতির জায়গা নেই। আছে কেবল টিকে থাকার লড়াই। ফলে রাজনীতির অক্ষ সামাজিক ন্যায় নাকি ধৰ্মীয় সংখ্যাগুরুবাদ, তাতে তার কিছুই যায় আসেনা। ফলে বাঙালির নিজস্ব সম্প্রীতির ধারণা, রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে যা পেয়েছিল এক স্পষ্টতা, আজ দূরীভূত। পড়ে আছে কেবল দেশভাগের যন্ত্রনা লালিত ঘরছাড়া বাঙালি। ফলে বিদ্বেষ আজ স্বাভাবিক, সামাজিক মৎস্যন্যায় আজ প্রতিষ্ঠিত।
এই শূন্যতা কি আদৌ পূরণ সম্ভব? নাকি বাঙালি তার ঐতিহ্য, চেতনা এবং প্রতিরোধের সংস্কৃতিকে হারিয়ে আরও বেশি করে উপনিবেশিত এক মানসিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? তবে আশার আলো এখনও নিভে যায়নি। এপার-ওপারের নতুন প্রজন্ম, যারা অতীতের ক্ষত থেকে শিক্ষা নিয়ে, নতুনভাবে নিজেদের পথ খুঁজতে চাইছে, তাদের হাত ধরেই হয়তো বাঙালির নতুন স্বপ্নের দিন আসবে। কিন্তু সেই দিনের জন্য, বাঙালিকে তার আত্মপরিচয় নিয়ে আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে। কে জানে, হয়তো সেই ভাবনার মধ্যেই রয়েছে একটি নবজাগরণের সূচনা। হয়তো বা বামপন্থী রাজনীতিও খুঁজে পাবে তার হৃত গৌরব।