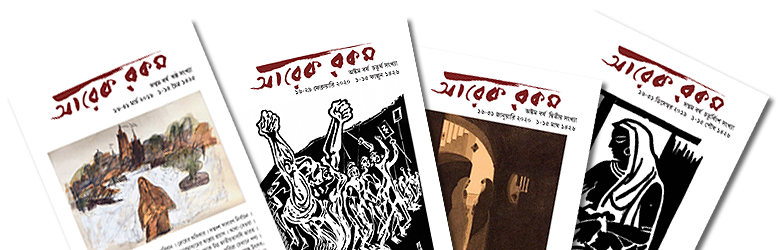আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ চতুর্বিংশ সংখ্যা ● ১৬-৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ ● ১-১৫ পৌষ, ১৪৩১
প্রবন্ধ
দৈনন্দিন বিষয়ও কীভাবে ইতিহাস হয়ে ওঠে
অনমিত্র ঘোষ
'ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ' কলকাতার পক্ষে ছোটদের জন্য লেখা ‘ইতিহাসের হাতেখড়ি’ সিরিজের সাম্প্রতিক তিনটি প্রকাশনা - অনীক বিশ্বাস ও কৌস্তুভ মনি সেনগুপ্তের ‘খেলাধুলো’, অন্বেষা সেনগুপ্ত ও সীমন্তিনী মুখোপাধ্যায়-এর ‘খাওয়াদাওয়া‘, দেব কুমার ঝাঁজ ও দেবারতি বাগচীর ‘পোশাক-আশাক’। ভাবতেই অবাক লাগে যে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ এইসব অতি সাধারণ বিষয়ও কীভাবে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠে। তিনটি বইয়ের লেখার মধ্যে একটা সাধারণ সাদৃশ্য - খেলাধুলো, খাওয়াদাওয়া বা পোশাক-আশাককে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবোধ, সম্প্রীতি, সাম্প্রদায়িকতা, লিঙ্গ অসাম্য এবং শ্রেণি ও জাত বৈষম্যের বিষয়গুলোও আনুষঙ্গিকভাবে উঠে এসেছে।
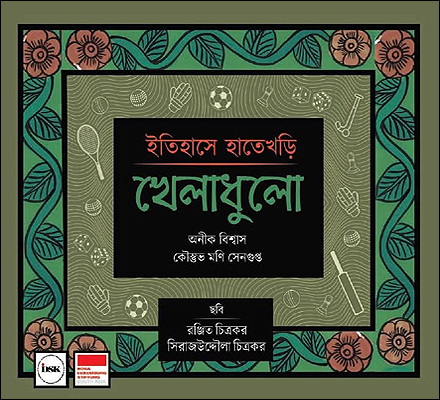
খেলাধুলো
ফুটবল, ক্রিকেট আর হকি তিনটি বিদেশি খেলা কীভাবে পরাধীন ভারতে জাতীয়তাবোধের স্ফূরণে সহায়ক শক্তি হয়ে উঠেছিল তার সুন্দর একটা ছবি শুরুতে উঠে এসেছে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা পর্বে এবং বঙ্গভঙ্গ রোধের বছরে মোহনবাগান ক্লাব দু'বার ইউরোপীয় ক্লাবকে হারায়। গোটা পর্বে এটা যতটা ছিল ফুটবল খেলায় জয়ী হবার প্রতিযোগিতা, ভারতীয়দের কাছে এটা ছিল তার চেয়েও বেশি কিছু - বিদেশি শাসককে পরাস্ত করার ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের আনন্দ। বইয়ের আলোচনায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে সেই ছবিটা।
সঠিকভাবে আলোচনায় এসেছে তিরিশের দশকে মহমেডান ক্লাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফুটবল জগতে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগাভাগির কথা। আরও পরে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে হিন্দুদের মধ্যেও ঘটি বাঙাল বিভাজন। সব বর্ণের মানুষ গা ঘেসাঘেসি করে ফুটবল খেলার আপত্তির কথাও উল্লেখিত হয়েছে।
ক্রিকেট খেলার ক্ষেত্রেও পারসি, মুসলমান, হিন্দু আর অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের নামে আলাদা আলাদা টিম। বিদেশিদের কাছে বিদেশি খেলা শিখে তাদেরকে হারিয়ে দিলেও দেশপ্রেম হেরে যায় ধৰ্মীয় বিভাজন আর জাতপাতের উগ্রতার কাছে। নিচু জাতে জন্মগ্রহণ করা দক্ষ অধিনায়ক বালুকে পাভেলিয়নের বাইরে মাটির ভাঁড়ে চা পানে বাধ্য করার কাহিনি দেশের সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তার উদ্রেক করে। জয়-পরাজয়ের পরিসংখ্যান, খেলার উন্মাদনা বা আনন্দের বাইরেও খেলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্তঃসম্পর্ক সুন্দরভাবে এসেছে আলোচনায়।
ফুটবল বা ক্রিকেটের মতো প্রায় একই সময়ে পাশাপাশি হেঁটেছে হকি। স্বাধীনতার আগে পরে মিলিয়ে হকির চল্লিশ বছরের গৌরবময় অধ্যায়। খেলার সৌজন্যে দলের অধিনায়ক জয়পাল মুন্ডা পরবর্তীতে আদিবাসী সমাজের সার্বিক প্রতিনিধি হিসেবে উঠে আসা ও সংবিধান সভায় নির্বাচিত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ করতেও লেখকরা ভোলেননি। আলোচনায় দেশীয় অভিজাত শ্রেণির খেলোয়াড়দের পাশাপাশি গরিব সাধারণ মানুষ যারা ফাইফরমাস খাটতেন তাদের প্রতি বিদেশি ও দেশীয় বাবুদের অমানবিক ব্যবহারের উল্লেখ পাঠককে নিশ্চিত ভাবাবে। হকির মাধ্যমে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অলিম্পিকের মাঠে হিটলারকে হাত তুলে অভিবাদন জানাতে অস্বীকার করা ও জার্মানিকে হারানোর ইতিহাস পাঠককে রোমাঞ্চিত করবেই।
সব ধরণের খেলার ক্ষেত্রে মহিলাদের পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করেই তাদের জায়গা করে নিতে হয়েছে। বিদেশি শাসকদের কাছে যারা যোগ্য প্রমাণের তাগিদ অনুভব করেছেন খেলার মাধ্যমে তারাই আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে বিপরীত অবস্থান নিয়েছেন। হোক সে ফুটবল, ক্রিকেট বা হকি। এই স্ববিরোধিতার দিকটি বেশ গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হয়েছে। গোটা বইয়ে সংক্ষেপে, অত্যন্ত সহজ ভাষায় অন্যান্য খেলা সহ প্রধান তিনটি খেলার ক্রমবিকাশ এবং তার সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমি, দ্বন্দ্ব ও সৌহার্দ-ছবি উঠে এসেছে সাবলীলভাবে।
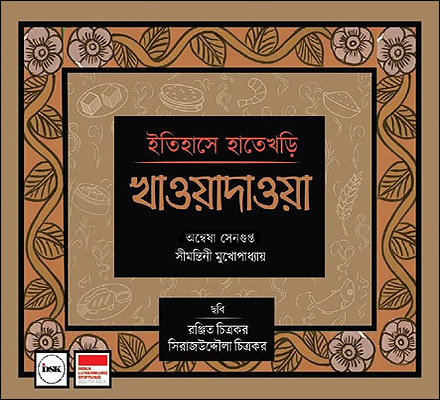
খাওয়াদাওয়া
ভৌগোলিক অর্থনৈতিক সামাজিক কারণ থেকে অঞ্চলভেদে মানুষের খাদ্যভ্যাস আলাদা হতে বাধ্য যার সঙ্গে মিশে থাকে অভ্যাস, রুচি, এমনকি ধর্মীয় বিশ্বাস। রান্নার ধরনও আলাদা হয় এবং একজনের পছন্দের খাবার অন্যের কাছে অপছন্দের কারণ হয়ে ওঠে। গোল বাধে তখনই যখন একজনের পছন্দ অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অনৈতিক চেষ্টা চলে। হিন্দুদের মধ্যেই আমিষ নিরামিষ ভাগ। ভাত আর রুটির সেই সময়ের দ্বন্দ্বের ইতিহাস চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। গোমাংস খাওয়া ও আমিষ নিরামিষ বিতর্ক কতটা অপ্রয়োজনীয় সেটা এই বই পড়লে ছোটরাও বুঝতে পারবে।
আবার রান্না করা কেবল মেয়েদের কাজ এমন পুরুষতান্ত্রিক ভাবনা এখনও প্রবল। এক ধর্মের বা জাতের মানুষের রান্না অন্যরা স্পর্শ অব্দি করবে না এমন বিশ্বাসের মানুষও বেশ বেশি। এই রাজ্যেও স্কুলে মিড ডে মিলের রান্না নিয়েও ঝামেলার উল্লেখ পাঠককে ভাবাবে। খাবারের পুষ্টিগুণের চেয়েও নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের মোড়কেও নিজেদের বিশ্বাসকে পেশ করা হয়। খাওয়াদাওয়া নিয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি এতটাই প্রভাবশালী যে তা নিয়ে হানাহানি কম নয়। অথচ সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে বিভাজন আনে। সব ধরনেরই আলোচনা করা হয়েছে খুব প্রাঞ্জলভাবে। অনেক ক্ষেত্রে গল্পের মাধ্যমে অথচ যা তথ্যগতভাবেও সঠিক।
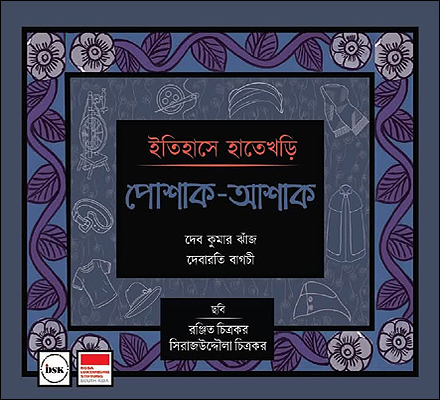
পোশাক-আশাক
শুরুতেই 'শাসকের পোশাক' শিরোনামে বেশ আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। পোশাকের পার্থক্য কীভাবে সম্ভ্রম বা অবজ্ঞার সূচক হয়ে ওঠে সে তো সকলের নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা। এদেশের আবহাওয়ার উপযুক্ত না হলেও সাহেবি পোশাক তো মানুষ এমনি পরেন না। এক অঞ্চলের প্ৰিয় পোশাক অন্য অঞ্চলের মানুষের কাছে উদ্ভট লাগে। পোশাকের সঙ্গে বেশি জড়িয়ে বাণিজ্যর সম্পর্ক। ইংরেজদের ব্যবসায়িক স্বার্থে এদেশের তাঁত শিল্প ধ্বংস করা এবং তাঁতে বোনা স্বদেশি কাপড়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠার বিষয়টা সুন্দরভাবে লেখায় এসেছে। পোশাক নিয়ে মেয়েদের ক্ষেত্রে আছে হাজার বিধিনিষেধ। শরীরের কতটুকু ঢাকা থাকবে তা নিয়ে কম বিতর্ক নেই। এদেশে মুসলমান ছাত্রীদের ক্ষেত্রে অনেক স্কুলে হিজাব পরে আসার ওপর সরকারি বিধিনিষেধ রয়েছে। আবার কট্টর মুসলিম দেশে হিজাব না পরলেই বিধান আছে কঠিন শাস্তির। দু'ক্ষেত্রেই মেয়েরা লড়ছে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সব ধরণের ইতিহাস স্বচ্ছ হয়ে ধরা দিয়েছে মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল আলোচনায়। তবে ত্রিবাঙ্কুরের অস্পৃশ্য নাডা সমাজের মহিলা-সমাজের নাঙেলির নিজের স্তন নিজের হাতে কেটে স্তন ট্যাক্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কাহিনির উল্লেখ থাকলে পোশাক নিয়ে সামাজিক অনুশাসনের মাত্রা বুঝতে বেশি সুবিধা হতো।
বই তিনটি লেখার জন্য লেখক-লেখিকারা যা আন্তরিক পরিশ্রম করেছেন সেটা বোঝা যায় তাদের অনেকগুলো কর্মশালা করা এবং রেফারেন্স বইয়ের তালিকা দেখলে। ইতিহাসের নানা জটিল বিষয় ছোটদের কাছে সহজভাবে বুঝিয়ে বলা খুব কঠিন কাজ। বইয়ের লেখক-লেখিকারা সেই অসম্ভব কাজকেই সম্ভব করে তুলেছেন পরিশ্রমের বিনিময়ে। ইতিহাসের হাতেখড়ি সিরিজের বইগুলো পড়লে ইতিহাসকে বোঝার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে বাধ্য। বইগুলি ছোটদের জন্য লেখা হলেও যে কোনও সাধারণ পাঠকের কাছে তা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় ও শিক্ষামূলক।
বইগুলোতে আনুষঙ্গিকভাবে যে কাহিনিগুলো এসেছে সেগুলো গল্পের মতো করে পরিবেশন করা হলেও সবগুলো ঐতিহাসিকভাবে সত্যি। লেখাগুলো সহজবোধ্য করার জন্য লেখকদের অনেক সচেতন থাকতে হয়েছে সেটা সহজেই অনুমেয়। চোখের আরাম ও বক্তব্য বোঝার সুবিধার জন্য প্রাসঙ্গিক ছবি বা মানচিত্র দেওয়া হয়েছে। পট চিত্রশিল্পী রঞ্জিত চিত্রকর ও সিরাজদৌল্লা চিত্রকরের ছবিগুলো ছোটদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় হবে সন্দেহ নেই। এই অসহনশীলতার যুগে মুসলিম ধর্মালম্বী হয়েও এই ধরণের পট শিল্পীরা হিন্দু ধর্মের আখ্যান নিয়েই ছবি আঁকেন বা গান বাঁধেন এটা জেনে অবাক হতে হয় বৈকি।
সুখপাঠ্য তিনটি বইয়ের প্রচ্ছদ, কাগজ ও মুদ্রণ নিয়ে কোনও অভিযোগের সুযোগ নেই। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থে একপেশে, মনগড়া ও বিকৃত ইতিহাস রচনার এই কঠিন সময়পর্বে ‘ইতিহাসের হাতেখড়ি’ সিরিজ প্রকাশ করে নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস অনুধাবনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও একজন আদর্শ ভাবি নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সহায়ক এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।