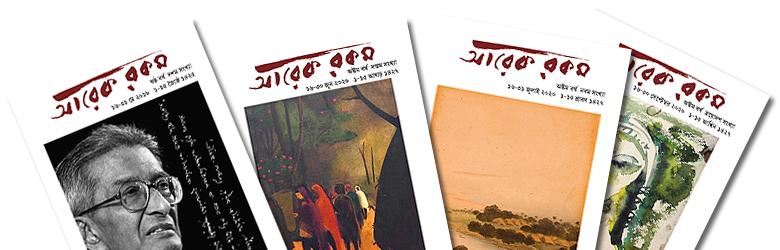আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ চতুর্বিংশ সংখ্যা ● ১৬-৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ ● ১-১৫ পৌষ, ১৪৩১
প্রবন্ধ
অনিশ্চয়তার চরে অনেক হিসাবই মিলবে না
গৌতম হোড়

মালদহের কাছে গঙ্গার চর এক আশ্চর্য জগৎ। চরের বাইরের জীবন এবং চরের জীবনের মধ্যে কোনো তুলনা চলে না। চরের জীবনের সব ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চয়তা থাকে। ছিন্নমূল মানুষের অনিশ্চয়তা। বাইরে থেকে গিয়ে তা টের পাওয়া যায়, অনেকটা অনুভব করা যায়, কিন্তু যার সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়নি, তার পক্ষে এই অনিশ্চয়তা পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়।
পঞ্চানন্দপুর ঘাট থেকে নৌকায় করে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগল পলাশগাছি বা পালানপুর চরে পৌঁছতে। নৌকা থেকে নেমে চায়ের দোকানে বসে আছি। চায়ের প্রতীক্ষার ফাঁকে পাশে বসা মানুষদের সঙ্গে গল্পগুজব চলছে। এক বয়স্ক মানুষ বললেন, "বছর কুড়ি এই চরে আছি"। তারপর বাঁদিকে হাতটা প্রসারিত করে তিনি বললেন, "আগে ওইদিকে ছিলাম। গঙ্গা আমাদের জমিজমা বাড়িঘর সব নিয়ে নিল। তারপর এইদিকে গেলাম"। এবার ডানদিকের একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন তিনি। নিরাসক্তভাবে বলতে থাকলেন, "সেখানেও ভাঙন শুরুর পর এখানে এসে বসেছি"।
নিজেদের বাড়ি, জমি, চারপাশের চেনা জায়গা সব একদিন চলে যায় নদীর ভিতর। সেই জমি গ্রাস করে নেয় গঙ্গা। সরকার জানিয়ে দেয়, ওই জমি 'শিকস্তি' হয়ে গেছে - অর্থাৎ, এই জমির মালিকানা আগে যাদের কাছে ছিল, তা এখন নদীর তলায়। জমিই নেই, ফলে মালিকানার প্রশ্নও নেই। বাস্তুহীন মানুষগুলির আবার পথ চলা শুরু। সেই সফর আপাতত শেষ হয়েছে ওই চরে। পরে আবার কবে সেই চর ভাঙবে বা সেই চর থেকে উঠে যেতে হবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই বলছিলাম, এই মানুষগুলির কষ্ট পুরোটা বোঝা সম্ভব নয়।
কিন্তু কাহিনি তো এখানেই শেষ হচ্ছে না। এই যে চর, তার জমির লিজের সব কাজ হয় মালদহে। অথচ, যারা এই চরে বাস করেন, তাদের আধার কার্ড, রেশন কার্ড দিয়েছে ঝাড়খণ্ড সরকার। রেশন পান, জিজ্ঞাসা করতেই একজন দেখিয়ে দিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের ছবি সহ ব্যাগ। সেই ব্যাগে রেশন দেওয়া হয়। কী দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ লেখা রয়েছে সেখানে। এই চরের মানুষ ঝাড়খণ্ডের ভোটদাতা। সেখানে সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে তারা ভোট দিয়েছেন। ভোটের আগে নিয়মিত রেশনও পেয়েছেন।
সেই বয়স্ক মানুষ বললেন, "তাহলে বুঝতে পারছেন তো আমাদের অবস্থাটা। আমরা না ঘরকা, না ঘাটকা"। বলে নেওয়া ভাল, পুরো কথপোকথনটা হচ্ছিল বাংলায়, কারণ, তাঁরাও তো বাঙালি। আদতে মালদহের মানুষ। কিন্তু এখন যে চরে আশ্রয় নিয়েছেন, সেই চর আবার প্রশাসনিক দিক থেকে ঝাড়খণ্ডের। ফলে স্কুলের শিক্ষকের বেতন দেয় ঝাড়খণ্ড সরকার। সেখানে একটা ভাষা হিসাবে বাংলা পড়ানো হয়। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হিন্দি। সেই স্কুলের কথা পরে হবে, আপাতত দেখে নেওয়া যাক, কেন এই অবস্থা হল?
গঙ্গা একূল ভাঙে, ওকূল ভাঙে, বর্ষার সময় বয়ে নিয়ে আসে বিপুল পরিমাণ পলিমাটি। ফারাক্কা ব্যারেজের কল্যাণে সেই পলি আর বিশেষ বাইরে যেতে পারে না। সে সবই জমতে থাকে এধারে। নদীর তলদেশ উঁচু হতে থাকে। তারপর নদীগর্ভ থেকে মাথা তুলতে শুরু করে চর। অল্প অল্প করে মাথা তোলা সেই চর আকারে আয়তনে বাড়তে থাকে। উঁচু হতে থাকে। আট থেকে দশ বছর গেলে সেই চরের মাটি শক্ত হয়। গাছপালা গজায়। জঙ্গল হয়। তখন সেই চর মানুষের বসবাসের উপযুক্ত হয়। সেখানে বাস্তুহারা মানুষ যেতে শুরু করেন। এই চরের জমি সরকারের। যারা সেখানে গিয়ে বসবাস ও চাষ আবাদ করেন, তারা জমি লিজ নেন সরকারের কাছ থেকে। এবার আসে প্রশাসনের ভূমিকা। চরে মানুষ থাকবে, তাদের জমি লিজ দেওয়া হবে, তাহলে তো তাদের জন্য ন্যূনতম পরিষেবাও দিতে হবে। তাদের বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে, রাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি দেখতে হবে। পঞ্চায়েত করতে হবে। সেই বাম আমল থেকে দীর্ঘদিন সরকার এই দায়িত্ব নিতে চায়নি। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, মালদহের প্রশাসন সেসময় কোনো উদ্যোগ নেয়নি। চর ও গঙ্গার ভাঙন নিয়ে আন্দোলন করা হাবিব জানিয়েছেন, গঙ্গার যে চরে মানুষ বসবাস করে তার মধ্যে সাতটি মালদহে আছে। বাকিগুলি চলে গিয়েছে ঝাড়খণ্ডে। অথচ, সেখানে জমির লিজের বিষয়টি মালদহে এসে করতে হয়। তারা মালদহের মানুষ। বাংলায় কথা বলেন। তারা বাঙালি। অথচ থাকছেন ঝাড়খণ্ডে।
হাবিব কথাগুলো বলছিলেন খাটিয়াখানা চরে বসে - যেখানে এখন বিদ্যুৎ এসেছে, স্কুল তৈরি হয়েছে, পঞ্চায়েত আছে। ঝাঁ চকচকে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রও সেজেগুজে তৈরি। কিন্তু এর জন্য হাবিবদের, চরের মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করতে হয়েছে। মালদহে গিয়ে অবস্থান করতে হয়েছে। ঘেরাও করতে হয়েছে। অনেক অনুরোধ, আবেদন, আন্দোলনের পর সেখানে এখন অনেককিছুই হয়েছে। হাবিবরা এখনও আন্দোলন করছেন। তবে তা গঙ্গাভাঙন রোধ করার জন্য। গঙ্গাভাঙনের কথা পরে হবে। তার আগে চোখ রাখা যাক চরের জীবনে।

যে কোনো চরে একটু হাঁটলেই দেখবেন, বাড়ির সামনে বসে মেয়েরা বিড়ি বাঁধছেন। মেয়েদের নিয়ে মা সমানে বেঁধে চলেছেন বিড়ি। এমনই একটা বাড়ির সামনে চারজন মেয়ে বিড়ি বাঁধছিলেন। বিড়ি বেঁধে কত পান? প্রশ্নটা শোনার পর জবাব আসতে দেরি হল না। হাজারটা বিড়ি বাঁধলে ১৬৫ টাকা। হাজারটা বিড়ি বাঁধতে কত সময় লাগে? ছয় থেকে সাত ঘণ্টা। কতক্ষণ বিড়ি বাঁধেন? সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত - খাওয়া-দাওয়ার সময়টা বাদ দিয়ে। অথচ, মালদহে মেইনল্যান্ডে হাজারটা বিড়ি বাঁধার মজুরি ২২০ থেকে ২৪০ টাকা। কিন্তু এই যে চরে এসে বিড়ির সরঞ্জাম দেবে, সেখান থেকে বিড়ি সংগ্রহ করবে, তার খরচটাও ব্যবসায়ীরা তুলে নেয়। ফলে কোপ পড়ে মজুরিতে। চরের অনিশ্চিত জীবনে এমন অনেক অসাম্যের গল্প আছে।
বিড়ি বাঁধতে ব্যস্ত ১৪-১৫ বছরের মেয়ের হাতে মেহেন্দি দেখে হাবিব জিজ্ঞাসা করলেন, "কার বিয়ে হয়েছে রে"? হাতে মেহেন্দির নতমুখে জবাব, "আমার। তিনমাস হলো"। হাবিবের পরের প্রশ্নটা আরও মারাত্মক, "বর মারে"? এবার একটা মিষ্টি হাসি এল উত্তরদাতার কাছ থেকে। এই চর এলাকা নিজের হাতের তালুর মতো চেনা হাবিব বললেন, "যদি জিজ্ঞাসা করেন, বর মারে কি না, তাহলে বলবে, একেবারেই না। যদি জানতে চাইবেন কতটা মারে, তাহলে প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন। আর মনে রাখবেন, চরের মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় ১৩ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। এই যে বাড়ির বাইরে বসে বিড়ি বাঁধছে, সেখানে দেখেই মেয়েদের পছন্দ করে পাত্র বিয়ে করতে চায়। পছন্দ হলে বাবা-মা-র সঙ্গে কথা এগোয়"।
চরের এই অবস্থা দেখে মনে পড়ে গেল, 'ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে'র তথ্যর কথা। সেই সার্ভে বলছে, যে তিনটি রাজ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, সেগুলি হল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ত্রিপুরা। সারা দেশে চাইল্ড ম্যারেজের হার ১৯৯২-৯৩ সালে ৫৪.২ শতাংশ থেকে কমে ২০১৯-২১ সালে হয়েছে ২৩.৩ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই হার ৪১ শতাংশ। যে তিন জেলায় অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, সেগুলি হল মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর। তাই চরের এই অল্পবয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতাকে বিচ্ছিন্ন বলা যাবে না।
চরের রাস্তা দিয়ে আরও এগিয়ে যাওয়া গেল। বাড়ির বাইরে কাঠের শিকের মধ্যে গোবর দিয়ে তৈরি ছোটো ছোটো জ্বালানি রোদে শুকোতে রাখা হয়েছে। ধুলোময় রাস্তা। বাড়ির আঙিনায় মুরগি চরছে। ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে ছাগলের গায়ে জামা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে ফিরছে। যারা স্কুল যায়নি, তারা অধিকাংশই বিড়ি বাঁধছে।
বাড়ির বাইরে মেয়েকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এক নারী। তার পাশে কিছু বাচ্চা ও কয়েকজন মেয়ে। তাদের সঙ্গে কথা বলছিল সৃজনী। সে অক্সফোর্ডে সৃজনশীল ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করছে। তাকে বারবার এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হল, "তোমার বিয়ে হয়নি কেন"? প্রতিবারই সে জবাব দিয়ে গেল, "পড়ছি তো তাই এখন নয়, পরে বিয়ে করব"। প্রতিবারই এই জবাব ওই চরের মেয়েদের যারপরনাই অবাক করল। তারা ঠিক হিসাব মেলাতে পারছিল না। তাদের ওখানে তো মেয়েদের দ্রুত বিয়ে দেওয়াই দস্তুর। সেখানে পড়ছে বলে বিয়ে করছে না, এই যুক্তি কঠিন অঙ্কের মতো জটিল।
ওই নারীর কোলে থাকা মেয়েকে দেখিয়ে সৃজনী বলল, "আপনার মেয়ে দেখতে খুব সুন্দর"। তাঁর জবাব এল, ‘’কিন্তু তোমার মত গায়ের রং পায়নি’’। ওই নারীর বয়স ২৬ বছর। এখনই পাঁচ সন্তানের মা। নিজে আর সন্তান করতে চায় না। কিন্তু পাশ থেকে এক নারী জানালেন, "সন্তানধারণ কি আর আমাদের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে"! ঠিকই, পুরুষ-প্রধান সমাজে নারীর ইচ্ছে অনিচ্ছের মূল্য চর বা চরের বাইরের ভারতে তো একই। নারীর ইচ্ছের উপর খুব কম বিষয়ই নির্ভর করে। এই বাস্তবতা নিয়েই তো তাদের দিনযাপন। সৃজনীও ওই নারীর সমবয়সী। তার বিয়ে হয়নি জেনে সেই নারীর চোখও কপালে ওঠার জোগাড়। জানতে চাইলেন, "কী কর"? সৃজনীর জবাব, "পড়াশুনো করি"। শুনে একটু থেমে বললেন, "প্রার্থনা কর, আমার মেয়ে যেন তোমার মতো হয়"।
জানি না, শীতের দমকা বাতাসের সঙ্গে তার সেই ইচ্ছে উড়ে যাবে নাকি সত্যিই সেই ছোট্ট মেয়ে একদিন তার মায়ের প্রত্যাশা পূর্ণ করবে। অনিশ্চয়তার চরে কোনো কিছুই যে নিশ্চিত করে বলা যায় না।