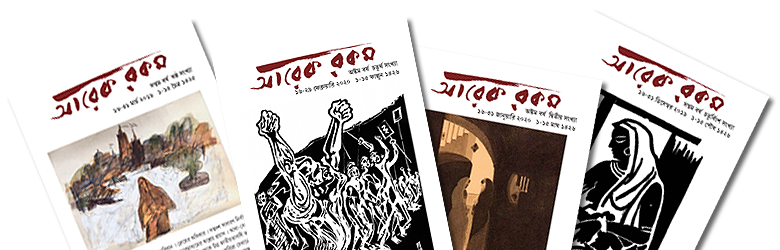আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ ত্রয়োবিংশ সংখ্যা ● ১-১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ ● ১৬-৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১
প্রবন্ধ
দক্ষিণ ও উত্তরের রাজনীতির দ্বন্দ্ব
অশোক সরকার
দক্ষিণের রাজ্য অন্ধ্র ও তামিলনাড়ু-র দুই মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি এক অদ্ভুত কথা শুনিয়েছেন। জনসংখ্যা বাড়াতে হবে। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি, এখনও শুনি ভারতে জনসংখ্যাই নাকি সমস্যা, সম্প্রতি অন্য গল্প শুনতে পাই, ‘ওদের বাড়ছে, আমাদের বাড়ছে না’। এর মধ্যে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে একী কথা? কেনই বা?
আসলে এর পিছনে দুটো প্রধান আশঙ্কা আছে। প্রথমেই বলি আশঙ্কা দুটি যে শুধু অন্ধ্র আর তামিলনাড়ুর জন্য প্রযোজ্য তা নয়। দক্ষিণের সব কটি রাজ্যের জন্যই তা প্রযোজ্য এবং নানা ভাবে দক্ষিণের নেতাদের মুখে তা আগেও শোনা গেছে। ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বিরোধী দল পরিচালিত রাজ্যগুলির অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে কেরালার মুখ্যমন্ত্রীও একই আশঙ্কার কথা তুলেছেন।
কী সেই আশঙ্কা?
প্রথম আশঙ্কাটি হল কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে করের ভাগাভাগি নিয়ে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে করের ভাগাভাগি ঠিক করে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন। এখন ১৬তম অর্থ কমিশন তার কাজ করছে। এর আগে ১৪ ও ১৫তম অর্থ কমিশনের সময়ে দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বঞ্চিত করছে। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা ঠিক। অর্থ কমিশন যে ফর্মুলা তৈরি করেছে তার ফলে প্রায় ১০টি রাজ্য থেকে কেন্দ্র যা কর পায়, রাজ্যগুলি কেন্দ্র থেকে পায় তার অনেক কম। তার মধ্যে সব কটি দক্ষিণের রাজ্য পড়ে, তার সঙ্গে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, এবং গুজরাত, এমনকী পশ্চিমবঙ্গও আছে।
কেন্দ্র নিচের রাজ্যগুলি থেকে ১ টাকা কর সংগ্রহ করলে সেই রাজ্যগুলি কত টাকা কেন্দ্র থেকে পায়
| মহারাষ্ট্র | কর্ণাটক | হরিয়ানা | গুজরাত | তামিলনাড়ু | তেলেঙ্গানা | অন্ধ্রপ্রদেশ | কেরালা | পশ্চিমবঙ্গ | |
| পয়সা | ৮ | ১৫ | ১৮ | ২৮ | ২৯ | ৪৩ | ৪৯ | ৫৭ | ৮৭ |
| বিহার | উত্তরপ্রদেশ | আসাম | মধ্যপ্রদেশ | ঝাড়খণ্ড | ছত্তিসগড় | হিমাচল প্রদেশ | ওড়িশা | রাজস্থান | |
| টাকা | ৭.০৬ | ২.৭৩ | ২.৬৩ | ২.৪২ | ২.১৫ | ১.৯৬ | ১.৪৬ | ১.৩৫ | ১.৩৩ |
সূত্রঃ দি হিন্দু, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।
উত্তর ভারতের একটা দুটো রাজ্য বাদ দিলে প্রায় সবকটি রাজ্য থেকে কেন্দ্র যা কর পায়, সেই রাজ্যগুলি পায় তার চেয়ে অনেকটা বেশি। সবচেয়ে বেশি পায় বিহার, তারপরে উত্তরপ্রদেশ।
এই অসমতার পিছনে আছে, অর্থ কমিশনের ফর্মুলা - রাজ্যগুলির মধ্যে টাকার ভাগাভাগিটা কোন নীতিতে হবে তার ফর্মুলা। এই ফর্মুলায় কয়েকটি সূচক আলাদা আলাদা গুরুত্বে দেখা হয়। সবচেয়ে বেশি ৪৫ শতাংশ গুরুত্ব দেওয়া হয় একটা সূচককে, যার নাম ‘Income Distance’ - একটি রাজ্যের আয় এবং সর্বোচ্চ আয়ের রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য। গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GSDP) হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সাধারণত এক বছরে, একটি রাজ্যের সীমানার মধ্যে উৎপাদিত সমস্ত পণ্য ও পরিষেবার মোট মূল্য। ‘Income Distance’ যত বেশি সেই রাজ্য পাবে তত বেশি - গরিব রাজ্যগুলি বেশি পাবে। এছাড়া আছে জনসংখ্যাকে ১৫ শতাংশ গুরুত্ব, অরণ্য ও পরিবেশকে ১০ শতাংশ, রাজ্যের আয়তনকে ১৫ শতাংশ, রাজ্যের নিজস্ব কর সংগ্রহের সঙ্গে রাজ্যের সম্পদের অনুপাতকে ২.৫ শতাংশ, আর আছে demographic performance (জনসংখ্যার নিরিখে একটি মাপকাঠি) নামে একটা সূচক যার গুরুত্ব ১২.৫ শতাংশ। এই শেষ সূচকটি ১৫তম অর্থ কমিশনের অবদান। এই সূচকটি হল জনসংখ্যা-সম্পর্কিত কারণগুলির মূল্যায়ন, যেমনঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জনসংখ্যার গঠন এবং সময়ের সঙ্গে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন।
দক্ষিণের রাজ্যগুলি ১৪তম অর্থ কমিশনের সময় থেকেই দরবার করছিল যে তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে স্থিতিশীলতা আনতে পেরেছে, ওই রাজ্যগুলিতে মহিলাদের সামগ্রিক প্রজননের হার (টোটাল ফারটিলিটি রেট) অনেক কমে গেছে - জনসংখ্যা সেভাবে আর বাড়ছে না। সামগ্রিক প্রজননের হার মেয়েদের শরীরগত ক্ষমতা নয়, এটা একটা সামাজিক সূচক, যা বলে একটা সমাজে মেয়েরা তাদের জীবদ্দশায় কতগুলি সন্তানের জন্ম দেবার সম্ভাবনা রাখে। মেয়েরা যত আধুনিক, শিক্ষিত, রোজগেরে হয়, তত এই সম্ভাবনা কমে।
উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে এখনও জনসংখ্যা অনেক বেশি হারে বাড়ছে, ফলে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি তাদের ব্যর্থতার জন্য ‘পুরস্কৃত’ হচ্ছে অর্থ কমিশনের কাছ থেকে। তাদের কথা শুনে ১৫তম অর্থ কমিশন সামগ্রিক প্রজননের হারকে হিসেবে আনতে রাজি হয়। অর্থ কমিশন বলেছিল যদি সামগ্রিক প্রজননের হার ২ হয়, তাহলে তার বিপরীত বা ১/২=০.৫-কে সূচক হিসেবে নেবে। যে রাজ্যে সেই হার সবচেয়ে কম, সেই রাজ্যের সূচক তত বেশি হবে।
সামগ্রিক প্রজননের হার (টোটাল ফারটিলিটি রেট)
| মহারাষ্ট্র | কর্ণাটক | হরিয়ানা | গুজরাত | তামিলনাড়ু | তেলেঙ্গানা | অন্ধ্রপ্রদেশ | কেরালা | পশ্চিমবঙ্গ | |
| পয়সা | ১.৭ | ১.৭ | ২.০ | ১.৯ | ১.৮ | ১.৮ | ১.৭ | ১.৭ | ১.৬ |
| বিহার | উত্তরপ্রদেশ | আসাম | মধ্যপ্রদেশ | ঝাড়খণ্ড | ছত্তিসগড় | হিমাচল প্রদেশ | ওড়িশা | রাজস্থান | |
| টাকা | ৩.০ | ২.৩৮ | ১.৯ | ২.০ | ২.৩ | ২.০ | ১.৭ | ২.১ | ২.০০ |
সূত্রঃ ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে পঞ্চম রাউন্ড ২০২১-২০২২।
অর্থ কমিশন শুধু প্রজননের হার-কে নিলে এক রকম হতো, কিন্তু আসলে সূচক হিসেবে নেওয়া হল (জনসংখ্যা x ১ / প্রজননের হার)-কে। এটাকে অর্থ কমিশন বলল demographic performance। এতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের অবস্থান চলে এল অনেকগুলি রাজ্যের উপরে। ফলে দক্ষিণের রাজ্যগুলি খুশি হল না।
এমনিতেই income distance-কে প্রধান গুরত্ব দেওয়ায় দক্ষিণের রাজ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ২০১৭-তে যখন ১৫তম অর্থ কমিশন শুরু হয় তখন হরিয়ানা ছিল সবচেয়ে উপরে। নিচের সারণীতে ছবিটা বোঝা যাবে।
সবচেয়ে বেশি জন প্রতি সম্পদ হরিয়ানার তুলনায় অন্যান্য রাজ্যের জন প্রতি সম্পদ (২০১৭ সাল)
| মহারাষ্ট্র | কর্ণাটক | হরিয়ানা | গুজরাত | তামিলনাড়ু | তেলেঙ্গানা | অন্ধ্রপ্রদেশ | কেরালা | পশ্চিমবঙ্গ | |
| টাকা | ১৭২৬৬৩ | ১৮৫৮৪০ | ২০৮৪৩৭ | ১৮৩২৫২ | ১৭৫২৭৬ | ১৭৯৩৫৮ | ১৩৮২৯৯ | ১৮৩২৫২ | ৯১৪০১ |
| Income distance | ৩৫৭৭৪ | ২২৫৯৭ | ০০ | ২৫১৮৫ | ৩৩১৬১ | ২৯০৭৯ | ৭০১৩৮ | ২৫১৮৫ | ১১৭০৩৬ |
| বিহার | উত্তরপ্রদেশ | আসাম | মধ্যপ্রদেশ | ঝাড়খণ্ড | ছত্তিসগড় | হিমাচল প্রদেশ | ওড়িশা | রাজস্থান | |
| টাকা | ৩৬৮৫০ | ৫৭৬১১ | ৭৫১৫১ | ৮৫৯৬৬ | ৬৭৪৮৭ | ৮৮৭৯৩ | ১৬৫৪৯৭ | ৮৭০৫৫ | ৯৮৬৯৮ |
| Income distance | ১৭১৫৮৭ | ১৫০৮২৬ | ১৩৩২৮৬ | ১২২৪৭১ | ১৪০৯৫০ | ১১৯৬৪৪ | ৪২৯৪০ | ১২১৩৮২ | ১০৯৭৩৯ |
সূত্রঃ https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=22089
অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, এবং Income Distance - দুটি দিক থেকেই দক্ষিণের রাজ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে তারা মনে করছে। তাদের যুক্তি, করের বাটোয়ারার মধ্যে একটা ন্যায্যতা থাকতে হবে। দেশের লক্ষ্য হবে যারা পিছিয়ে আছে তাদের সামনে টেনে তোলা, অর্থের জোগান তার একটা বড় অস্ত্র। পাল্টা যুক্তি হল এই রাজ্যগুলির পিছিয়ে থাকার পিছনে ধারাবাহিকভাবে শাসনের সামগ্রিক ব্যর্থতাই প্রধান কারণ - স্বাস্থ্য শিক্ষা পুষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোযোগ না দেওয়াই এর প্রধান কারণ। সেই ব্যর্থতাই ‘পুরস্কৃত’ হচ্ছে।
দক্ষিণের কথায় যুক্তি আছে। এই সব রাজ্যে সরকার বদলেছে অনেকবার, কিন্তু আর্থ সামাজিক উন্নয়ন আটকে আছে, কাজেই শাসনের ব্যর্থতা মানতেই হবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে শাসনের ব্যর্থতার জন্য কি মানুষ বঞ্চিত হবে? এ এক খুড়োর কল নয় কি?
রাজনৈতিক অসন্তোষ
তবে দক্ষিণের রাজ্যগুলির অসন্তোষ শুধু অর্থনৈতিক কারণে নয়। একটা বড়, হয়ত বা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কারণ কাজ করছে। সেটা প্রতিনিধিত্বের বঞ্চনার আশঙ্কা। এই বিষয়টা বুঝতে গেলে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের কাঠামোটি বুঝতে হবে।
সংবিধানের ৮১(১)এ এবং বি অনুচ্ছেদ বলেছিল যে লোকসভায় ৫০০-র বেশি নির্বাচিত প্রতিনিধি হবে না এবং সাড়ে সাত লক্ষ জনসংখ্যায় কমপক্ষে একজন প্রতিনিধি থাকবে। এই সংখ্যাগুলি এল কোথা থেকে? এর পিছনে যুক্তিটা ৮১(২) এ এবং বি অনুচ্ছেদে বলা আছে। এক, প্রতিটি রাজ্যে জনসংখ্যা ও আসনের অনুপাত সমান থাকবে, দুই, কত জনসংখ্যা প্রতি একটা লোকসভা আসন, সেই সংখ্যাটিও প্রতিটা রাজ্যে সব আসনের জন্য মোটামুটি একই হবে। জনসংখ্যা সেন্সাস অনুযায়ী নির্ধারিত হবে, প্রতিটা সেন্সাসের পর লোকসভার আসন সংখ্যা আর কত জনসংখ্যা প্রতি একটা আসন, তা পাল্টানো হবে।
১৯৫০-এর পর প্রতিটি সেন্সাসের তথ্য নিয়ে লোকসভার আসন সংখ্যা আর রাজ্যের লোকসভা আসনগুলি পাল্টানো হতো। ১৯৭৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে বলা হয় ২০০১ পর্যন্ত আসন সংখ্যা ৫৪৩-ই থাকবে, ২০০১-এ সেটিকে ২০২৬ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এর কারণ পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী চালু ছিল এবং আর্থ সামাজিক কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছু রাজ্যে ইতিমধ্যেই কমতে শুরু করেছিল, যদিও সব জায়গায় সমান হারে কমছিল না। ধরে নেওয়া হল, ২০২৬ পর্যন্ত সব রাজ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে স্থিতিশীলতা এসে যাবে।
অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত লোকসভার মোট আসন, আর প্রতি রাজ্যে লোকসভা আসন ১৯৭১-এর জনসংখ্যা অনুযায়ী আটকে দেওয়া আছে। ইতিমধ্যে ৫৪ বছর কেটে গেছে। সামগ্রিক প্রজননের হার দেখলেই বুঝবেন দক্ষিণের রাজ্যগুলির সঙ্গে উত্তরের রাজ্যগুলির তফাৎ। কাজেই ৮১(২) এ এবং বি অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে যদি ২০২৬-এ মোট লোকসভা আসন আর প্রতিটা রাজ্যের আসন ঠিক করতে হয় তাহলে কী হবে? নিচের তালিকা থেকে তা পরিষ্কার হবে। ইতিমধ্যেই আগামী বছর সেন্সাস হবে ঘোষণা করা হয়েছে, অর্থাৎ ২০২৬-এ সেই জনসংখ্যার হিসাবে লোকসভার আসন যে নির্ধারিত হতে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। এই সংখ্যা এখনকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ভিত্তিতে সম্ভাব্য বর্ধিত জনসংখ্যার হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
২০২৬-র পর দেশের সম্ভাব্য জনসংখ্যা অনুযায়ী মোট লোকসভা আসন হবে ৮৪৮। নিচের রাজ্যগুলির আসন হবে -
| মহারাষ্ট্র | কর্ণাটক | হরিয়ানা | গুজরাত | তামিলনাড়ু | তেলেঙ্গানা | অন্ধ্রপ্রদেশ | কেরালা | পশ্চিমবঙ্গ | |
| এখন | ৪৮ | ২৮ | ১০ | ২৬ | ৩৯ | ১৭ | ২৫ | ২০ | ৪২ |
| ২০২৬ | ৭৬ | ৪১ | ১৮ | ৪৩ | ৪৯ | ২৪ | ৩০ | ২০ | ৬০ |
| শতাংশ | ৫৮ | ৪৬ | ৮০ | ৬৫ | ২৫ | ৪১ | ২০ | ০ | ৪২ |
| বিহার | উত্তরপ্রদেশ | আসাম | মধ্যপ্রদেশ | ঝাড়খণ্ড | ছত্তিসগড় | হিমাচল প্রদেশ | ওড়িশা | রাজস্থান | |
| এখন | ৪০ | ৮০ | ১৪ | ২৯ | ১৪ | ১১ | ৪ | ২১ | ২৫ |
| ২০২৬ | ৮০ | ১৪৩ | ২১ | ৫২ | ২৪ | ১৯ | ৪ | ২৮ | ৫০ |
| শতাংশ | ১০০ | ৭৮ | ৫০ | ৭৯ | ৭১ | ৭২ | ০ | ৩৩ | ১০০ |
সূত্রঃ https://carnegieendowment.org/research/2019/03/indias-emerging-crisis-of-representation?lang=en
দক্ষিণের ৫টি রাজ্যের মোট আসন সংখ্যা বাড়বে ১২৯ থেকে ১৬৪ অর্থাৎ ৩৫টি, আর একা উত্তরপ্রদেশের বাড়বে ৬৩টি, বিহারের বাড়বে ৪০টি। সামগ্রিক প্রজননের হার আর লোকসভা আসনের অভিক্ষেপ দেখলে বলা যায় দক্ষিণের এমনকীপূবের রাজ্যগুলিও ক্ষতিগ্রস্থের দলে। এখানেও সেই জনসংখ্যা স্থিতিশীল করতে না পারার ‘গণতান্ত্রিক পুরস্কার’ পাচ্ছে উত্তরের রাজ্যগুলি বিশেষত বিহার, উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ইত্যাদি। অন্যদিকে কেরালা আর হিমাচলের একটাও আসন বাড়ছে না।
এইখানে প্রতিনিধিত্ব ও সম্পদের বন্টনের ভিত্তি নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন ওঠে। গণতন্ত্রে প্রতিটি মানুষের ভোট সমান। সংবিধান বলেছে, প্রতিটি প্রতিনিধি একই সংখ্যক জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করবে। আরও বলেছে, প্রতিটি রাজ্যে সেই জনসংখ্যা মোটামুটি সমান হতে হবে। এই শর্ত পূরণ করতে গেলে লোকসভায় বিভিন্ন রাজ্যের কত প্রতিনিধি হবে তা নির্ভর করবে ওই রাজ্য কতটা তার জনসংখ্যা স্থিতিশীল করতে পেরেছে তার উপর। যে পারল না সে পাবে বেশি প্রতিনিধি, যে পারল সে পাবে কম প্রতিনিধি?এটা কি ন্যায্য? একইভাবে যদি জনসংখ্যার স্থিতিশীলতা পরোক্ষে করের ভাগাভাগির ভিত্তি হয়, তাহলেও একই ঘটনা ঘটবে।
আমেরিকায় এর দুটো প্রতিবিধান আছে। প্রথমত ওদের মোট ইলেক্টরাল কলেজ সীটের (ভাবুন আমাদের লোকসভা) সংখ্যা ৫৩৮, যা ৫০টি প্রদেশ ও একটি জেলা (ওয়াশিংটন ডিসি) থেকে আসে। আমাদের দেশের মতই নানা প্রদেশে ইলেক্টরাল কলেজ সীটের (আমাদের লোকসভা আসনের মত) সংখ্যা জনসংখ্যা অনুসারে এক এক রকম। ক্যালিফোর্নিয়ার ৫৪, টেক্সাসের ৪০। কিন্তু প্রতিটা সীট কি একই ভোটার সংখ্যা বা জনসংখ্যার ভিত্তিতে? এর উত্তর না। টেক্সাসে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ভোটারে একটা সীট, ক্যালিফোর্নিয়ায় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ভোটারে একটা সীট। অন্যদিকে আমেরিকার সিনেটেপ্রতিটি রাজ্যের মাত্র দু জন করেই প্রতিনিধি আছে। ছোট বড় সব রাজ্যই সেখানে সমান। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও একটা সমাধান বের করেছে। সেখানে সামগ্রিক প্রতিনিধিত্ব আর জনসংখ্যা প্রতি প্রতিনিধি - এই দুটিকে আলাদা করে দিয়েছে। ফলে ডেনমার্ক ৬০ লক্ষ জনসংখ্যার দেশ সেখান থেকে প্রতিনিধি আছে ১৫ জন, অর্থাৎ ৪ লক্ষ জনসংখ্যায় একজন প্রতিনিধি, কিন্তু জার্মানির জনসংখ্যা হল ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ, তার ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রতিনিধি আছে ৯৬ জন মানে ৮ লক্ষ ৮০ হাজার জনসংখ্যায় একজন প্রতিনিধি। যদি ৪ লক্ষ জনসংখ্যায় একজন প্রতিনিধি নেওয়া হতো তাহলে জার্মানির প্রতিনিধি দাঁড়াত ২১১। ভারতে রাজ্যসভাতেও রাজ্যগুলির সমানতা নেই, সেখানেও জনসংখ্যা অনুসারে রাজ্যসভায় আসন।
করের ভাগাভাগির ভিত্তিকে যদি আরেকটু ন্যায়োচিত করতে হয়, তাহলে যেমন আর্থ সামাজিক সমতার লক্ষে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত ভাগ দিতে হবে, কিন্তু তারা যাতে সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকতে পারে এবং সুনির্দিষ্ট পথে এগোতে পারে তার জন্য কিছু শর্ত থাকা দরকার। অন্যদিকে যারা ইতিমধ্যেই অনেক এগিয়ে গেছে, তাদের উৎসাহিত করার ব্যবস্থাও এই ভাগাভাগির কাহিনিতে থাকতে হবে। এখনও পর্যন্ত সেই ধরণের ভাবনা আমাদের নীতি আলোচনায় বা রাজনৈতিক আলোচনাতে আসেনি।
আমরা এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে দু' চার কথা বলে নিই। পশ্চিমবঙ্গে প্রজনন হার দেশের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে সব চেয়ে কম, ফলে কেন্দ্রকে এক টাকা কর দিলে সে কেন্দ্রের কাছ থেকে পাচ্ছে ৮৭ পয়সা। এটা আরও কম হতে পারত, যেহেতু income Distance-টা যথেষ্ট বেশি, তাই দক্ষিণের তুলনায় আমাদের জুটছে একটু বেশি। অন্যদিকে জনসংখ্যা অনুসারে নতুন করে লোকসভার আসন নির্ধারিত হলে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র ১৮টা আসন বাড়বে। শতকরা হিসাবে তা দক্ষিণের মতোই। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গও এই নতুন ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্থের দলে পড়তে চলেছে।