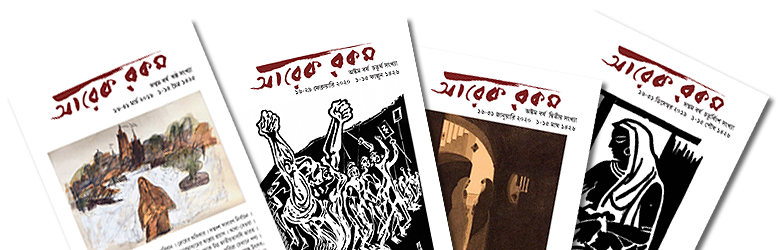আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ ত্রয়োবিংশ সংখ্যা ● ১-১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ ● ১৬-৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১
প্রবন্ধ
বৈষম্যের অর্থনীতি ও মেয়েদের লড়াই
অনিতা অগ্নিহোত্রী
গত তিন মাস ধরে আমরা নারীর উপর আক্রমণের নানা নির্মম ঘটনা নিয়ে ক্ষুব্ধ, উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। ঘটনাগুলি নিরন্তর বহমান। সূচনায় আছে আর জি কর হাসপাতালে একজন পোস্ট গ্রাজুয়েশন ছাত্রীর নির্মম হত্যা। কাজের ক্ষেত্রে এমন এক সুপরিকল্পিত হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে দুর্নীতি ও দমন নীতি মুক্ত করার, কর্ম পরিসরে ডাক্তারদের সুরক্ষার দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে, মূল দাবি ছিল নিহত মেয়েটির হত্যার বিচারের। আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিলেন জুনিয়র ও সিনিয়র ডাক্তাররা, কিন্তু সমাজের নানা পেশার মানুষ, নারী ও পুরুষ, রাজনৈতিক কর্মীরাও এই আন্দোলনে সামিল হন। এই আন্দোলনের ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থা সংস্কারের কিছু চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কিন্তু প্রশাসনিক স্তরে যে সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতা আশা করা গিয়েছিল, তার জায়গায় পাওয়া গেছে পাথরের দেওয়ালের কাঠিন্য। কিন্তু এর পরেও, সমান্তরালভাবে গ্রামে গঞ্জে মেয়েদের বিরুদ্ধে নানা নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা উঠে আসছে প্রতিদিন। সচেতন নারী-পুরুষ সকলেই উদ্বিগ্ন। কোথাও যেন নারীর বিরুদ্ধে বিপুল হিংসা দ্বার খুলে দিয়েছে এক ধরণের অরাজকতার। আইনশৃঙ্খলার রক্ষকদের নিস্পৃহতা চোখে পড়ার মতো। মনে হয় যেন, নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের রোখার জন্য ৯ ফুট উঁচু ব্যারিকেড তুলতে পুলিশ আছে, দুষ্কৃতী ধরতে নেই। এই রকম প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বিষয়টি গুরুত্ব পায়। নারীর বিরুদ্ধে হিংসা নিশ্চয়ই পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার অভিব্যক্তির চরমতম রূপ। কিন্তু বৈষম্যের যে নানা স্তর মেয়েদের জীবনকে খর্ব করার চেষ্টা করছে, তাদের শোষণ করছে, তাদের আঘাত করছে, তার পূর্ণ অনুভব ও বিশ্লেষণ ছাড়া নারীর বিরুদ্ধে হিংসার মোকাবিলা সম্ভব নয়।
নারী সমানাধিকারের নানা দিক নিয়ে যে ভাবনা চিন্তা চলেছে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে নারীর কণ্ঠস্বরকে মন দিয়ে না শুনলে সে দিকে যাত্রা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। এটা বুঝতে হবে যে যাবতীয় ক্ষমতাকে পুরুষের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই সমাজে নারী কেমন আছে তার প্রতিফলন বৈষম্যের নানা স্তরে। এক অর্থে বলা যায় মেয়েদের জন্মই এক বিরাট সমাপতন। প্রতি ১০০০ শিশুর জন্মে কন্যাসন্তানের সংখ্যা গত এক দশকে বেড়েছে ৯১৯ থেকে ৯৩৩। ভালো খবর নিঃসন্দেহে। কিন্তু এটা ভারতের গড়, দেশের নানা অঞ্চলে, জেলায় এই গড় আরও কম।প্রকৃতপক্ষে জন্মকালে কন্যা-শিশুর সংখ্যা হওয়া উচিত ১০০০-এ ৯৬০। অর্থাৎ ১০০০ জাত সন্তানের মধ্যে ৩০টি কন্যাকে আমরা হারাচ্ছি। আমরা মেয়েদের জন্মানোর পথে যদি পাথর পেতে রাখি কারণ আমাদের পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষা তীব্র, পুৎ নামক নরক থেকে উদ্ধার করবে তারা, আবার বৃদ্ধ বাবা-মা-কে ত্যাগ করলেও সোনার আংটি সোজাই থাকবে। আরও প্রখর একটি কারণ, মেয়ে জন্মালে তাকে সুরক্ষা দেবে কে? সদ্যোজাত বালিকা থেকে নব্বই বছরের বৃদ্ধা যে অপহরণ ধর্ষণ আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারে দেখেই তো সাধারণ মানুষ অভ্যস্ত। মেয়েদের পাশে দাঁড়ানো যে রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার নয়, তাও তো আমাদের কাছে স্পষ্ট।
অজাত ভ্রূণের লিঙ্গ নিরূপণ এবং তার উন্মূলনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ চিহ্নিত করে কেন্দ্রীয় আইন আছে, অথচ সে আইনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নানা জাল বিছিয়ে রেখেছে মানুষ ও যন্ত্র। আলট্রা সোনোগ্রাফি, যার মূল প্রয়োগ হওয়ার কথা জন্মের আগে সুস্থতা নিরূপণে, তার ব্যবহার হচ্ছে শিশুর লিঙ্গ চিহ্নিত করার জন্য।ক্লিনিকগুলি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে, তাদের সঙ্গে মিলে মিশে গেছে দালাল চক্র ও পুত্রসন্তান অভিলাষী পরিবার। মারাঠওয়ডা ও তার বীড অঞ্চলকে নিয়ে লিখেছিলাম 'কাস্তে' উপন্যাসে। গত এক দশকে বর্ষা দেশপাণ্ডের মতো সমাজকর্মীদের চেষ্টায় বীড যা ছিল দেশের মধ্যে কন্যাসন্তানের সবচেয়ে কম জন্মহারের ভূমি, তার পরিসংখ্যানেও উন্নতি হয়েছে। তবে এখনও বদলায়নি বীড থেকে পশ্চিম মহারাষ্ট্রে কাজ করতে যাওয়া ভ্রাম্যমান আখ কাটাই শ্রমিকদের জীবনের বাস্তব। মেয়েদের যৌন সুরক্ষা নেই, শ্রমিকরা থাকে আলোহীন, দরজা জানালাহীন ঝুপড়ি ঘরে, কাজ করার জন্য দাদন নেবার আগে তাদের মধ্যে নিঃসন্তান বা একটি সন্তানের জননীরও ২৪-৩০ বছর বয়সে জরায়ু নিষ্কাশন করিয়ে নিতে হয়। ধর্ষণ হোক বা সহবাস, সন্তানের দায় মা-কেই নিতে হবে। অযাচিত সন্তানের পথ আগেই বন্ধ করে নেওয়া ভালো। কন্যা ভ্রূণ হত্যা বা জরায়ুর অকাল উন্মোচন - অজাত বা জীবিত নারীর সুরক্ষার নামে এই যে মহাযজ্ঞ, এতে সারা দেশে খাটে কোটি কোটি টাকা। এই অর্থনৈতিক উত্তেজনা জীবিত মেয়েদের কল্যাণে হতে পারেনা? কেন হতে পারেনা?
যন্ত্র ও মানুষের নজরদারি এড়িয়ে যে কন্যাসন্তান জন্মালো তার মৃত্যুহার পুত্রসন্তানের চেয়ে কম। কিন্তু স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষার সুযোগ সবেতেই তার অধিকার তুলনামূলকভাবে কম। অমর্ত্য সেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দুইকেই ক্ষমতায়নের কারণ বলেছেন। এই দু'য়ের অধিকার থেকেই আসে পূর্ণ স্বাধীনতা।অথচ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মতো বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা আর হয়না। কেবল ধনী-দরিদ্র নয় নারী-পুরুষের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। এবং শৈশব থেকেই এর আরম্ভ। সারা পৃথিবীতে ৫০ লক্ষের বেশি মেয়ে মারা যায় গর্ভধারণ ও শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে। আমাদের দেশেও এই সংখ্যা উদ্বেগজনক। এছাড়া জীবনের নানা পর্বে, সময়ে চিকিৎসা না পেয়ে, অপুষ্টিতে, গার্হস্থ্য হিংসায়, মানসিক ভারসাম্যহীনতায়, একাকীত্বে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে নারীর জীবন। আসলে বৈষম্যের ফলে যে জনসংখ্যার অর্ধেকের জীবনের মান নীচু হয়, তার অভিঘাত পড়ে সার্বিক উন্নয়নে, সেকথা আমাদের অভিভাবক ও নীতি রূপায়নের দায়িত্বপ্রাপ্তদের মনে থাকেনা।
স্বাস্থ্য পরিষেবায় পূর্ণ অধিকার না পেয়ে দরিদ্র ঘরের অপুষ্ট কিশোরী কন্যা চলে অকাল মাতৃত্বের দিকে। অকাল মাতৃত্ব দুনিয়ায় আনে আরও কম ওজনের অপুষ্ট শিশুদের। নাবালিকা বিবাহে ভারত পৃথিবীর অন্যতম দেশ। রাজ্য হিসেবে বাংলা এই দিকে এগিয়েই আছে, ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় হয়ে। নাবালিকা বিবাহে বাংলা কেবল আজ এগিয়ে তা নয়, কুড়ি বছর আগেও ছিল। রাজ্যের দরিদ্রতম অঞ্চলগুলি থেকে মেয়েরা কাজের খোঁজে বাইরে চলে যায়, বিবাহ করেও ভিন রাজ্যে যায়। বিবাহ আর আন্তঃরাজ্য পাচার চক্রের মধ্যেকার সূক্ষ্ম বিভাজন রেখা প্রায়শই মুছে যায়। কেমন থাকে সে সব মেয়েরা যারা ঘর ছাড়ে ভুল করে বা ভুল করতে না চেয়ে। দরিদ্র ঘরে এক বড় চিন্তা, মেয়ে বড় হলে আক্রান্ত হবে, অপহৃতা হবে। যৌন সুরক্ষা দিতে পারবে না এই আশঙ্কায় অধিকাংশ প্রান্তিক ও দরিদ্র পরিবারের সমাধান, যেন তেন প্রকারেণ কন্যার বিবাহ। বিবাহের নামে পাচার করে ভিন রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার চক্রে বিপুল টাকার বিনিয়োগ হয়।
২০১৯-২০-তে জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সার্ভে (NFHS) নম্বর ৫-এর ফল বেরিয়েছে। এটা আপাতত আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পদ। জনগণনা এখন বন্ধ আছে, জাতিগত জনগণনা নিয়েও শাসক স্বস্তিতে নেই। প্রতি পাঁচ বছর এই NFHS সার্ভে হয়। আরম্ভ হয়েছে ১৯৯২-৯৩ থেকে। কোনও দেশের বা অঞ্চলের মানুষদের আয়ু, কর্মক্ষমতা ও জীবনের মান নির্ধারিত হয় সেই অঞ্চলের নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ভিত্তিতে।
এই সার্ভের ফলে বাংলার মেয়েদের যে অবস্থা আমরা দেখছি, তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। শিশুদের পুষ্টির অবনতি ও নারী ও শিশুদের রক্তাল্পতার বৃদ্ধি। বাংলায় মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণের প্রবণতা একটুও বদলায়নি।১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত সমীক্ষায় যে বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল, তাতে অবনতি দেখা যেতে লেগেছে। এই সময়ের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার কমেছে, প্রতিষ্ঠানে প্রসব বেড়েছে, অথচ, রক্তাল্পতা বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে স্টান্টেড শিশু ও কম ওজনের শিশুর সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেশি। এখনও এ রাজ্যে ৪২ শতাংশ মেয়ের নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে হয় এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণের প্রবণতা বেশি। আসলে ভারত সরকারও যেমন পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বরাদ্দ বাড়াচ্ছেন না, রাজ্য সরকারও স্বাস্থ্য বলতে বোঝেন বীমা। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। মেয়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি যে রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, আমরা কি ভুলে যাচ্ছি?
শ্রমে বঞ্চনা ও শোষণের উপরেই যেন গড়ে উঠেছে দেশের অর্থনীতি। সারা পৃথিবীতেই বৃহৎ সংখ্যক মহিলা ঘরে ও বাইরে পরিষেবা দেন, তার মূল্যায়ন হয় না। কিংস কলেজ লণ্ডন তাঁদের সম্পাদিত 'Essays on Equaliy' নামক সংকলনে অমূল্যায়িত সেবাকাজ বা Unpaid Care Work নিয়ে যে গবেষণা করেছেন তাতে দেখা গেছে, সারা পৃথিবীতে সমস্ত বয়সের ৬০ কোটির বেশি মেয়ে দিনে সাড়ে ৪ ঘন্টা হিসেবে এই কাজের ৭৫ ভাগ করেন। পুরুষরা গড়ে এই সব কাজে সময় অনেক কম দেন, তাঁদের সংখ্যাও অনেক কম, ৪ কোটির মতো। অন্যদের জন্য, নিজের ঘরে, কম্যুনিটির জন্য দেওয়া শ্রম ও সেবা এর মধ্যে আসে। যে বয়সে মেয়েদের নিজেদের উপার্জন করার কথা, পড়াশুনো বা কেরিয়ার গড়ার কথা, সেই সময়টা এই অমূল্যায়িত শ্রমে ব্যয় হয়। সারা পৃথিবীর যা উৎপাদন, তার ১৩ শতাংশই এই Unpaid Care Work বা অবমূল্যায়িত শ্রম।
আমাদের দেশেও গৃহবধূরা ছাড়া এমন শ্রম দেন অসংগঠিত ক্ষেত্রের মেয়েরা। উদাহরণস্বরূপ আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, মিড ডে মিল রান্নার কর্মীদের কথা বলা যায়। তৃতীয় গোষ্ঠীর কথায় প্রথমে আসি। একে মিড ডে মিলের বরাদ্দ কম, তার উপর যাঁরা রান্না করেন তাঁরা পান দশ মাসের মাইনে। পুরো বছরের নয়। ২০১৩ সালে মিড ডে মিল কর্মীদের ১৫০০ টাকা মাইনে ধার্য হয়েছিল, তা খুব সম্প্রতি একবার বেড়েছে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে। সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম মাইনে বাংলায়। তাদের কোনও বোনাস ভাতা, অবসরকালীন পেনশন বা কাজের সময় দুর্ঘটনা হলে তার জন্য কোনও সুরক্ষা নেই। নিজেদের রান্না করা খাবারও তাঁরা খেতে পারেন না। কিন্তু নজরদারির জন্য সিসি ক্যামেরা লাগানোর নির্দেশ দিয়েছে সরকার। আজ দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ডাক্তারদের বাদ দিলে নির্ভরশীল মেয়েদের উপর। এঁরা হলেন আইসিডিএস কর্মী ও আশাকর্মী। ১৯৭৫ সাল থেকে আইসিডিএস যোজনা। তবু অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা আজও স্থায়ী নন, তাঁরা পান সাম্মানিক। বেতন নয়। ২০০৫ সালে যখন যোজনা আরম্ভ হল, আশা কর্মীরা মাসে ৮০০ টাকা পেতেন। মাসের শেষে ৬-৭ হাজার টাকার বেশি পাননা আশাকর্মীরা। আশা কর্মীরা প্রসূতির গর্ভধারণকালে যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে হাসপাতালে প্রসবের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু প্রসব কোনও কারণে হাসপাতালে না হলে তাঁরা নিজের ভাতা পাননা। প্রসব বা গর্ভকালীন পরিষেবা দেবার মতো সুবিধে বহু জায়গাতেই নেই। অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসূতির জন্য ইউএসজি যন্ত্র, ব্লাড টেস্টের ব্যবস্থা কিছুই থাকেনা। এই সব মেয়েদের জন্য সরকারী সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছেছে, এঁরা নিজেরাও সামাজিক সম্মান পান, কিন্তু সামাজিক সুরক্ষা, এমনকি প্রসবকালীন ছুটি ও আর্থিক নিরাপত্তা পান না। রাজ্য সরকার কিন্তু সব ধরণের কাজে আশা কর্মীদের উপস্থিতি চান, কিছুদিন আগে আবাস যোজনার সমীক্ষার কাজের ঝুঁকিও তাদের নিতে হয়েছে।
মেয়েদের নিয়ে কাজ করেন এমন একটি সংগঠন, 'নারী দিবস উদযাপন মঞ্চ', সম্প্রতি নানা ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছেন, মেয়েদের প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে তৈরি তাঁদের নানা পোস্টার ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে, সংগঠিত শিল্পে মেয়েদের পরিকল্পিতভাবে অস্থায়ী কর্মী করে রাখা হচ্ছে। চটকলে ৯০ শতাংশ মেয়েই অস্থায়ী, তারা কাজ করে কম টাকা পায়। পেনশন পায়না, দুর্ঘটনা ঘটলে বীমা পায় না। স্থায়ী মেয়ে কর্মীদের কথাতেও জানা যায়, এ মিল থেকে ও মিলে অন্যায়ভাবে বদলি করা হয়। নাইট শিফটে কাজ করতে বাধ্য করা হয় অথচ ওভারটাইম বলে আলাদা কিছু নেই। সামান্য মাইনে থেকেও পিএফ কাটা যায় কিন্তু পিএফ-এর টাকা জমা পড়ল কিনা জানার উপায় নেই।
ন্যূনতম মজুরি মেয়েরা প্রায় কোথাও পাননা। কিন্তু তাদের প্রতি বৈষম্য যথেষ্ট উদ্বেগের ব্যাপার। কারণ সংবিধান বা আইন কিছুই একে সমর্থন করেনা। কৃষিতে যে কাজগুলি বিশেষভাবে মেয়েরাই করে, তার মজুরি অত্যন্ত কম। যেমন পটলে ফুল ছোঁয়ানো (বিঘে প্রতি তিরিশ টাকা), লঙ্কা তোলা (এক কিলো লঙ্কা ১ টাকা)। বিড়ি শিল্পে যেখানে মেয়েরা ঘরে বসে কাজ করে, সেখানে হাজার বিড়ি বাঁধলে ২১০-এর জায়গায় ১৬০ টাকা মজুরি পান। জঙ্গিপুরের মেয়েদের কাছে শুনলাম, বিড়ির বাণ্ডিল অনেক বাতিল হয়। তাতেও লোকসান। যৌন হেনস্থা তো স্বাভাবিক ব্যাপার শিল্পে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে। তার কোনও রেকর্ডও থাকেনা কোথাও। চা বাগানের মেয়েরা বলছিলেন অনেকে হয়রানি থেকে বাঁচতে সেটিং করে নেন, চটকলে প্রস্তাবে রাজি না হলে হেনস্থা অবধারিত। অনেক মেয়ে চাকরি ছেড়ে দেন। কাজের ফাঁকে যাওয়ার মতো বাথরুম নেই মেয়েদের। সন্তানদের জন্য ক্রেশ-এর প্রশ্নই নেই। চা বাগানে কর্মীরা অধিকাংশই মেয়ে। কিন্তু চা বাগান থেকে পাতা তোলানোর মত দীর্ঘ ও পরিশ্রম সাধ্য কাজ তাদের দিয়ে করানো হয়, এর মজুরিও কম। ফ্যাক্টরির কাজ সাধারণত পুরুষরাই করে। সেখানেও মেয়েরা পায় পাতা বাছাইয়ের কাজ, যন্ত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হয়না বলে রোজগার বাড়ানোর বা উন্নতির সুবিধে থাকেনা। অর্ধেকের বেশি মেয়ে ৪ হাজারের বেশি রোজগার করেন না। ৮ ঘন্টা পরিশ্রম করেও আড়াইশত টাকা মজুরি। অস্থায়ী কর্মী মেয়েরা কোনও মাতৃত্ব ছুটি পায়না। কোনও কাজে যেতে হলে হাফ হাজিরা। ফলে অন্য কোনও সরকারী স্কীমে আবেদন করার কাগজপত্র জমা দিতে যাওয়াও সম্ভব হয়না।
মেয়েদের লড়াই। কেমন সে লড়াই? সে কি সবসময় চোখে দেখা যায়? কেবল স্বাধীনতা আন্দোলনে নয়, তেভাগার মেয়েদের লড়াইয়ের কথা আমরা জানি, মরীচঝাঁপির মেয়েদের কথা। নকশালবাড়ির কৃষক রমণী ও পরে আন্দোলনের নারী কর্মীদের কথা। কোরাপুটের পরজা মেয়েদের, বস্তারের গোণ্ড মেয়েদের, নর্মদা উপত্যকার ভীল রমণীদের দেখেছি নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে। একদিন মেয়েরা দেশের জন্য, সাম্যের জন্য, মতাদর্শের জন্য ও বসতের অধিকার নিয়ে লড়েছিলেন।
দেশ স্বাধীন হল অথচ যত দিন যাচ্ছে নারীর অস্তিত্বের সংকট তত বাড়ছে। তাদের স্বীকৃত ন্যূনতম পাওনা নিয়ে লড়তে হচ্ছে। কাজের পরিবেশ, ছুটি, ন্যূনতম মজুরির মতো আইনি অধিকার নিয়ে। সবটাই লড়াইয়ের জমি। আমরা সম্প্রতি মিড ডে মিল কর্মী, আশা কর্মী, চা বাগানের শ্রমিক মেয়েদের দেখেছি আন্দোলনে। শ্রমিক আন্দোলনে মেয়েদের পাশে দাঁড়াতে সব ইউনিয়নও প্রস্তুত নয়।প্রশাসনিক ব্যবস্থা যদি মেয়েদের অধিকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।
কিন্তু সংঘবদ্ধতা, দৃশ্যমানতা, এগুলিই লড়াইয়ের একমাত্র চিহ্ন নয়। মেয়েদের অদৃশ্য যুদ্ধ চলেছে নানা স্তরে। প্রতিবন্ধী সন্তানকে কোলে করে যে মা ডে কেয়ার সেন্টারে আসেন, যাকে স্বামী ত্যাগ করেছেন, তার লড়াই আমরা জানিনা। অটিস্টিক শিশুর কাছে থাকতে পারলেন না বলে যে ডাক্তার মা আত্মহননকে বেছে নিলেন তিনি কি অসংবেদনশীল বদলি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন না? ক্লান্তি, অপুষ্টি, অবজ্ঞা, পরিবারের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে নিজের জায়গাটুকু টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা - এও তো লড়াই।
কিন্তু কেন এই লড়াই করতেই হবে ক্ষেত্র নির্বিশেষে মেয়েদের?
কারা চায় স্থিতাবস্থা? পরিবার, সমাজ, এমনকি রাষ্ট্রও?
তবে কি মনে করব নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যজাত মুনাফা বইছে আমাদের শাসন ব্যবস্থার শিরা ধমনীতে, তাই বৈষম্য তীব্রতর হয়ে চলেছে? তাই কি দমনের সংস্কৃতি কথা বলে নারীর প্রতি হিংসার ভাষায় এবং নিজের মুখোশ নিজেই খুলে দেয়?
(১৭ই নভেম্বর, ২০২৪ শিলিগুড়িতে দেওয়া তৃতীয় 'রত্না ভট্টাচার্য স্মারক ভাষণ'-এর মূল অংশ।)