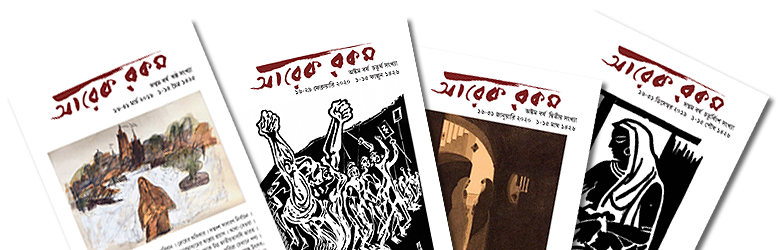আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ দ্বাবিংশ সংখ্যা ● ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ● ১-১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১
প্রবন্ধ
আজকের চিকিৎসা ব্যবস্থাঃ দাম ও মান
প্রতীশ ভৌমিক
বর্তমানে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের মূল্যবৃদ্ধিই মানুষের মূল চিন্তার একমাত্র কারণ নয় বরঞ্চ ওষুধের মান, নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য পরিষেবা, সরকারি চিকিৎসা তথা মৌলিক অধিকার নিয়েই আছে মূল সংশয়।
স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পরিকাঠামোর অভাবে ভারতে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ ছিল স্বল্প, প্রয়োজনীয় ওষুধ ছিল ব্যয়বহুল। বাজারে সিংহভাগ ওষুধই ছিল বিদেশি কোম্পানির, ফলত বাজারে একচেটিয়া ওষুধের দাম ছিল অত্যন্ত বেশি। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার খরচও ছিল অধিক।
১৯৭০ সাল পরবর্তী সময়ে ছবিটা একটু একটু করে বদলাতে শুরু করে। ১৯৭৭ সাল পরবর্তী সময়ে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য কল্যাণ দপ্তর যথেষ্ট অগ্রগতি করতে সক্ষম হয়। ফলে গ্রামভিত্তিক হেল্থ সেন্টারগুলো গড়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক আমল থেকে ব্রিটিশ প্রশাসন স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি যে সামান্য দৃষ্টিপাত করেছিল তার ফলে রোগ সংক্রমণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্যানিটেশন ও রোগ প্রতিরোধ, ভ্যাক্সিনেশন প্রভৃতি বন্দোবস্ত কিছু অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। ফলত কলেরার মতো মহামারির মোকাবিলা করা কিছুটা সম্ভব হয়েছিল। দেশজুড়ে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং এর ফলে রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রাথমিক উদ্যোগ মানব জীবনকে দীর্ঘায়িত করে। মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।
পরবর্তীকালে ন্যাশনাল হেলথ মিশন, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি জনগণকে উজ্জীবিত করেছে। গ্রাম ও শহরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি হেলথ সেন্টার, সাব সেন্টার এবং সরকারি হাসপাতাল সহ একাধিক স্বাস্থ্য কাঠামো ক্রমশ তৈরি হয়েছিল। জনস্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরে সংগঠিত হয়েছে। তৃতীয় স্তর হল জেলা সাধারণ হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজগুলি।
আবার আজকের সময়ে আশ্চর্যজনকভাবে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ও জেলা হাসপাতালে চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীদের নিয়োগ বন্ধ। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সহ অক্সিজেন ইত্যাদির অভাবে কর্মরত চিকিৎসক বা চিকিৎসা কর্মীদের অবস্থা ভয়াবহ। গ্রামীণ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও সরঞ্জাম না থাকায় অসুস্থ রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখোমুখি হচ্ছেন চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীরা। রোগীর স্বাস্থ্যের জটিলতায় এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে রোগীকে পাঠাতে হচ্ছে। অপ্রতুল চিকিৎসক, পরিকাঠামোর অভাব, বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে পাঠানো 'রেফার্ড' রোগীর সংখ্যা ক্রমে বেড়ে গিয়ে চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটছে।
সার কথা, তৃতীয় স্তরে রোগী পরিষেবার জন্য যত সংখ্যক চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীর প্রয়োজন তা নেই, নেই জীবনদায়ী ওষুধ। হাসপাতালগুলোতে বেসরকারিকরণের হাত ধরে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা, ইউএসজি, এক্স-রে ও অন্যান্য রোগনির্ণয় পদ্ধতি করতে খরচ বাড়ছে, করোনা মহামারির সময় থেকে এই বেসরকারিকরণের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন জেলায় প্রান্তিক স্তরে হাসপাতালগুলোতে ইউনানী, হোমিও ও ডেন্টাল চিকিৎসক দ্বারা কাজ চালান হয়। ফলতঃ গ্রামের মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ক্রমাগত ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে।
গ্রাম অঞ্চলে সরকারি পরিষেবা বলতে ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের কাজের পাশাপাশি ইমুনাইজেশন প্রক্রিয়ার কর্মসূচি, অন্তঃসত্ত্বা মায়ের যত্ন, আন্ত্রিক, দূষণ প্রতিরোধ এইসব অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলোও ব্যাহত হচ্ছে। বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং 'সেন্ট্রাল মেডিসিন সাপ্লাই' (সিএমসি)-র মাধ্যমে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া শুরু হয়েছিল। বর্তমান সরকার ওইসব ব্যবস্থা তুলে দিতে প্রয়োজনীয় সব ওষুধ সরবরাহ করছে না। রোগীকে 'ফেয়ার প্রাইস শপ'-এর উপর নির্ভরশীল করে তুলছে। ক্রমশঃ সরকারি দলের আশ্রিত ঠিকাদারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এই দায়িত্ব। এদের মধ্যে অনেকের চিটফান্ড সংস্থার সঙ্গে যোগ রয়েছে, যেমন রায়গঞ্জে 'ভিবজিওর', হাওড়া ও পুরুলিয়াতে 'অন্নপূর্ণা', মুর্শিদাবাদে 'সাহা এজেন্সি' ইত্যাদি। এছাড়া 'এম. এস. লাইফ' নামে অনেকগুলো দোকান ওই সংস্থার রমরমা ব্যবসা তৈরি করেছে। সরকারি সম্পত্তির উপর গড়ে ওঠা এই ওষুধ ব্যবসা সম্পর্কে কিছু না বললেই নয়।
ক) সরকারি ভর্তুকিতে পাওয়া বিনামূল্যের ওষুধের ঘাটতি তৈরি করে জনগণকে ওই 'ফেয়ার প্রাইস শপ' থেকেই ওষুধ কিনতে বাধ্য করছে।
খ) চিকিৎসকদের প্রতিটি হাসপাতাল থেকে জেনেরিক নামে ওষুধ লিখতে বাধ্য করা হয়। প্রেসক্রিপশনে ওষুধের কোনো ব্র্যান্ডের নাম উল্লেখ না থাকার কারণে ওই ‘ফেয়ার প্রাইস শপ’ থেকে রোগীকে দোকানের সাপ্লাই করা ‘ব্রান্ডেড ওষুধ’ বিক্রি করা হয়। বিল করার সময় জেনেরিক নামে লেখা হয়। জেনেরিক নামে বিল করার উদ্দেশ্য হল দোকানের নিজস্ব পছন্দের ব্রান্ড ওষুধটি বিক্রি করার পর ব্রান্ডেড ওষুধ বিক্রির প্রমাণ থাকে না। এই পদ্ধতিতেই ওই ঠিকাদার বা রাজনৈতিক দলের আশ্রিত ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে। আশ্চর্যজনকভাবে ওই ওষুধ ৫০ শতাংশ থেকে ৭৬ শতাংশ ছাড় দিয়েও বাজারের ভালো কোম্পানির ওষুধের থেকেও অনেক বেশি দামি। ২০১৩ থেকে শুরু করে বহু পত্রিকায় বহুবার প্রকাশিত হয়েছে এই 'ফেয়ার প্রাইস প্রাইস শপ'-এর বিক্রি হওয়া স্যালাইন বোতলে ফাংগাস পাওয়া গেছে। স্যালাইন ওয়াটারের মানও অত্যন্ত নিম্নমানের। ১ জুন, ২০১৩ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর, কোনো হাসপাতালে 'ফেয়ার প্রাইস শপ'-এর ওষুধ নিম্নমানের হলে জরিমানা ও ব্ল্যাক লিস্টেড করা হবে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও বাস্তবে এই ওষুধ নিয়ে পরবর্তীতে শুধু কথার কথাই রয়ে গেছে।
হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ‘ব্র্যান্ডের’ ওষুধ লেখার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকায় চিকিৎসকরা রোগীদের ওই 'ফেয়ার প্রাইস শপ'-এর নিম্নমানের ওষুধ খেলেও কিছু বলতে পারছেন না। চিকিৎসকদের সংগঠন এ.এইচ.এস.ডি.-র পক্ষ থেকে অনেক আগেই সরকারের কাছে দাবি রাখা হয়েছে, 'ফেয়ার প্রাইস শপ'-এর নামে ধোঁকা হচ্ছে, যেখানে চুক্তি অনুযায়ী জেনেরিক ওষুধ থাকার কথা সেখানে নিজেদের ‘ব্রান্ডেড ওষুধ’-ই বিক্রি করছে দোকান মালিকরা। যেখানে একজন ফার্মাসিস্ট থাকা আবশ্যিক, কাগজপত্রে লেখা থাকলেও কোনো ফার্মাসিস্ট দোকানে উপস্থিত থাকেন না। ডাক্তারদের কথায় হাসপাতালের বিনামূল্যের ওষুধ এখন জনগণকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে 'ফেয়ার প্রাইস শপ' নামের দোকান থেকে। এই বিষয়ে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এ্যান্ড সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়ন' বহু প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করেছিল - কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি।
বর্তমানে হাসপাতালে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাবে সাধারণ মানুষ নিজেদের পকেটের টাকায় নিম্নমানের ওষুধ ও সরঞ্জাম কিনতে বাধ্য হচ্ছে, সরকার থেকে ওষুধের উপর গড়ে ১২ শতাংশ জিএসটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে যা অসুস্থ মানুষের প্রতি অমানবিক পদক্ষেপ - ইতিমধ্যে দাবি উঠেছে ওষুধের উপর জিএসটি মকুব করতে হবে। খবরে প্রকাশিত হাসপাতালের গ্লাভস ও সিরিঞ্জ সহ অন্যান্য সরঞ্জাম নিম্নমানের, এমনকি তাতে রক্তের দাগ লাগা রয়েছে৷ এমন নির্লজ্জ দুর্নীতি করা হয়েছে যে সরকারের ঘরে রিসাইকেল করা সামগ্রী আসছে, যার থেকে মারাত্মক রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকছে।
ইতিমধ্যে খবরে প্রকাশ হয়েছে, রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে স্যালাইনে ফাংগাস, হাসপাতালে জাল ওষুধ। বাজারে ৫০টি কোম্পানির ওষুধ তাদের গুনমাণ যে ১০০ শতাংশ সঠিক তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণের রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে সরকার তার চূড়ান্ত দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না, এক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রের দুই সরকারের উত্তর নেই। এই অরাজক পরিস্থিতিতে যেখানে জাল ওষুধ, নিম্নমানের ওষুধের জন্য মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন উঠছে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার কোন যুক্তিতে ৫০টি-র বেশি জীবনদায়ী ওষুধের দাম সরাসরি বাড়িয়ে দেয়! ইতিমধ্যে গত এপ্রিল ২০২৪-এ ওষুধের দাম ১২ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল। এছাড়া নির্বাচনে ফার্মা কোম্পানিগুলোর থেকে রাজনৈতিক দলগুলো কোটি কোটি টাকা চাঁদা তুলেছে, পরিবর্তে সরকার ওষুধের দাম বাড়িয়েছে।
একদিকে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের, খাদ্য দ্রব্যের আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, যেখানে কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই, অন্যদিকে সরকার কর্তৃক ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা নেই৷ সাধারণ মানুষ ব্যক্তিগত মালিকানার কর্তৃপক্ষের বঞ্চনার শিকার। ছাঁটাই বাড়ছে, হাতে চাকরি নেই, রোজগার কমেছে, সেখানে স্বাস্থ্য খাতে খরচ বাড়ছে তীব্র গতিতে। অথচ রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্রমাগত বেসরকারিকরণের পথে দু’পা এগিয়ে।
বর্তমানে রাজ্যের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের দ্বারা জনগণের জন্য সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ দিচ্ছে। পাশাপাশি কিছু বেসরকারি হাসপাতালে আংশিকভাবে চিকিৎসা করার সুযোগ দিচ্ছে - অবশ্য সেখানে প্রায় অর্ধেক টাকা নিজের থেকে দিতে হচ্ছে। আশ্চর্যজনকভাবে সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যের চিকিৎসা ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স কোম্পানী, ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্সুরেন্স কোম্পানী, বাজাজ অ্যালায়েঞ্জ, ইফকো টোকিও ইত্যাদি কর্পোরেট সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এজেন্সির মাধ্যমে সরকারের ঘরের টাকা এজেন্ট মাধ্যমেই কর্পোরেটকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সরকারের কোষাগারের টাকা কর্পোরেটকে সমৃদ্ধ করছে, আবার জনগণকে বেসরকারি হাসপাতালে যত্নসহকারে ঠেলে দিচ্ছে।
প্রশ্ন হল সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা কি নিঃশব্দে বেসরকারি কর্পোরেটের হাতে চলে যাচ্ছে? জনগণের মৌলিক অধিকার কি হাতছাড়া হতে চলেছে?