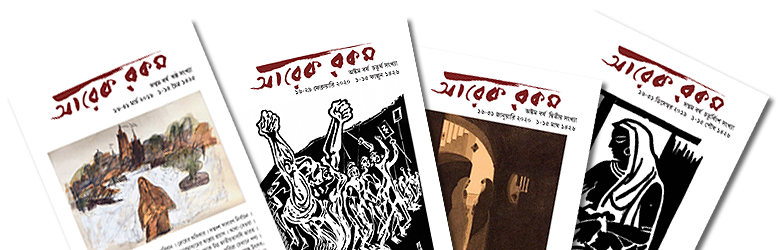আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ একবিংশ সংখ্যা ● ১-১৫ নভেম্বর, ২০২৪ ● ১৫-৩০ কার্তিক, ১৪৩১
প্রবন্ধ
নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ বদলে আসামে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে মরিয়া বিজেপি
মৃন্ময় সেনগুপ্ত
গত ১৭ অক্টোবর নাগরিকত্ব আইনের ৬ক ধারা বহাল রাখার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ আসামের ক্ষেত্রে নাগরিকত্বের ভিত্তি বর্ষ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চই বহাল রইল।অসম সম্মিলিত মহাসংঘ ও ইন্ডিজেনাস ফোরাম আসামেও ১৯৫১ সালকে নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ করার জন্য মামলা করেছিল। সেই মামলায় প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় সহ পাঁচ জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত সাংবিধানিক বেঞ্চ এই রায় দেন। আদালতের মতে নাগরিকত্ব আইনের ৬ক ধারাই আসামে নাগরিকত্ব সমস্যার আইনি সমাধান সূত্র।
বিজেপি বহুকাল ধরে ৬ক ধারা বাতিল করে ১৯৫১ সালকে আসামে নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ করার দাবি জানিয়ে আসছে। এক দেশ, এক আইনের ধুয়ো তুলে এনআরসি নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতাকেই তারা আরও বাড়াতে চায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চকে ভিত্তি বর্ষ করার পর যেখানে আসামে এনআরসি তালিকা থেকে ১৯ লক্ষের বেশি মানুষের নাম বাদ পড়েছে, সেখানে ১৯৫১ সালকে ভিত্তিবর্ষ করলে আরও বহু সংখ্যক মানুষ বিদেশি বা সন্দেহজনক বলে চিহ্নিত হবেন। আপাতভাবে মনে হতে পারে যে, বিজেপি’র দাবি ন্যায়সঙ্গত। সারা দেশে প্রযোজ্য নিয়ম, আসামের বেলায় খাটবে না কেন? মনে রাখতে হবে, আসাম তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিস্থিতি সারা দেশের থেকে আলাদা। আসামেই একমাত্র ১৯৫১ সালে এনআরসি হয়েছিল। ডি ভোটার, ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। বিজেপি আসামের মতো সারা দেশেই এসব চালু করতে চায়। ১৯৮৫ সালের আসাম চুক্তি অনুসারে নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ সালের সংশোধন ঘটিয়ে ৬ক ধারা যুক্ত করা হয়। এটি কেবল আসামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
আসাম চুক্তি অনুসারে নাগরিকত্ব
● ১৯৬৬ সালের পূর্ব থেকে আসামে বাস করা মানুষ।
● ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যে যারা বিদেশ থেকে ভারতে এসেছেন। তবে তাঁদের দশ বছর পর ভোটাধিকার দেওয়ার কথা (বাস্তবে, এটি ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল ও বর্ডার পুলিশের ওপর নির্ভরশীল। যাদের ভূমিকা নিয়ে বহু অভিযোগ রয়েছে)।
● ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর যাঁরা বিদেশ থেকে আসামে এসেছেন, তাঁরা নাগরিকত্ব পাবেন না।
আসামে নিয়ম আলাদা হওয়ার কারণ খুঁজতে গেলে, দীর্ঘদিন ধরে সে রাজ্যে চলা পরিচিতি সত্তার রাজনীতি বিচার করতে হবে। যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'আসাম' বলে পরিচিত আজকের ভূখন্ড আর তার জনবিন্যাসের পরিবর্তনের সাম্প্রতিক ইতিহাস।
ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত আসামের জনবিন্যাস ও জনগোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক
আজকের আসাম বলতে যে ভূখণ্ড বোঝায় তার অস্তিত্ব ব্রিটিশ আমলের আগে ছিল না। তখন এই অঞ্চলগুলি ছিল নানা রাজার শাসনাধীন। ব্রিটিশ আমলের আগে থেকেই নানা ধর্ম, ভাষা, জনজাতির মানুষ আসামে বসবাস করে। বাইরে থেকে আসা মানুষের স্রোত বারে বারে আসামের জনবিন্যাস বদলে দিয়েছে। আহোমদের মূলবাসী বলে দাবি করা হলেও তারা বহুযুগ ধরে আসামের বাসিন্দা নয়। আবার বাংলাভাষী বা মুসলমান মাত্রই বহিরাগত সে তত্ত্বও সঠিক নয়। গৌড়বঙ্গের পাল রাজাদের সাম্রাজ্য আসামে বিস্তৃত হয়েছিল। তখন থেকেই আসামে বাংলাভাষী মানুষ আসতে শুরু করে। কোচবিহারের রাজার শাসনাধীন অঞ্চলে কোচ-রাজবংশীদেরও বাস ছিল। আহোম ও মুসলমানদের আগমনের শুরু, মোটের ওপর আজ থেকে সাত-আট শতক আগে। আহোমরা এসেছিল, বার্মা-তাইল্যান্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে। আবার বোড়োরা ভুটান, তিব্বত থেকে এখানে এসেছিল।
১৮২৬ সালে বার্মার সঙ্গে ইয়ান্দাবু সন্ধিতে ব্রিটিশরা আসামে শাসনক্ষমতা পায়। সরকারি ও প্রশাসনিক কাজের জন্যে বাংলা থেকে অনেককে ব্রিটিশরা নিয়ে যায়। এরা ছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দু বাঙালি। আসাম তখন উড়িষ্যা, বিহারের মতো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মধ্যে ছিল। ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থেই 'বাংলা ভাষা'কে আসামের সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেয়। ১৮৭৪ সালে সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে 'আসাম কমিশনার প্রভিন্স' গঠিত হয় (স্বাধীনতার পর অবশ্য সিলেট পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়)। এই তিনটি অঞ্চল কিন্তু বাংলাভাষী, বিশেষত মুসলমান-বাঙালি অধ্যুষিত ছিল। ফলে আসামে বাঙালি-মুসলমানের অনুপাত বেড়ে যায়। মনে রাখতে হবে, এরা বহিরাগত নয়, মূলবাসী। ১৮৮১ সালের জনগণনায় আসামে মুসলমানের অনুপাত হয় মোট জনসংখ্যার ২৮.৬ শতাংশ।
তেলখনি, রেলপথ, চা বাগানের জন্য বাইরে থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী, জনজাতির লোককে ব্রিটিশরা নিয়ে যেতে শুরু করে। বিহার, উড়িষ্যা থেকে সাঁওতাল, ওরাঁও প্রভৃতি জনজাতিকে শ্রমিক হিসেবে, পূর্ববঙ্গ থেকে বহু মানুষকে চাষের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলকে এরা চাষযোগ্য করে তোলে। দুর্গম অঞ্চলে বন্যা, নদী ভাঙ্গনকে সঙ্গী করে আসামের কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এরা করেছিল। এদের সিংহভাগই বাংলাভাষী মুসলমান। যাদের এখনও চরুয়া, মিয়া এসব সম্বোধনে বিদ্রূপ করা হয়। তাদেরই আজ 'বিদেশি' বলে দাগিয়ে দিতে বিজেপি সরকারের উৎসাহ অন্তহীন। আসামের জমিদাররাও চাষের জন্য এদের বসতি স্থাপনে উৎসাহী ছিল। আসামে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের আগমনে অসমভাষীরা সংখ্যালঘু হয়ে যায়। ১৯২১ সালেই অসম ভাষীর সংখ্যা ৫০ শতাংশের নিচে নেমে যায়। ১৯৩১ সালের জনগণনায় দেখা যায়, তাদের অনুপাত মোট জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশ।
বোড়ো, রাভাদের জমির ব্যক্তি মালিকানা ছিল না, ছিল সামাজিক মালিকানা। তারা জুম প্রথায় চাষ করত। একদিকে পূর্ববঙ্গের কৃষকদের সংখ্যাবৃদ্ধি, অপরদিকে চা বাগানের জন্য জমি অধিগ্রহণে বোড়োরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী উন্নয়নের শিকার এইসব জনজাতির অস্তিত্বের সঙ্কট ধীরে ধীরে পরিচিতি সত্তার রাজনীতির ভিত তৈরি করে। যা পরবর্তীকালে বোড়োল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং গণহত্যায় মেতে উঠবে।
১৯৩৭ সালে আসামে মুসলিম লিগের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সরকার বেশিদিন চলেনি। কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বারেবারে সরকার বদলেছে। দুই দলের ক্ষমতার রাজনীতিতে অসমভাষীদের সঙ্গে বাংলাভাষী মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে।
স্বাধীন ভারতে পরিচিতি সত্তার রাজনীতি
অসমিয়া জাতীয়তাবাদের জমি কিন্তু বিজেপি নয়, তৈরি করেছিল কংগ্রেস। বিজেপি তাকে 'হিন্দুত্ববাদ'-এ রূপান্তরিত করতে চাইছে মাত্র। দেশভাগের কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে বহু উদ্বাস্তু আসামে আসতে থাকে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের নীতি অসমভাষীদের আরও শঙ্কিত করে। বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিজ রাজ্যে পরবাসী করে দেবে বলে তাদের আশঙ্কা বাড়তে থাকে। কংগ্রেস প্রথম থেকেই সেই আশঙ্কাকে মূলধন করে অসমিয়া জাতীয়তাবাদের জমি তৈরি করতে শুরু করে। সেই পরিচিতি সত্তার রাজনীতি ক্রমশ হিংস্র হয়ে ওঠে। নিরাপত্তা বা রুজি রোজগারের তাগিদে চা শ্রমিক ও বাঙালি-মুসলমানদের অনেকেই অসমিয়াকে মাতৃভাষা বলে মেনে নেয়। তবে একথা ঠিক যে, বাংলাভাষী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মানসিক ব্যবধান আগে থেকেই ছিল। হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে মুসলমান ভূমিহীন কৃষকদের শ্রেণিগত দূরত্বকে অসমিয়া জাতীয়তাবাদীরা কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। ১৯৭১ সালের জনগণনায় অসমভাষীর সংখ্যা দাঁড়ায় রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৭১ শতাংশ।
১৯৫১ সালে সারা ভারতে জনগণনা হয়। আসামে জনগণনার সময়ে রাজ্যবাসীদের একটা ফরম্যাট পূরণ করতে হয়েছিল। তারা যে ১৯৫০ সালের আগে থেকেই আসামে বসবাস করছে, তার প্রামাণ্য নথি দেখাতে হয়েছিল। যার ভিত্তিতে আসামে জাতীয় নাগরিক পঞ্জী (এনআরসি) প্রস্তুত করা হয়। একমাত্র আসামেই এই এনআরসি হয়েছিল। যদিও তা ছিল অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ। অনেকের নামই এনআরসি-তে স্থান পায় নি। দুর্গম চর অঞ্চলে এনআরসি’র কাজ ঠিকমতো হয় নি। ১৯৫০ সালে দ্য ইমিগ্রেশন (এক্সপালশন ফ্রম আসাম) আইন চালু করে অনেককেই পূর্ব পাকিস্তানে বিতাড়ন করা হয়েছিল। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির পর তাদের অনেকে ফিরে এলেও, সকলে আসতে পারে নি।
১৯৬০ সালে অসমিয়াকে সরকারি ভাষা করার সিদ্ধান্তে বাংলা ও অসমভাষীদের সংঘর্ষ বাড়তে থাকে। তারই মর্মান্তিক পরিণতি ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচরে এগারো জনের ভাষা শহিদ হওয়া। বাংলা ভাষা আন্দোলনের সেই শহিদদের আজও দেশের নানা প্রান্তে স্মরণ করা হয়। প্রোজেক্ট অফ প্রিভেনশন অফ ইনফিলট্রেশন (পিআইপি)’র মাধ্যমে ছয়ের দশকে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে সরকার পূর্ব পাকিস্তানে বিতাড়িত করে। ১৯৬৪ সালে গঠিত হয় 'ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল'। বিদেশি আইন অনুসারে অভিযুক্তকেই নাগরিকত্বের প্রামাণ্য নথি দিতে হয়। অর্থাৎ অভিযোগকারীকে অভিযোগের সত্যতা নয়, অভিযুক্তকে নির্দোষের প্রমাণ দিতে হবে। সেই সময়ে কংগ্রেস সরকারের গঠিত এই ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালকেই কাজে লাগাচ্ছে আজকের বিজেপি সরকার।
১৯৭৮ সালে আসামে স্বাধীনতার পর প্রথম অ-কংগ্রেসি সরকার গঠিত হয়। ২৩ জন বামপন্থী বিধায়ক হন। এত সংখ্যক বাম বিধায়ক আসামের রাজনীতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অভূতপূর্ব এই ঘটনা পরিচিতি সত্তার রাজনীতির বিপরীতে শ্রেণি রাজনীতির এক সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। সেই সম্ভাবনাকে প্রথমেই ধ্বংস করার পরিকল্পনা শুরু হয়। অসমিয়া জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সুকৌশলে, অনেকখানি গোপনে অনুপ্রবেশ ঘটে সংঘ পরিবারের। অসমভাষীদের অস্তিত্ব বাঁচানোর নামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের নীল নকশা প্রস্তুত হতে থাকে। ভাষা ভিত্তিক পরিচিতি সত্তার রাজনীতিকে ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার প্রয়াস। সেদিন আসামে সংঘ পরিবার প্রায় অস্তিত্বহীন হলেও, আজ তাদের রাজনৈতিক সংগঠনই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায়। ১৯৭৯ সালের আসামে মঙ্গলদই লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন করার কাজ শুরু হয়। বহু বিদেশির নাম তালিকায় রয়েছে এই অভিযোগে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী আন্দোলন। অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আসু) ও অল আসাম গণ সংগ্রাম পরিষদ 'বাংলাদেশি খেদাও’-র ডাক দেয়।
আসামজুড়ে ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নেমে আসে। একের পর এক গণহত্যা সংঘটিত হয়। ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আসামের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়। ভোটার তালিকা থেকে বিদেশি নাম বাদ দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনকারীরা ভোট বয়কটের ডাক দেয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি সংগঠিত হয় নেলি হত্যাকাণ্ড। নগাঁও জেলার সেই কুখ্যাত গণহত্যাকান্ডে এক দিনেই প্রায় দু’হাজার মুসলমানকে খুন করা হয়। আসাম জুড়ে বাঙালি, বিশেষত মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে এমন একের পর এক গণহত্যা সংগঠিত হয়। অবশেষে ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়। দেশের তখন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া।
যদিও এই চুক্তির পরেও ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ কিন্তু কমে নি। আসাম চুক্তির পর হিতেশ্বর শইকিয়া কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ভেঙে দেন। বিধানসভা ভোটে জেতে অসম গণ পরিষদ (অগপ)। ১৯৮৭ সাল থেকে পৃথক বোড়োল্যাণ্ড রাজ্যের দাবিতে একের পর এক গণহত্যা ঘটতে থাকে। আক্রমণের লক্ষ্য মুসলমান, সাঁওতাল, ওরাঁও জনগোষ্ঠী। ১৯৯৭ সালে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন আসামে ভোটার তালিকা সংশোধনে ডি ভোটারের বিষয়টি যোগ করে। বিদেশি বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তি মাত্রেই ডি ভোটার হিসেবে চিহ্নিত হন ও যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা দেশের নাগরিক হিসেবে প্রমাণিত হবেন ততক্ষণ তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। আগেই বলা হয়েছে, এই প্রমাণ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকেই দিতে হবে।
বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার আসামের মতো সারা দেশেই এনআরসি করার জন্য ২০০৩ সালে বিধি জারি করে। সেই বিধিতে কেবলমাত্র আসামের জন্য ৪ক ধারা যুক্ত করা হয়। যা আসলে নাগরিকত্ব আইনের ৬ক ধারার অনুসারী। রাজনৈতিকভাবে আসাম চুক্তির বিরোধী হলেও সাংবিধানিক দায়বদ্ধতায় ৬ক ধারাকে এনডিএ সরকার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।
২০০৪ সালের ভোটে কেন্দ্রে এনডিএ সরকার হেরে যায়। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ ক্ষমতায় আসে। দেশজোড়া এনআরসি'র কাজ স্থগিত হলেও, ২০০৫ সালে কেন্দ্রের ইউপিএ, আসামের কংগ্রেস সরকার এবং আসুর বৈঠকে ১৯৫১ সালের এনআরসি নবীকরণের সিদ্ধান্ত হয়। যদিও অশান্তির জন্য তা বাস্তবায়িত হয় নি। ২০১৪ সালে এক জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আসামে এনআরসি নবীকরণের নির্দেশ দেয়। কেন্দ্রে ততদিনে ইউপিএ সরকারের বদলে এসেছে মোদি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট প্রকাশিত এনআরসি নবীকরণের চূড়ান্ত তালিকায় ১৯ লক্ষ ৬ হাজার ৬৫৭ জনের নাম বাদ পড়ে। যার মধ্যে ১২ থেকে ১৪ লক্ষ হলেন হিন্দু বাংলাভাষী।
বিজেপি'র সাপ হয়ে কাটা ও ওঝা হয়ে ঝাড়ার নীতি
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে থেকে আসামে বসবাস করার প্রামাণ্য নথি দেখাতে না পারায় অনেকের নাম এনআরসি তালিকা থেকে বাদ যায়। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সহযোগিতার ভূমিকা পালন না করে, নাম না তোলাতেই বেশি আগ্রহী ছিল বলে অভিযোগ। নিয়মের জটিলতায় অনেক যোগ্য আবেদনকারীর নাম বাদ যায়। আবার এনআরসি'র চূড়ান্ত তালিকা অসমিয়া জাতীয়তাবাদীদেরও অসন্তুষ্ট করে। তাদের মতে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যাটা নাকি প্রায় ৪০ লক্ষ। এনআরসি'র চূড়ান্ত তালিকায় বাদ যাওয়া ও ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দিদের মধ্যে সিংহভাগ হিন্দু হওয়ায়, মুসলমান অনুপ্রবেশকারী নিয়ে বিজেপি'র প্রচারও ভুল বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপি বলেছিল যে, আসামে ৩৪ শতাংশ বিদেশি রয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনায় দেখা যায় যে, সে রাজ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৩৪.২২ শতাংশ। আসলে মুসলমান মাত্রই বিদেশি বলে তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সেবার নির্বাচনী প্রচারে বলেছিলেন যে, রাজ্যের ৩৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আগেই আলোচনা হয়েছে যে, আজকের আসামের অনেকাংশে মুসলমানরা মূলবাসী। অনেকে আবার এসেছিল ব্রিটিশ আমলে। তাই এই পরিসংখ্যান যদি সত্যিও হয়, তাহলেও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিজেপি তাদের বিদেশি বলে এবং এনআরসি’র ধুয়ো তুলে তীব্র বিদ্বেষের পরিবেশ সৃষ্টি করে। ২০১৬ সালের সেই নির্বাচনে জিতে বিজেপি আসামে প্রথম ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় এসেই তারা 'ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল'কে প্রভাবিত করতে থাকে। ২০১৭ সালের জুন মাসে আসাম সরকার ট্রাইব্যুনালের ১৯ জন বিচারককে সরিয়ে দেয়। তাঁরা দু’বছরে ৪০ হাজার এমন রায় দিয়েছিলেন, যেখানে বর্ডার পুলিশের দ্বারা অভিযুক্ত বিদেশিরা ভারতের নাগরিক হিসেবে প্রমাণিত হন। এটাই তাঁদের অপরাধ। তাঁরা গুয়াহাটি হাইকোর্টে মামলা করলে, আদালত বলে, বিচারকদের কাজের মূল্যায়নের অধিকার সরকারের নেই। এরপরেও নির্লজ্জ বিজেপি সরকার ১৫ জন বিচারককে তাঁদের কাজের জন্য সতর্ক করে। বিচারকদের কাজে কার্যত নাক গলাতে গঠন করা হয় 'স্ক্রিনিং কমিটি'।
২০১৯ সালে এনআরসি'র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরে বিজেপি নাগরিকত্ব আইন সংশোধনী (সিএএ)-কে সামনে আনে। শুরু করে এনআরসি এবং সিএএ-কে গুলিয়ে দেওয়ার খেলা। আগে এনআরসি, না আগে সিএএ। বিজেপি ২০১৯ সালে কেন্দ্রে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পরেই সিএএ সংসদে পাশ করানো হয়। এনআরসি আর সিএএ-কে আলাদা করে দেখলে ভুল হবে। বিজেপি সেটাই করতে চায়। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে সিএএ সংক্রান্ত বিধি চূড়ান্ত করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। সংশোধিত আইন অনুসারে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে যাঁরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরা নাগরিকত্ব পাবেন। তবে মুসলমানরা পাবেন না। অর্থাৎ নাগরিকত্বের সঙ্গে যেমন ধর্মীয় পরিচয় জুড়ে দেওয়া হল, তেমন ভিত্তিবর্ষ হল ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর।
একদিকে সিএএ'র মাধ্যমে নাগরিকত্বে ভিত্তিবর্ষ ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর, অপরদিকে আসামে নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ ১৯৫১ সাল করার চেষ্টা - বিজেপি'র এই দ্বিচারিতার কারণ কী? অসম ও বাংলাভাষীদের মধ্যে বিদ্বেষ জাগাতে তারা কেবল এনআরসি চায় তাই নয়, ভিত্তিবর্ষেরও পরিবর্তন চায়। এতে অসমভাষীরা যেমন বিজেপির ওপর সন্তুষ্ট হবে, তেমন 'আসাম চুক্তি' অবৈধ প্রমাণ করতে পারলে কংগ্রেসকেও কোণঠাসা করা যাবে। অগপ এনডিএ-র সঙ্গী হলেও, আজ জমি অনেকখানি হারিয়েছে। কংগ্রেসকে কোণঠাসা করতে পারলে বিজেপি আরও স্বস্তিতে থাকবে। তাই নাগরিকত্ব আইনের ৬ক ধারা বিজেপি বাতিল করতে চাইছে।
এর ফলে অসম ও বাংলাভাষীদের মধ্যে আবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা। আর তখনই বিজেপি হিন্দু-বাঙালিদের ত্রাতা সাজবে। সিএএ দেখিয়ে বলবে তাঁদের ভয় নেই। যদিও সিএএ অনুসারে আবেদন করলেই নাগরিকত্ব পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। বাঙালিদের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন বাড়বে। হিন্দু বাঙালিরাও সিএএ-র জন্য বিজেপি'র প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য হবে। অসমভাষী ও হিন্দু-বাঙালি - দুই পক্ষেরই কংগ্রেসের প্রতি ভরসা কমবে। এটাই হল বিজেপির ছক। পরিণামে ভাষা ও ধর্মকে কেন্দ্র করে বিদ্বেষের রাজনীতি বাড়লেও বিজেপির কিছু আসে যায় না। সারা দেশে তারা এটাই চায়। যার ভয়াবহ পরিণাম আমরা আজকে মণিপুরে দেখতে পাচ্ছি।
আসল লক্ষ্য কর্পোরেট ও রাষ্ট্রের একাধিপত্য
অসমিয়া জাতীয়তাবাদের অন্যতম ডাক 'জাতি-জমি-ভিত' (জাতি, মাটি, ভেতি)। এর থেকেই বোঝা যায় যে, প্রথম থেকেই জমির লড়াইকে অসমিয়া জাতিসত্তার সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। জমির লড়াই, শ্রমজীবি মানুষের অধিকারের লড়াইয়ের বদলে শ্রমজীবি মানুষেরাই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় মেতে উঠেছে। শ্রেণি আন্দোলনের উপাদান মজুত থাকলেও, পরিচিতি সত্তার রাজনীতি তা বিনষ্ট করেছে। আসাম চুক্তির প্রায় চল্লিশ বছর পরেও, পরিস্থিতির উন্নতি হয় নি। বরং আরও জটিল হয়েছে। বিজেপি সরকার জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে ভূমিপুত্রের সংজ্ঞা হিসেবে ১৯৫১ সালকে ভিত্তিবর্ষ করেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সেই পদক্ষেপের বৈধতা অবশ্য প্রশ্নচিহ্নের মুখে। আসাম সহ উত্তর-পূর্ব ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী। জনজাতি, ভাষা, ধর্মের ভিত্তিতে সংঘর্ষ বাড়লে, সেই সম্পদে কর্পোরেটের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। আসাম সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে পরিচিতি সত্তার রাজনীতি হিংস্র হওয়ার পাশাপাশি নির্মাণ প্রকল্প, শিল্পের নামে কর্পোরেট বিনিয়োগও বাড়ছে।
আবার এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম।প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশ দিয়ে ঘেরা এই অঞ্চলে চাই রাষ্ট্রের সদর্প, বাহুবলী উপস্থিতি। অশান্তি থাকলে, রাষ্ট্রের শক্তি প্রদর্শনের সুযোগও থাকে। তাই এনআরসি, সিএএ-র কোনোটাই আসামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করবে না, বরং অশান্তি বাড়াবে। এই অশান্তি এড়াতে চাই রাজনীতির অভিমুখ বদল। ভাষিক বা ধর্মীয় পরিচয়ের রাজনীতি নয়, শ্রেণি রাজনীতিই পারবে এই অবস্থার বদল ঘটাতে।