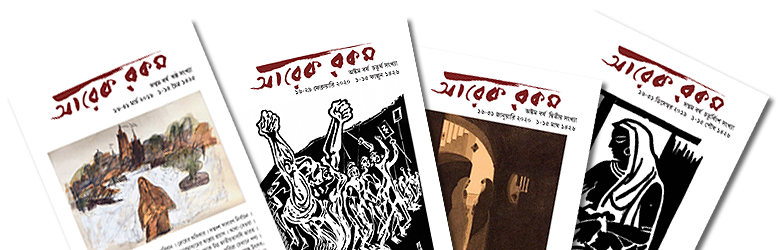আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ একবিংশ সংখ্যা ● ১-১৫ নভেম্বর, ২০২৪ ● ১৫-৩০ কার্তিক, ১৪৩১
প্রবন্ধ
ডাক্তারদের আন্দোলন - প্রাসঙ্গিক কিছু কথা
শ্যামাশীষ ঘোষ
ন্যায়বিচারের দাবি
রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তারদের সাম্প্রতিক আন্দোলন জনমানসে এক সুগভীর প্রভাব ফেলেছে। সরকারি হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তার, এমনকি বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তাররাও এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে গেছেন। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভয়াবহ চেহারা প্রকট হয়ে উঠেছে। সরকার-পুলিশ-প্রশাসনের নির্লজ্জ আচরণ দিনে দিনে বাড়ছে। কয়েকজন জুনিয়র ডাক্তার আমরণ অনশনে বসেছেন, তাঁদের শারীরিক অবস্থা দিনে দিনে অবনতির দিকে যাচ্ছে অথচ শাসক মেতে আছে উৎসবে; পাড়ার ক্লাব, সাধারণ মানুষ সকলকে উৎসবে নামতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা চলেছে নির্লজ্জভাবে - এই অন্যায়ের স্মৃতি ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রতিবাদীদের উপর পুলিশি নির্যাতন ও হয়রানি সত্ত্বেও মানুষ প্রতিবাদে অনড় থেকেছে। দুর্গাপূজায় মণ্ডপে মণ্ডপে মানুষের ভিড় হয়েছে, তবে প্রতিবাদের চেহারাও আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে তা দেশের এবং বিদেশের মানুষের মনেও ছাপ ফেলেছে। সুপ্রীম কোর্টের নজরদারিতে, সিবিআই এই অপরাধের এবং তার সঙ্গে এই ঘটনার তথ্যপ্রমাণ লোপ করার কাজে দোষীদের খুঁজে বার করার এবং উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের কাজে নিযুক্ত। সুতরাং ন্যায়বিচারের প্রাথমিক বিষয় অর্থাৎ দোষীদের শাস্তিপ্রদানের দায়িত্ব সিবিআইয়ের হাতে।
জুনিয়র ডাক্তাররা রাজ্য সরকারের কাছে যে দাবিপত্র পেশ করেছে, তাতে অভয়ার উপর অত্যাচারের বিচারের দাবির সঙ্গে ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যেও নির্দিষ্ট ব্যবস্থাগ্রহণের দাবি আছে। এককথায়, সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থায় দুর্নীতি, হুমকি সংস্কৃতির সমূল উৎপাটনের দাবিই মুখ্য। মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কাউন্সিল, স্বাস্থ্য দফতর এবং অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি করা নানা কমিটির মাধ্যমে বিগত কিছু বছর ধরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি। পুলিশ-সহ সরকারি প্রশাসনও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই দুর্নীতির রক্ষণাবেক্ষণে জড়িত বলে অভিযোগ। সুতরাং, এই ঘটনার জন্য দায়ী দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাই। ব্যাপকভাবে মহিলারা পথে নেমেছেন। সামগ্রিকভাবে মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব, লিঙ্গবৈষম্য দূর করার প্রশ্নও জোরদারভাবে উঠে এসেছে এই আন্দোলনে - যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনুবাদের ভক্তদের কাছে এই দাবি অস্বস্তিকর। শুধু নিরাপত্তারক্ষী বা সিসি ক্যামেরার সংখ্যা বাড়িয়েই হবে না, একথা সরাসরি বলতে পেরেছে এই আন্দোলন - দরকার এই বাস্তুঘুঘুদের বহিষ্কার এবং শাস্তি। সেই অর্থে, এই আন্দোলন একটা উত্তরণের দিশা দেখাচ্ছে, যা নজর করার এবং আশা রাখার মতো একটি বিষয়।
দরকার এই স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিবর্তনের ভাবনা। বিষয়টা অবশ্যই অরাজনৈতিক হতে পারে না। ডাক্তাররা বারবার এই আন্দোলনকে অরাজনৈতিক রাখার কথা বলছেন - উদ্দেশ্য হয়ত এটাকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা। তাই নিয়ে ছোটখাট বিতর্কও নজরে আসছে। সাম্প্রতিককালের রাজনীতির কদর্য চেহারা দেখে অভ্যস্ত সাধারণ মানুষের কাছেও 'অরাজনৈতিক' অভিধা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।
এই আন্দোলনের পিছনে আসল শক্তি যোগাচ্ছে এক বড়ো নাগরিক সমাজ। নচেৎ, শুধু ডাক্তারদের আন্দোলন হিসাবে এর পক্ষে এতটা জোরদার হয়ে ওঠা শক্ত হতো। বর্তমান শাসকদল রাজনৈতিক, প্রশাসনিক সব শক্তি ব্যবহার করছে আন্দোলনকে শেষ করতে, অন্যায় চাপা দিতে। সুতরাং এর রাজনৈতিক চেহারাটা লুকোনো নেই। ডাক্তারদের দাবিগুলি নিয়ে টালবাহানা থেকে দিনে দিনে পরিষ্কার হচ্ছে, এই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির প্রতিষ্ঠাতা এবং পৃষ্ঠপোষক যে সরকার, তাদের না সরিয়ে সম্ভবত বিশেষ কোনো লক্ষ্যপূরণ সম্ভব নয়। মূলস্রোতের নাগরিক সমাজের এই আন্দোলনের পাশাপাশি উপস্থিত গঠনমূলক রাজনৈতিক আন্দোলনও নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। নাগরিক সমাজের আন্দোলনে নির্দ্বিধায় যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন মত ও পথের পতাকা ছাড়া রাজনৈতিক মানুষেরা। এই আন্দোলনে বামপন্থী মতাদর্শ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শিক্ষক, ছাত্র, যুব, মহিলারা। সংগঠিত বামপন্থী শ্রমিক কৃষক ক্ষেতমজুরদেরও দেখা গেছে পথে। এই দুটি ধারা যতক্ষণ একে অন্যের পরিপূরক থাকবে, ততক্ষণই আন্দোলন জোরের সঙ্গে টিকে থাকতে সক্ষম হবে। আন্দোলন অবশ্যই রাজনৈতিক, তবে দলীয় রাজনীতির নয় - সমগ্র নাগরিক সমাজের। সাধারণ মানুষের এই ‘নাগরিক’ হয়ে ওঠা একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। প্রশ্ন করতে শেখা, সচেতন ‘নাগরিক’ই পারে বর্তমান বা ভবিষ্যতের যে কোনো সরকারের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।
বৃহত্তর প্রেক্ষিত - নয়া উদারবাদী অর্থনীতি
আলোচনাকে আরও গভীরে নিয়ে যেতে গেলে, নজর দেওয়া দরকার নব্য উদারবাদী অর্থনীতির প্রভাবের দিকে। দুর্নীতির ব্যাপার নিয়ে দরকার পরিষ্কার বোঝাপড়া। এটা আর শুধু ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত লাভ বা স্বার্থসিদ্ধির সংজ্ঞায় আটকে থাকে না। আমাদের তাকাতে হবে রাজনীতির অধ্যাপক স্টিফেন মরিস-প্রদত্ত সংজ্ঞায় - "রাজনৈতিক দুর্নীতি হল ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহার"। বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল কাউফম্যান দুর্নীতির ধারণাটা প্রসারিত করেছেন ‘আইনি দুর্নীতি’কেও অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে আইনের সীমার মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয় - কারণ ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা প্রায়শই তাঁদের সুরক্ষার জন্য আইন তৈরি করার ক্ষমতা এবং, একইসঙ্গে প্রয়োজনে সেই আইনকে পাশ কাটানোর ক্ষমতা রাখেন। এই নব্য উদার অর্থনীতির যুগে দুর্নীতির পরিসরটা আর ব্যক্তি মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে নেই। জনগণ-প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজির স্বার্থরক্ষা একটা বড়ো দুর্নীতি। শেষ বিচারে, আমাদের তাকাতেই হবে সেই ব্যবস্থা বদলানোর অভিমুখে। সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে, দেশের অর্থনীতিতে এই নব্য উদারনীতির প্রভাবের বিষয়েও আলোচনা করা দরকার।
মোটামুটি, ১৯৮০র দশকের মধ্যভাগ থেকে এদেশে নয়া উদারবাদী সংস্কারের ছোঁয়া দেখা গেলেও, সরকারি ঘোষণায় অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তনের কথাটা এল ১৯৯১ সালে নরসিমা রাও এবং মনমোহন সিং-এর হাত ধরে। নয়া উদারবাদী অর্থনীতির একটা স্তম্ভ হল বেসরকারিকরণ। অর্থনীতির রাশ থাকবে বেসরকারি উদ্যোগপতিদের হাতে - সরকার হবে সহযোগী। দ্বিতীয় স্তম্ভ বাজার অর্থনীতি - আইনি নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে অর্থনীতিকে ছেড়ে দিতে হবে বাজার ব্যবস্থার অধীনে। তৃতীয় স্তম্ভটা হল, আন্তর্জাতিক পুঁজি চলাচলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আরোপিত বাধাগুলোর অপসারণ। অবশ্য, ১৯৯১ থেকে তিরিশ বছরের বেশি সময় ধরে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি থাকা সত্ত্বেও, আমাদের দেশ কখনই খুব দ্রুত সংস্কারের পথে হাঁটেনি। সংস্কার এগিয়েছে মন্থর গতিতে, কখনও তার গতি রুদ্ধ হয়েছে, এমনকি রাষ্ট্রের ভূমিকা কমিয়ে আনার বদলে কখনও তা বেড়েছে।
দেশের স্বাস্থ্যনীতি এই অর্থনীতিরই ফসল। চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রাইভেট সেট-আপ তার আগেই ছিল, ক্রমে দেশীয় পুঁজিরও প্রবেশ ঘটেছিল স্বাস্থ্য পরিষেবায়। তবে নব্বুইয়ের দশকে বৃহৎ পুঁজির প্রবেশ দেশের চিকিৎসার চালচিত্রে বড়সড় পরিবর্তন আনল। চিকিৎসা পরিকাঠামোয় অভাবনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার লাগামছাড়া খরচ এবং চিকিৎসকদের সামাজিক অবস্থানের অবনতি দেখা গেল। বস্তুত, নয়া উদারবাদী নীতি এদেশের সংসদে পেশ করার সময়েই বলা হয়েছিল, এই নীতিগুলোর কোনো বিকল্প নেই; মনমোহন সিং-এর ভাষায় - There Is No Alternative (TINA)। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল হিসাবে কেউ নয়া উদারবাদ পছন্দ না করলেও, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবর্গীয় মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে না-দাঁড়াতে চাইলেও, এছাড়া নাকি কোনও বিকল্প নেই!
যাদের সুবিধা পাওয়ার তারা উদ্বাহু হলেন। একটা বড়ো অংশের মানুষ কিছুই বুঝলেন না, বোঝার জন্য সময় দেওয়ার ফুরসৎ তাদের ছিল না। আরেকটা অংশের মানুষ এই ‘সিস্টেম’কে পুরোপুরি সমর্থন না করলেও, এমনকি ‘সিস্টেম’টা মূলগতভাবে অন্যায় বলে বিশ্বাস করলেও, একে মেনে নিতে শুরু করেছেন। নিজের গায়ে আঁচ আসা অবধি সবই মেনে নেওয়ার এই অভ্যাস, আর, এই প্রতিটা মেনে নেওয়া, প্রতিটা প্রতিবাদহীন সম্মতি ‘সিস্টেম’কে মজবুত করেছে অবিরত।
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল এবং নতুন জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১৭
দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেশ নড়বড়ে ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে। স্বাস্থ্যসূচকে, বিশ্বগুরু হতে চাওয়া, ভারতের স্থান ১৯৫টি দেশের মধ্যে ৬৬ নম্বরে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কযুক্ত বিশ্ব ক্ষুধা সুচকে ১২৭টি দেশের মধ্যে আমাদের স্থান ১০৫ নম্বরে। দেশের এই নড়বড়ে স্বাস্থ্যের হালের উৎস সন্ধান করেছেন অমর্ত্য সেন তিনটে মূল ব্যর্থতার মধ্যে।
১) প্রাথমিক স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে চূড়ান্ত অবহেলা।
২) বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপরে অত্যধিক নির্ভরতা এবং সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে ক্রমাগত লাটে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা।
৩) স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন আলোচনার অভাব এবং স্বাস্থ্যকে এজেন্ডা হিসাবে তুলে আনায় অনীহা।
১৯৭৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) স্বাস্থ্যকে সংজ্ঞায়িত করেছিল, "অসুখ বা অসুস্থতাহীন থাকাটাই শুধু নয়, সুস্থ থাকার অর্থ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে ভালো থাকা"। মেনে নেওয়া হয়েছিল, সকলের জন্য স্বাস্থ্যের দাবি। মোটামুটি এর ভিত্তিতে ১৯৮৩ সালে তৈরি হয়েছিল দেশের প্রথম স্বাস্থ্যনীতি।
এরপর বিশ্বব্যাঙ্ক আর আইএমএফ আনল তাদের আর্থিক সংস্কারের নীতি, শুরু হল গণহারে বেসরকারিকরণ, ‘সবার জন্য স্বাস্থ্য’ এই নীতির সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। ২০০২ সালে এল দ্বিতীয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি - এই নীতির দিকনির্দেশ এল মুকেশ আম্বানি এবং কুমারমঙ্গলম বিড়লার নেতৃত্বে। সকলের জন্য স্বাস্থ্যের বিষয় পিছু হটতে শুরু করল। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারি লগ্নিবিষয়ে ঢালাও উৎসাহপ্রদান, উন্নত চিকিৎসাক্ষেত্রে বেসরকারি বিমাসংস্থার আবশ্যিকতা - বেসরকারি লগ্নির মুনাফার কথা মাথায় রেখে স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের সেই শুরু। সেই প্রথম সরকার স্বীকার করে নিল, স্বাস্থ্য মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্র, স্বাস্থ্যচিকিৎসাকে ব্যবসা হিসাবে দেখা যেতে পারে।
২০১৭-য় এল নতুন জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি। সরকার, স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার করার দায় থেকে সরে গেল - ‘স্বাস্থ্য’ নেমে এল ‘স্বাস্থ্যের আশ্বাসে’ (Health Assurance)। স্বাস্থ্যনীতিতে বলা হয়েছে, দেশে একটি কার্যকরী, দক্ষ, নিরাপদ, সকলের সাধ্যায়ত্ত, নীতিনিষ্ঠ, যুক্তিনির্ভর চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে বেসরকারি সহযোগিতায়। অথচ, বেসরকারি উদ্যোগের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য মানুষের অসুস্থতাজনিত অসহায়তা কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জন। তাদের সহযোগিতায় গড়ে উঠবে নীতিনিষ্ঠ ও সকলের সাধ্যায়ত্ত চিকিৎসাব্যবস্থা! সরকার বলেছিলেন, স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ তারা একেবারে আড়াইগুণ করে দেবেন, জিডিপির ১.১৫ শতাংশ থেকে ২.৫ শতাংশ, ২০২৫ সালের মধ্যে। ২০২৪ এসে তার থেকে বেশ দূরে আমরা, যদিও এই বরাদ্দও বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা ৫ শতাংশ থেকে বহু দূরে। এই বাড়তি অর্থের সংস্থান অবশ্য কোথা থেকে হবে, বোঝা যায়নি।
২০১৯ সালে এল জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন বিল। চিকিৎসকদের দ্বারা নির্বাচিত মেডিক্যাল কাউন্সিলের স্থানে এল কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত সদস্যদের মেডিক্যাল কমিশন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রের হর্তাকর্তাবিধাতা। এর মাধ্যমে মেডিক্যাল শিক্ষায় বেসরকারিকরণ এবং বেসরকারি মালিকদের যথেচ্ছ ফিজ নির্ধারণের স্বাধীনতা দেওয়া হল। স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীকরণ ঘটানো হল।
স্বাস্থ্যনীতিতে, সরকার মাথায় রেখেছেন বেসরকারি লগ্নির স্বার্থ; জানিয়েছেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যটুকুই, তাও শুধুমাত্র গরীব মানুষের জন্য, সরকার সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে রাখবেন। জনস্বাস্থ্য বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যে বিনিয়োগে বিশেষ বাণিজ্যিক লাভ নেই; ফলে এখানে বিনিয়োগের দায় সরকারের। চিকিৎসায় বাণিজ্যিক লাভ আসে রোগের চিকিৎসা থেকেই। আবার, সরকার জনস্বাস্থ্যে সত্যিকারের নজর দিলে রোগের প্রকোপ কমে। তাতেও কর্পোরেট হাসপাতালের জন্য চাহিদা কমে। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে চিকিৎসা পাওয়া গেলে মানুষ কর্পোরেট হাসপাতালে দৌড়ে যাবে না। তাই, জনস্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যে অবহেলা, ডাক্তার ও পরিকাঠামোগত অভাব এবং সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনীহা দেখিয়ে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে অপটু করে রাখা একটা সচেতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।
একদিকে বিশ্বমানের হাইটেক হেলথকেয়ারের বিজ্ঞাপন - আর একদিকে সমস্ত স্বাস্থ্যসূচকে দেশের অধোগমন। এই শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার রাজনীতিকে লোকচক্ষুর আড়াল করতে দরকার সাধারণ মানুষকে অসচেতন করে রাখা। তাই, অহরহ বোঝানো হয়েছে, TINA! সরকার, আবার, বেসরকারি পরিকাঠামো থেকে প্রয়োজন অনুসারে পরিষেবা কিনবে। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের একটা বড়ো অংশ পৌঁছবে বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের হাতে। সরকার গরীব মানুষের চিকিৎসার খরচ নিজেরা বহন না-করে ছেড়ে দিচ্ছে বিমা কোম্পানির হাতে - সেখানেও বেসরকারি বিমা কোম্পানিদেরই রমরমা।
স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বাজারের অনিবার্য নিয়ম মেনে নিয়ে প্রতিযোগিতার হাতে ছেড়ে দিলে, নিয়ম বা নজরদারি দিয়েও পরিস্থিতির বদল হতে পারে না। দুর্নীতির শিকড় লুকিয়ে এখানেই। স্বাস্থ্য-চিকিৎসাকে পণ্য বানিয়ে, চিকিৎসার মতো একটা অত্যাবশ্যক বিষয়কে মুনাফা-অর্জনের প্রতিযোগিতার হাতে ঠেলে দেওয়ার ধান্দার মধ্যেই দুর্নীতির বীজটা লুকিয়ে। চিকিৎসাকে ক্রেতাসুরক্ষা বিধির আওতায় এনে চিকিৎসা পয়সা দিয়ে কেনার ‘সিস্টেম’ চালু হল। চিকিৎসা যে ক্রয়যোগ্য পণ্য হতেই পারে না, এমন কথা জোরগলায় বলার লোক কোথায়?
ওষুধ কোম্পানিগুলো পণ্য বিক্রির জন্য প্রাণপণ বিপণন করছে, ল্যাব বা ডায়গনস্টিক সেন্টারগুলো পরীক্ষার খদ্দের খুঁজছে, কর্পোরেট হাসপাতালগুলো রোগী আকর্ষণের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্যাকেজের ব্যবস্থা করছে বা ডাক্তারবাবুদের দিয়ে রেফার করানোর জন্য বিভিন্ন উপঢৌকনের ব্যবস্থা রাখছে, ওষুধ কোম্পানির বার্ষিক বাজেটের একটা বিরাট অংশ মার্কেটিং-এর জন্য বরাদ্দ হচ্ছে, বেসরকারি হাসপাতাল মোটা মাইনে দিয়ে মার্কেটিং টিম পুষছে আর সেই টিম হাসপাতালের নীতি নির্ধারণ করছে। বিজ্ঞাপন ঢেকে দিচ্ছে আমাদের চিন্তাভাবনার ক্ষমতা।
এই ব্যবস্থা বজায় রেখে দুর্নীতির মোকাবিলা সম্ভব? এই নগ্ন শোষণ ব্যবস্থায়, কর্পোরেট মালিক মুনাফা আদায় করে, কিন্তু, সামনে মুখ থাকে ডাক্তারের, রোগীদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের ঠেলা সামলাতে হয় তাঁকেই - শোষক বনাম শোষিতের এই বাইনারিতে তাঁর অবস্থান ঠিক কোথায়, ভাবতে হবে ডাক্তারবাবুদেরও।
আমাদের চোখের সামনেই, নীতিনির্ধারকেরা ‘স্বাস্থ্য’কে বদলে দিয়েছিলেন ‘স্বাস্থ্য পরিষেবায়’। আমরা নীরব থেকেছি, সবকিছু মেনে নিয়েছি। স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করতে বসলেই, হয়, ডাক্তারদের আদ্যশ্রাদ্ধ বা বিক্ষিপ্ত কিছু তাকলাগানো কর্মকাণ্ড, এসবেই মগ্ন হয়ে যাই আমরা। কিন্তু, একটা দেশের স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে তেমন আলোচনা কই!
উদার অর্থনীতির বড়ো প্রবক্তা খোদ আমেরিকায় বিল ক্লিন্টন বলতে বাধ্য হয়েছেন, "প্রতিযোগিতার ওপর নির্ভর করে ভালো ভালো নীতি প্রণয়ন করা গেলেও, সারা পৃথিবীজুড়ে থাকা সমস্যা - যেমন জলবায়ুর বদল, বিভিন্ন অসুখবিসুখ - এসবের সমাধানের জন্য প্রতিযোগিতার চাইতে অনেক বেশি জরুরি হল সহযোগিতা, হাতে হাত ধরে চলার মানসিকতা। বিশেষকরে গরিব, প্রান্তিক মানুষজনের সমস্যাগুলো মেটাতে হলে এই কথাটা আরও বেশি প্রযোজ্য। মুশকিল হল, তুলনামূলকভাবে, সমস্যাগুলো গরিব বা প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে অনেক বেশি"।
এটা পরিষ্কার, নয়া স্বাস্থ্যনীতির পথ সার্বিক উন্নতির নয়, উন্নয়নের আশা দেখানোর। রাষ্ট্র যতদিন না সব নাগরিকের সামর্থ্যের মধ্যে একটা স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করছে, ততদিন সুরাহা মিলবে না। বাধ্য করতে হবে, রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের ইস্তেহারে স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে স্থান দিতে। প্রশ্ন করতেই হবে, জাতীয় স্বাস্থ্যের মতো জরুরী বিষয়টা নজরের বাইরে রাখা হচ্ছে কেন? সত্যসত্যই ‘নাগরিক’ হয়ে উঠতে গেলে এই জরুরী প্রশ্নগুলো ভোলা যাবে না!
কৃতজ্ঞতাঃ ডা. বিষাণ বসু, কিনে আনা স্বাস্থ্য - বাজার-পুঁজি-মুনাফা আর আপনি।