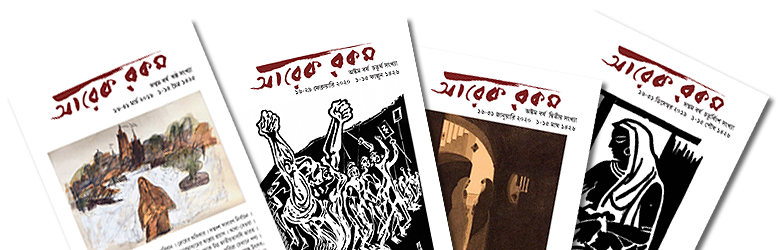আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ ষোড়শ সংখ্যা ● ১৬-৩১ আগস্ট, ২০২৪ ● ১-১৫ ভাদ্র, ১৪৩১
প্রবন্ধ
ধর্মের অনুসন্ধানে
মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়
ধর্ম কাকে বলে? অক্সফোর্ড অভিধান অনুযায়ী -
Recognition on the part of man of some higher unseen power as having control of his destiny, and as being entitled to obedience, reverence and worship; the general mental and moral attitude resulting from this belief, with reference to its effect upon the individual or the community; personal or general acceptance of this feeling as a standard of spiritual and practical life. (Oxford English Dictionary 1989)
কিছু উচ্চতর অদৃশ্য শক্তির স্বীকৃতি তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। (সেই শক্তির) প্রতি আনুগত্য, শ্রদ্ধা এবং উপাসনার অধিকার হিসাবে এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত মানসিক এবং নৈতিক মনোভাব, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের ওপর এর প্রভাব - আধ্যাত্মিক এবং ব্যবহারিক জীবনের একটি মানদণ্ড হিসাবে ব্যক্তিগত বা সাধারণের গ্রহণযোগ্যতা থাকা (কে ধর্ম বলা যায়)। (অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান ১৯৮৯)। [অনুবাদ বর্তমান লেখকের]
লক্ষ্য করুন শব্দ ক'টি - কিছু 'উচ্চতর অদৃশ্য শক্তি' বা অন্যভাবে বলা যায় কোনো উচ্চতর অবস্থানে লুকিয়ে থাকা পরাজাগতিক শক্তি।
'খই-সান'-রা হলো দক্ষিণ আফ্রিকার দুটি জনগোষ্ঠী, এরা অনেক সময়ে একসঙ্গে থেকে শিকার করে। জিনোমিক বিশ্লেষণ থেকে মনে হয় 'খই-সান'-রা এই পৃথিবীর প্রথম 'হোমো সেপিয়েন্স (Homo sapiens) জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি যা এখনও টিকে আছে।[1] আজকে মাত্র ১ লক্ষ সান জনগোষ্ঠীর মানুষ বেঁচে আছেন, যারা ঐতিহ্যগতভাবে শিকারি এবং সংগ্রাহক। যদিও বর্তমান সময়ের 'সান' শিকারি-সংগ্রাহকরা সেই আদি সমাজের পূর্বপুরুষের সরাসরি, অবিচ্ছিন্ন বংশধর নাও হতে পারে; তবে একথা বলা যেতে পারে, এই শিকারি-সংগ্রাহকরা অবশ্যই প্রস্তর যুগের ক্রিয়াকর্মের যে বৈশিষ্ট্যগুলো গোষ্ঠীর মধ্যে নির্বাচিত হয়েছিল তাকে জানবার একফালি জানালা। প্রাথমিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য সহ তা আজও 'খই-সান' গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রবাহিত।
আজকের পৃথিবীর কিছু ভাষা কি এখনও প্রথমদিকের হোমো সেপিয়েন্স কথিত প্রাচীন মাতৃভাষার মতো টিক টিক করে ধ্বনি তোলে? ভাষা খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়। তাই প্রাচীনতম ভাষার স্বরূপ খুঁজে বেড়ানো সহজ কাজ নয়। কিন্তু নতুন জিনগত অধ্যয়ন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ভাষার আদি প্রাচীনত্বকে মনে করিয়ে দেয় - এই সম্ভাবনাকে উস্কে দেয় যে, তাদের ভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পূর্বপুরুষের প্রাথমিক মাতৃভাষার অংশ ছিল। এ হলো দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লিক ধ্বনিভাষা। 'সান'-দের ভাষার প্রাচীনতা ও বৈচিত্র তাদের গভীর জিনোমিক বৈচিত্রর মতোই বিস্ময়কর।[2]
১৭শ সাধারণাব্দে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকরা ওই অঞ্চলে গিয়ে 'খই-সান'-দের মধ্যে কোনো 'বিশ্বাস ব্যবস্থা' খুঁজে পাননি, কোনো আধ্যাত্মিকতার হদিস পাননি।[3] কারণ তাঁরা খুঁজেছিলেন 'নৈতিক সর্বোচ্চ-সত্তা ঈশ্বর'কে (High God)। চাঁদের আলোতে সন্মোহন নাচ তাঁদের আত্মাদের জগতের সন্ধান দেয়নি। তাঁরা বলেছিলেন 'খই-সান'-দের কোনো ধর্ম নেই, কোনো 'বিশ্বাস ব্যবস্থা' নেই। ধর্ম ধারণা বুঝতে শুধু আজকের বৃহৎ মনোলিথিক 'বিশ্ব ধর্ম'গুলোতে মনোযোগ দিলে বোঝা যাবে না তার উৎস কোথায়, 'বিশ্বাস ব্যবস্থা' কত পুরোনো। ধর্মেরও বিবর্তন হয়েছে। আদি, অপরিস্ফূট প্রাথমিক প্রোটো-ধর্মের থেকে, বুঝতে হবে যে, আজকের 'বিশ্ব ধর্ম'গুলোর সূত্রপাত হয়েছে।
ধর্ম বিভিন্ন ধরনের হয়। তাদের আকার, শৈলী, রীতি, গঠনে প্রচুর পার্থক্য আছে। শিকারি-সংগ্রাহকদের 'প্রাকৃতিক' ধর্মের স্বাতন্ত্র, মধ্যপ্রস্তর যুগের পূর্বপুরুষদের 'বিশ্বাস ব্যবস্থা'-র সঙ্গে আজকের আধুনিক 'বিশ্ব ধর্ম'গুলোর তুলনা করতে গেলে আগে খেয়াল রাখতে হবে, এইসব 'বিশ্ব ধর্ম'গুলো প্রথম এসেছে খুব বেশি হলে নব্যপ্রস্তর যুগের শেষের দিকে - কৃষি ও পশুপালন উৎপাদন ব্যবস্থা বেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরে। প্রাথমিক আব্রাহামিক ধর্মমতগুলো এসেছে আরও অনেক পরে - ধাতুর যুগে।
যদিও শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ আদিম ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে, তবে এই ধরনের সমাজে আধুনিক ধর্মের ধারণা বিশেষ নেই। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থাকে তাদের ক্রিয়াকলাপ। শিকারি-সংগ্রাহকদের প্রতিটি সমাজ তার অনন্য বিশ্বাস-ব্যবস্থা বজায় রাখে এবং শিল্প, সংস্কৃতি, স্ব-মূল্যবোধ, সাধারণ স্বাস্থ্য ও দলের মঙ্গলের জন্য ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যায়। এই সমস্ত আচার ও বিশ্বাস-ব্যবস্থাকে একসঙ্গে বলা যায় আদি ধর্ম।
এক সক্রিয় বা 'নৈতিক সর্বোচ্চ সত্তা ঈশ্বর' সাধারণত উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্তভাবে আসে। প্রযুক্তিগত জটিলতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে 'সর্বোচ্চ সত্তা ঈশ্বর'কে আরাধনার সম্ভাবনা থাকে বেশি। তাই শিকারি-সংগ্রাহক সমাজে এই ব্যবস্থা থাকবার সম্ভাবনা কম, আবার কৃষিব্যবস্থায় 'সর্বোচ্চ সত্তা ঈশ্বর' বা একেশ্বরবাদের থাকার সম্ভাবনা বেশি। উৎপাদন ব্যবস্থার জটিলতর পরিবর্তনের সঙ্গে ধর্মের চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে।
আব্রাহামিক ধর্মমতগুলো মোটের ওপরে নৈতিক 'সর্বোচ্চ সত্তা ঈশ্বর' বিশ্বাসের দ্বারা লালিত হয়েছিল। সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে সহযোগী সমাজ তৈরি করতে এই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এক অতিপ্রাকৃত ধর্মীয় ধারণা ব্যবহার করেছিলেন। ফলে সমাজের সম্পদ বন্টন মসৃণ হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। নৈতিক কানুনের অতিপ্রাকৃত প্রয়োগ সামাজিক শান্তি বজায় রাখে, সংহতি তৈরি করে এবং আরও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও তা ধর্মের অনুমোদন পায়। এই সামাজিক সুবিধা অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সহায়ক শক্তি হয়ে যায়।[4] তাই ধর্ম নিয়ে গবেষণামূলক চর্চা দেখায়, ধর্মের বিবর্তনের মধ্যে পরবর্তীকালে এক 'নৈতিক সর্বোচ্চ সত্তা ঈশ্বর'-এ বিশ্বাসের ওপর দৃষ্টি রাখা হয়েছে, যাকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা মানবিক বিষয়ে সক্রিয় এবং মানুষের সহায়ক হতে পারেন। 'নৈতিক সর্বোচ্চ সত্তা ঈশ্বর'-এর বিবর্তন হয়েছে খরা, বন্যা, অনাবৃষ্টি, মড়ক, শক্তিনাশ ইত্যাদির প্রতিক্রিয়াতে।
উন্মেষের সময়ের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তালমিল রেখেই অনেক ধর্মে 'নৈতিক সর্বোচ্চ সত্তা ঈশ্বর' অনুপস্থিত থাকেন, আবার কোথাও তারা উপস্থিত থাকলেও মানবিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না, কোথাও বা করেন। সোয়ানসন[5] 'নৈতিক সর্বোচ্চ সত্তা ঈশ্বর'কে সংজ্ঞায়িত করেছেন,
"একটা আত্মা যিনি বাস্তব জগত সৃষ্টি করেছেন, এর মধ্যে আছে সমস্ত আত্মা - যার একমাত্র কাজ ছিল অন্যান্য আত্মাদের তৈরি করা, যারা প্রাকৃতিক বিশ্ব সৃষ্টি করেছে। অবশ্য পরম ও সর্বোচ্চ ঈশ্বর ছাড়াও অন্যান্য দেবতা থাকতে পারে।" [ভাবানুবাদ বর্তমান লেখকের]
খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় পার্থক্য শুধু 'বিশ্ব ধর্ম'গুলোর সঙ্গে শিকারি-সংগ্রাহক সমাজের প্রাথমিক ধর্মের মূল্যবোধে আছে এমনটা কিন্তু নয় - আজকের পৃথিবীর প্রধান ধর্মমতগুলোর মধ্যেও বহু মূলগত পার্থক্য রয়ে গেছে। আজকের বিশ্ব ধর্মগুলোর মধ্যে আছে তিনটি আব্রাহামিক ধর্ম - খ্রিস্ট, ইসলাম ও ইহুদি। আর আছে ভারতবর্ষীয় দুই মূল ধর্ম - হিন্দু ও বৌদ্ধ।
ইহুদি ধর্মে স্বতন্ত্র প্রার্থনা এবং একত্রিত প্রার্থনার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে; একত্রিত প্রার্থনা 'মিনিয়ান' নামে পরিচিত। এই প্রার্থনা অগ্রাধিকারযোগ্য কারণ 'তোরাহ্' ধর্মগ্রন্থের কিছু স্তব এই প্রার্থনাতে আছে, একাকী প্রার্থনাতে তা বাদ দেওয়া হয়। এই ধর্মমতের আধুনিক প্রার্থনার মূল কাঠামো প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থির করা হয়েছিল - অবশ্য কিছু সংযোজন পরবর্তীকালেও হয়েছে।
"যখন আমরা একসঙ্গে প্রার্থনা করি, আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করি" - বাইবেল-এর ম্যাথু ১৮:২০ স্তবে বলা হয়েছে। "কারণ যেখানে দুই বা তিনজন আমার অনুসারী হিসেবে একত্রিত হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি। খ্রিস্ট এবং তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাসের কারণে, আমরা এখন সাহসের সঙ্গে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে অনুভব করতে পারি।" [অনুবাদ লেখকের]
খ্রিস্টানদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময়ে ধর্মস্থানে একত্রিত প্রার্থনা করা হয়, যেমন প্রতি রবিবারে, বড়দিনের পর্বে বা লেন্ট-এর অনুষ্ঠানে। ধর্মমতগুলোর মিথস্ক্রিয়া, পরবর্তী আরোপিত বিশ্বাস ইত্যাদির ফলে এক বিবর্তনীয় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েও ধর্মের আচারের পরিবর্তন হয়।
সালাত আল-জামাআহ্ (সামাজিক প্রার্থনা) বা জামাতে প্রার্থনা (জামাআহ্) নিজের একান্তে প্রার্থনা করার চেয়ে সামাজিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে বেশি লাভদায়ক বলে মনে করা হয়। জামাতে নামাজ পড়ার সময়, মুসলিমরা কিবলার দিকে মুখ করে নির্বাচিত ইমামের পিছনে সোজা সমান্তরাল সারিতে দাঁড়ায়। সকলে একত্রিতভাবে শরীর দিয়ে প্রার্থনা করেন। দিনে পাঁচবার এই প্রার্থনার রেওয়াজ ধর্মীয় আচারে বিশ্বাসী মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত।
হিন্দু ধর্মের আচারের সঙ্গে আব্রাহামিক ধর্মমতগুলোর আচারের যোজন দূরত্ব। হিন্দু ধর্মের প্রাথমিক সূচনা হয়েছে এই ধর্মমতগুলোর অনেক আগে। এই ধর্ম দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সর্বপ্রাণবাদ, লোকাচার ও স্থানীয় বিশ্বাস, হরপ্পীয় ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষের রীতিনীতি আয়ত্ব করেছে, বিবর্তিত হয়েছে। তাতে যুক্ত হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয়দের বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও পরবর্তীকালে উপনিষদের দর্শন। হিন্দু ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মে ভক্ত একাকী নিজ বিশ্বাসের জন্য বা মনের শান্তির জন্য ধর্মাচরণ বা প্রার্থনা করেন। আচার অনুষ্ঠান মূলত পারিবারিকভাবে পালিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য গ্রামের মানুষের উপস্থিতিও কাম্য ছিল। তবে তা অনেক সময়েই ছিল অনুগৃহীত ও অনুগ্রহকারীর সম্পর্ক। প্রাচীন ভারতে রাজারা তাঁদের সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বকরণের জন্য বৈদিক যজ্ঞের আয়োজন করতেন। সাম্রাজ্যের প্রসার, ক্ষমতা ও গৌরব অর্জন, প্রতিবেশী সাম্রাজ্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা হলো রাজসূয় যজ্ঞের উদ্দেশ্য। রাজসূয় রাজার পবিত্রকরণের সঙ্গে যুক্ত। গ্রামের পুজোয় জমিদার বাড়িতে দরিদ্র চাষী আসতেন পুজো দেখতে, প্রসাদ খেতে। সেখানে দলিতের প্রবেশাধিকার ছিল না। অপরদিকে ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মে একত্রিত সর্বজনীন প্রার্থনা বেশি প্রচলিত। সেখানে তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রকাশ, দলের মধ্যে সংহতি মুখ্য। তবে এই দুই 'বিশ্বাস ব্যবস্থা'য় কিন্তু সমাপতিত অংশ আছে। ধর্মভীরু খ্রিস্টান বা মুসলমান একাকীও তার বিশ্বাসের সৃষ্টিকর্তাকে আরাধনা করতে পারেন ও করেন। হিন্দুও পুজো প্যান্ডেলে সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে একত্রিতভাবে পুজো দেন - অবশ্য এই বারো-ইয়ারি পুজোর প্রথা একেবারেই সাম্প্রতিক সময়ে শুরু হয়েছে, প্রাচীন ধর্মের মধ্যে আধুনিক আরোপ। বৌদ্ধ ধর্মে সকল শ্রেণীর মানুষ গোম্ফা বা মঠে গিয়ে পুজো দিতে পারেন। তবে সেই পুজোয় বিশেষ দিন বাদে একাকী আরাধনাও গুরুত্ব পায়।
অবশ্য অধিকাংশ ধর্মমতেই (প্রাথমিক ধর্ম এবং আজকের বিশ্ব ধর্মমতগুলো) মোটের ওপরে অতিমানবীয়/অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস থাকে। অতীন্দ্রিয় শক্তিকে সন্তুষ্ট করতে কেউ করেন উপাসনা, কেউ বলি দেন পশু, কেউ করেন যজ্ঞ। আবার কেউ বা সন্মোহন নাচেন। কেউ সর্বপ্রাণবাদী (অ্যানিমিজম), কেউ বহু দেবতায় বিশ্বাসী, কেউবা একেশ্বরে বিশ্বাস করেন। আবার বৌদ্ধ ধর্মমত সেই অর্থে কোনো পরম ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়।
ধর্ম কোনো আধুনিক ধারণা নয়। লিখিত ইতিহাসের বহু আগে থেকে মানুষের মধ্যে 'বিশ্বাস ব্যবস্থা' থেকেছে। সে অতীন্দ্রিয় জগতে বিশ্বাস করেছে। এই অতীন্দ্রিয় জগতে থাকে আত্মা, অথবা থাকে কিছু শক্তি। আত্মাদের সঙ্গে মরজগতের যোগ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। কবে থেকে সে অতীন্দ্রিয় জগতে বিশ্বাস করে? যবে থেকে সে স্বজনকে কবর দিচ্ছে নিদেনপক্ষে গুহার একধারে চাপা দিয়ে রাখছে; আর তার সঙ্গে দিচ্ছে কিছু ভোগ্যবস্তু, অন্ততপক্ষে তবে থেকে। পরকালে সেই ভোগ্যবস্তু কাজে লাগবে। তাই প্রাচীন, অতি প্রাচীন, মধ্যপ্রস্তর যুগের, কবরে পাওয়া যায় লাল গিরিমাটি, পুঁতি, ঝিনুক, পাথরের অস্ত্র, পশুর হাড়। এই কবরসামগ্রীর উপস্থিতি মৃত ব্যক্তির সঙ্গে বস্তুগুলোর একটা মানসিক সংযোগ এবং সম্ভবত পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসের ইঙ্গিত দেয়। খেয়াল রাখতে হবে, প্রাথমিক ধর্মের ওপরে কোনো দার্শনিক তত্ত্বের আবরণ নেই। শিকারি-সংগ্রাহকদের বিশ্বাস ব্যবস্থাকে প্রাথমিক ধর্ম বলা যায়।
অনেকে মনে করেন সেই সুদূর অতীতে, সে অন্তত ১.৫ লক্ষ বছর আগে, মানব মন বাস্তবতার বাইরে চিন্তা করতে সক্ষম ছিল এবং প্রতীক, ফ্যান্টাসি ও কল্পনার জগতে সে ঘোরাফেরা করতে পারত।
ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী এবং বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানী রবিন ডানবার মনে করেন, মস্তিষ্কের নিওকর্টেক্স-এর বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি প্রায় ৫ লক্ষ বছর আগে প্রাচীন মানব প্রজাতির মধ্যে ঘটেছিল।[6] তিনি ইঙ্গিত করেন নিওকর্টেক্স যথেষ্ট প্রশস্ত হবার পরেই মানব প্রজাতিগুলো বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম যেমন ভাষা ও ধর্মাচরণ শুরু করতে পারে। নিওকর্টেক্স স্তন্যপায়ী প্রাণীর সংবেদনশীল উপলব্ধি, জ্ঞান, যুক্তিবোধ, দূরত্ব সংক্রান্ত অনুভূতি এবং ভাষার মতো উচ্চতর মস্তিষ্কের কাজের সঙ্গে জড়িত। গবেষণাটি জীবিত এবং বিলুপ্ত হোমিনিনদের[7] বেশ কয়েকটি সামাজিক আচরণ ও নিওকর্টেক্স-এর আকারের অনুপাত থেকে বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।
অবশ্য বাস্তব বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার মতোই ধর্ম এক ঝাপসা, অস্পষ্ট অভ্যাস। বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রে কিছু রীতির মধ্যে মিল থাকলেও এর সংজ্ঞা নিয়ে যুক্তিবিন্যাস করা পরিহার্য। এখন অনেকে এইভাবেই ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করেন যে, একদল মানুষ যে অতীন্দ্রিয় 'বিশ্বাস ব্যবস্থায়' বিশ্বাসী তাকেই বলে ধর্ম। আবার ধর্মের অর্থ এইভাবেও করা যায়, একদল মানুষ অতীন্দ্রিয় 'বিশ্বাস ব্যবস্থা'য় বিশ্বাসী হয়ে যে ক্রিয়াকর্ম একত্রিতভাবে বা একাকী করেন তাকে ধর্ম বলা যায়। অর্থাৎ ধর্ম হল একইসঙ্গে অতীন্দ্রিয় 'বিশ্বাস ব্যবস্থায়' বিশ্বাসী হয়ে কিছু ক্রিয়াকর্ম একত্রিতভাবে বা একাকী সম্পাদন করা।
এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ধর্মীয় ধারণা প্রভাবিত করা যেতে পারে; অবশ্য তা করতে জটিল মানসিক চিত্রের প্রয়োজন এবং প্রতীকী চিন্তাভাবনাও দরকার। প্রয়োজন যোগাযোগের ক্ষমতা যার মধ্যে যৌথ নাচ, গান, নানা ধরনের আচার, অঙ্গভঙ্গি, শিল্প ও অলঙ্করণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এবং অবশ্যই পাশাপাশি থাকা দরকার প্রাথমিক ভাষায় কিছুটা প্রকাশ ক্ষমতা। যাইহোক, সেই প্রাগৈতিহাসিককালের প্রাথমিক ধর্ম থেকে ঐতিহাসিককালে সৃষ্ট আজকের বৃহৎ 'বিশ্ব ধর্ম'গুলোতেও এক অশরীরী, অদৃশ্য শক্তির কল্পনা আছে। এই অদৃশ্য শক্তি অসীম ক্ষমতাশালী ও জীবজগতের ওপরে তার প্রভাব অপরিসীম। আমাদের জীবনকে সেই শক্তি প্রভাবিত করে। এটাই ধর্মগুলোর মোদ্দা কথা।
ধর্ম সম্ভবত বিশেষভাবে 'হোমো সেপিয়েন্স'-এর বৈশিষ্ট্য। বিবর্তনের কোন সময়ে, কী পরিবর্তনের ফলে প্রথমে প্রাথমিক ধর্মের ও পরবর্তীকালে বিশ্ব ধর্মের উদ্ভব হলো? প্রাথমিক ধর্ম থেকে বিশ্ব ধর্ম কীভাবে এল? ভাষার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কী? ধর্ম কি প্রাথমিকভাবে গল্প অনুসারী ছিল? বিশ্ব সংসারে প্রায় সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মের ব্যাপ্তি দেখে মনের মধ্যে এই প্রশ্নগুলো আসে।
আমাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এমন একটা বিশ্বাস ছিল যে মাত্র ৫০ থেকে ৪০ হাজার বছর আগে ইউরোপে 'আধুনিক মানুষ'-এর আমূল বিবর্তনীয় পরিবর্তন হয়েছে; তারা কথা বলেছে, গান করেছে, বাঁশি বাজিয়েছে, ছবি এঁকেছে।[8]
তারপরে আফ্রিকা ও এশিয়াতে বিভিন্ন প্রত্নস্থল ও সেখানে রকমারি শিল্পকর্ম আবিষ্কারের পরে এবং বিবর্তনীয় জীববিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে, আজকে ইউরোপ-কেন্দ্রিক এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এখন জানি আফ্রিকাতে ৭৩ হাজার বছর আগেও হোমো সেপিয়েন্স ঝিনুক দিয়ে মালা তৈরি করত, লাল গিরিমাটি দিয়ে রং তৈরি করত, মাটি খুঁড়ে কন্দ গুহাতে নিয়ে এসে তাকে পুড়িয়ে খেত।[9]
আবার তারও বহু আগে 'আধুনিক মানুষ'-এর এক ব্যর্থ পরিযান হয়েছিল এশিয়াতে, সেখানে ১.২০ লক্ষ বছর আগে, তাদের মৃত স্বজনকে সমাধি দেওয়া হয়েছে, সেই সমাধিও পাওয়া গেছে।[10] সেই সমাধিতে পাওয়া গেছে লাল গিরিমাটি, ফুটো করা ঝিনুক ইত্যাদি।
ধর্মের স্বাভাবিক উত্থানের ব্যাখ্যা নিয়ে শত শত বছর ধরে বিতর্ক চলেছে। তবে এই আলোচনা মূলত কৃষির আগমনের পরের ধর্মগুলো নিয়েই চলে। তুলনায় শিকারি-সংগ্রাহকদের ধর্মবোধ নিয়ে আলোচনা হয় কম। কবর দেওয়া ও সঙ্গে জড়বস্তু রাখা যেমন মৃত্যু পরবর্তী জগতের ভাবনার ইঙ্গিত দেয় তেমনই শরীরে রঙিন লাল গিরিমাটি দিয়ে আঁকাও প্রায়ই এক ধরনের প্রতীকী আচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে চিহ্নিত করা যায়। নিয়মিত লাল গিরিমাটির ব্যবহার হয়েছে ১.৬ লক্ষ বছর আগে থেকে।[11]
এখানে প্রশ্ন আসে প্রাথমিক ধর্মের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য কী ছিল? কীভাবে সেই ধর্ম বৈশিষ্ট্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় এবং পরস্পরের ওপরে ক্রিয়া করে? সম্প্রতি জাতিগত (ফাইলোজেনেটিক) তুলনামূলক পদ্ধতি বস্তুগত ও পরাবস্তুগত বিবর্তন অধ্যয়নের জন্য বেশি করে প্রয়োগ করা হয়েছে।
৩৩টি শিকারি সংগ্রাহক জনগোষ্ঠীর মধ্যে গবেষণা করে দেখা গেছে, সর্বপ্রাণবাদ বা অ্যানিমিজম এসেছে সকলের আগে। এই বিশ্বাস মানুষকে অতীন্দ্রিয় শক্তি বা আত্মাতে বিশ্বাস জাগায়। সর্বপ্রাণবাদ কোনো ধর্ম বা দর্শন নয় - এটি শিকারি-সংগ্রাহকদের মধ্যে চিন্তা করার একটা পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়া সামাজিক বুদ্ধিমত্তাকে আরও সক্ষম করে। এই বিশ্লেষণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রাণবাদ শিকারি-সংগ্রাহক গোষ্ঠীর প্রাথমিক ধর্মমতে সর্বজনীন। অ্যানিমিস্টিক বিশ্বাসের উপস্থিতি 'পরবর্তী জীবন'-এ বিশ্বাসের উদ্ভবের আগে হয়েছে। একবার অ্যানিমিস্টিক চিন্তাধারা একটা সমাজে প্রচলিত হলে আত্মাদের অবস্থান সম্পর্কে আগ্রহ জন্মায়; তার থেকে আসে মৃতদের বসবাসের এক অদেখা রাজ্যের ধারণা। সেই অদেখা রাজ্যে মৃত ব্যক্তিরা বেঁচে থাকে। আসে পরকালে বিশ্বাস।[12]
পরকালের ধারণা ফলপ্রসূ হতে পারে তখনই যখন এই বিশ্বাস জন্মায় যে পৃথিবীতে জীবনের ধারাবাহিকতা মৃত্যুর পরেও প্রবাহিত হয়। তার সঙ্গে আসে আরও কিছু প্রত্যয় - যারা সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করে তাদের জন্য মৃত্যুর পরে আছে অনন্ত শাস্তির রাজ্য। পরকালের বিশ্বাস হয়তো 'সত্তা'র অনুভূতি তৈরি করে; যেন মৃতদের আত্মা তাদের প্রত্যক্ষ করছে, ফলে সামাজিক নিয়মের প্রাচীন রূপগুলোকে ধরে রাখা সহজ হয়।
তথ্যসূত্রঃ
1. E. K. F Chan, et. al., 'Human origins in a southern African palaeo-wetland and first migrations,' Nature, 28 Oct. (2019).
2. Quentin D. Atkinson, 'Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa,' Science, 332 (2011):346-349.
3. Andrew Smith, 'First people, the lost history of the Khoisan,' Jonathan Ball publishers, (2022):50-52.
4. Hervey C. Peoples., 'Subsistence and the Evolution of Religion,' Hum Nat, (2012):23:253-269.
5. G. E. Swanson, 'The birth of the Gods: the origin of primitive belief,' Ann Arbor: University of Michigan Press, (1960).
6. Robin Dunbar, 'How Religion Evolved and Why it Endures,' Penguin Random House, UK, (2022).
7. 'আধুনিক মানুষ', বিলুপ্তপ্রায় মানব প্রজাতি এবং আমাদের সমস্ত কাছের পূর্বপুরুষদের নিয়ে গঠিত দলকে বলে হোমিনিন, এর মধ্যে আছে হোমো জেনাস, অস্ট্রালোপিথেকাস, প্যারানথ্রোপাস এবং আর্ডিপিথেকাস। অর্থাৎ বলা যায়, শিম্পাঞ্জি থেকে আলাদা হয়ে যে মানব প্রজাতিগুলোর উদ্ভব হয়েছে তাদের একসঙ্গে বলে হোমিনিন।
8. Richard Klein, with Blake Edgar, "The Dawn of Human Culture," John Wiley & Sons, Chapter 1 (2002).
9. Christopher S. Henshilwood et al., "An abstract drawing from the 73,000 year old levels at Blombos Cave, South Africa," Nature, 562, (2018):115-118.
10. H. P. Schwarcz, et al., "ESR dates for the hominid burial site of Qafzeh in Israel", Journal of Human Evolution, 17(8), (1988):733-737.
11. Roebroeks W., Sier M. J., Nielsen TK, De Loecker D, Parés JM, Arps CE, Mücher HJ. Use of red ochre by early Neandertals. Proc Natl Acad Sci USA. 2012 Feb. 7;109(6):1889-94.
12. Hervey C. Peoples, Pavel Duda & Frank W. Marlowe, 'Hunter-Gatherers and the Origins of Religion,' Hum Nat, (2016).