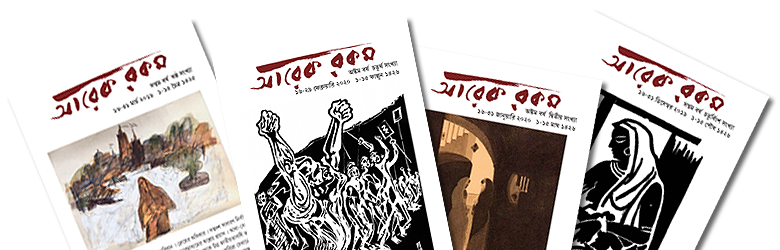আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যা ● ১-১৫ আগস্ট, ২০২৪ ● ১৬-৩১ শ্রাবণ, ১৪৩১
প্রবন্ধ
উন্নয়ন বনাম ভাতাঃ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট
দেবলীনা বিশ্বাস
২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় ৪২টি আসনের মধ্যে ২৯টি আসনে শাসকদল জিতেছে। ফল ঘোষণা থেকেই সমাজমাধ্যম এবং বিভিন্ন জন পরিসরে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন মীম-এর ছড়াছড়ি। কয়েকটা মীম এরকম - 'চাকরী সেরকম দরকার নেই। শিক্ষা না পেলেও হবে। শুধু যেভাবেই হোক পকেটে টাকা ঢুকে গেলেই শান্তি। বাংলা এবং বাঙালী এটাতেই খুশি, এটাই তাদের চয়েস।' / 'শিক্ষা আজ ভাতা নিতে ব্যস্ত'। / 'আজকের ফলের জন্য দায়ী সেইসকল বরেরা যারা বউদের হাতখরচা দেয় না।' এছাড়াও বিভিন্ন জনপরিসরের আলোচনায় উঠে আসছে যে সাধারণ মানুষের 'ভিখারী মানসিকতা', তারা যে নিজে থেকে কিছু করতে পারবে, এটা তারা আর মনেও করেনা। এটার একটা সরলীকৃত রূপ হল পশ্চিমবঙ্গবাসী ভাতায় বেশী নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। ফলে সাধারণ মানুষের আসল উন্নয়নের কোনও ইচ্ছা নেই। ভাতাতেই খুশি সবাই। একটি ভাতা-নির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মূলত উন্নয়নের পরিপন্থী এবং ভাতায় বিশ্বাসী।
এই ভাতা বনাম আসল উন্নয়নের প্রেক্ষাপট মূলত রাজ্য সরকারী কিছু প্রকল্প যা বিগত দশক ধরে মহিলাদের ক্ষমতায়নের উপায় হিসেবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথী, লক্ষীর ভাণ্ডার ইত্যাদি। এই প্রকল্পগুলো মূলত ক্যাশ ট্রান্সফার গোছের এবং মূল উপভোক্তা হলেন মহিলারা। তবে এই লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে যে পলিসিটি বেশীভাবে আলোচনায় উঠে এসেছে তা হল 'লক্ষীর ভাণ্ডার'। লোকসভা নির্বাচনের আগেই এই প্রকল্পের মাসিক ভাতার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। অগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের জন্য মাসে ৪০০ টাকার বদলে ১,০০০ টাকা, আর অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের জন্য মাসে ৫০০ টাকার বদলে ১,২০০ টাকা। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই ভোট পরবর্তী সময়ে অনেকেই এই ভাতার বৃদ্ধির ফলে শাসকদলের জয়, এই সরল সমীকরণকে সত্যি বলে ভেবেছেন। যেকোনো নির্বাচনী জয়ের নেপথ্যে বিবিধ কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু হবে সেই অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা যেখান থেকে এই ভাতা বনাম উন্নয়নের ন্যারেটিভের জন্ম।
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাঃ
যেকোনো অর্থনীতির কাঠামো (structure) নির্ভর করে দেশের জাতীয় উৎপাদন তথা জাতীয় আয়-এর ক্ষেত্রে কোন সেক্টর/ক্ষেত্র-র অবদান কত, দেশের জনগণ কোন ক্ষেত্রে সংযুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছেন এবং যে আয় হচ্ছে তার পরিমাণ তথা সেই ক্ষেত্রের জীবিকার শর্তাবলীর উপর। অর্থনৈতিক কাঠামোর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, দেশের শ্রমিকরা কোন ক্ষেত্রে কীভাবে নিয়োজিত, তাদের শ্রম-এর শর্তাবলী এবং তাদের জীবিকার অবস্থা। এই অর্থনৈতিক কাঠামো অনুযায়ী, দেশের সর্বমোট আয় কৃষি ক্ষেত্র, শিল্প এবং নির্মাণ ক্ষেত্র এবং পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে আসে।
অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি দেশ বা রাজ্যে উন্নয়ন হলে সেখানকার জনসংখ্যার মাথাপিছু গড় আয় বাড়বে। এছাড়াও, অর্থনৈতিক কাঠামোর দিক থেকে, দেশের আয়ের বৃহদাংশ শিল্প বা পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে আসবে। একই সাথে দেশের বেশীরভাগ কর্মক্ষম মানুষ নিয়োজিত থাকবেন শিল্প বা পরিষেবা ক্ষেত্রে। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে একটি কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা যাবে, যেখানে কম উৎপাদনশীল কৃষি বা প্রাথমিক ক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে এবং শিল্প বা পরিষেবা ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীলতা বাড়বে।
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বর্তমানে অর্থনৈতিক কাঠামোর অবস্থা বিচার করতে গেলে আয় এবং কর্মসংস্থানে কৃষি ক্ষেত্রের গুরুত্বের দিকটি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। পরিসংখ্যান বলছে ২০১১-১২ সালে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির মোট আয়ের ৫০% আসত পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে। কৃষি ক্ষেত্র ছিল ২৬% আয়ের উৎস এবং শিল্প তথা নির্মাণ ক্ষেত্র থেকে আসত মোট আয়ের ২৪%। ২০২৩-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৫১% আয়ের উৎস পরিষেবা। ২৭% আয় আসে শিল্প তথা নির্মাণ থেকে আর ২২% আয় আসে কৃষি ক্ষেত্র থেকে। সুতরাং আয়ের উৎসের দিক থেকে বিচার করে দেখতে গেলে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে প্রাথমিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব কমছে এবং শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের গুরুত্ব বাড়ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব মেনে একটি বিশেষ ধরণের পরিকাঠামোগত পরিবর্তন রাজ্যের অর্থনীতিতে লক্ষ করা যাচ্ছে। আয়ের উৎসের নিরিখে এই পরিবর্তন ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও লক্ষ করা গেছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির সাথে ভারতীয় অর্থনীতির এই ক্ষেত্রে কোনো চরিত্রগত পার্থক্য নেই।
কর্মসংস্থানের নিরিখে বিচার করে দেখতে গেলে, পশ্চিমবঙ্গে বিগত দশকেয়পরিষেবা ক্ষেত্র বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাৎসরিক শ্রম সমীক্ষা (পি.এল.এফ.এস.)- এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১১-১২ সালে কর্মক্ষম মানুষের ৪০% নিযুক্ত ছিলেন প্রাথমিক বা কৃষি ক্ষেত্রের সাথে, ২০২২-২৩ সালে এই সংখ্যাটি হয়ে দাঁড়ায় ৩২%। শিল্প তথা নির্মাণ ক্ষেত্রে ২০১১-১২ সালে প্রায় ২৭% কর্মক্ষম মানুষ যুক্ত ছিলেন যা বেড়ে ২০২২-২৩-এ হয়েছে ৩১%। অন্যদিকে ২০১১-১২ সালে ৩১.২৭% কর্মক্ষম মানুষ নিযুক্ত ছিলেন পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে, ২০২২-২৩-এ এসে দেখা যাচ্ছে কর্মক্ষম মানুষের ৩৬% এই ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের বেশীরভাগ মানুষ প্রাথমিক বা কৃষি ক্ষেত্র ছেড়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য শিল্প ও নির্মাণ তথা পরিষেবা ক্ষেত্রকে বেছে নিচ্ছেন। কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে এই যে পরিষেবা ক্ষেত্রের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়া এটা ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্টও বটে। শুধু পার্থক্য হল, কর্মসংস্থানের নিরিখে ভারতীয় অর্থনীতিতে এখনও প্রাথমিক ক্ষেত্রেই প্রায় ৪২% কর্মক্ষম মানুষ নিযুক্ত, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৩২% কর্মক্ষম মানুষ নিযুক্ত। অর্থাৎ কর্মসংস্থানের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতির তুলনায় শিল্প ও নির্মাণ তথা পরিষেবার গুরুত্ব অনেক বেশী। যেকোনো উন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর সাথে যদি একটি তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাবে, উন্নত দেশের কর্মক্ষম মানুষ বেশী নিযুক্ত পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে এবং আয়ের সিংহভাগও আসে এই ক্ষেত্র থেকে। সুতরাং, পরিকাঠামোগত দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির পরিকাঠামোর এবং উন্নত দেশের অর্থনীতির পরিকাঠামোর মধ্যে একটি সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং যা কোথাও আপাতদৃষ্টিতে একটি বিশেষ ধরণের উন্নয়নের প্রবণতার দিক নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন সংক্রান্ত দুটি বিপরীতমুখী আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অর্থনীতির পরিসংখ্যান একটি বিশেষ ধরণের উন্নয়নের প্রবণতার কথা বলছে, আর সমাজমাধ্যম এবং জনসাধারণের মতবাদ ভাতা নির্ভর অর্থনীতির ভাষা ব্যক্ত করছে। এই দুই বিপরীতধর্মী প্রবণতা খুব স্বভাবতই উন্নয়নের প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন জাগায়।
অর্থনীতিতে উন্নয়ন ব্যাপারটি একমাত্রিক নয়। এটি একটি বহুমাত্রিক তত্ত্ব। সেই জন্য উন্নয়ন পরিমাপের জন্য বিবিধ সূচকের ব্যবহারের প্রচলন আছে। তাই মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোগত পরিবর্তন যেমন উন্নয়নের প্রবণতা নির্দেশ করে, ঠিক একইভাবে মহিলা শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা বিবিধ সূচক ব্যবহার করতে হয় উন্নয়নের প্রকৃতি নির্ণয় করার জন্য। তাই উন্নয়ন তত্ত্বে মহিলাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একটি দেশে, কর্মক্ষম মহিলারা যদি কাজের সাথে যুক্ত থাকেন, উপার্জন করেন, রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকেন, তাহলে মহিলাদের ক্ষমতায়নের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাটিকেও বোঝায়। উন্নত দেশের মহিলা শ্রমিক জনসংখ্যা অনুপাত এবং কর্মী জনসংখ্যা অনুপাত অপেক্ষাকৃত বেশী। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ সবই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি সূচক হিসেবে ভাবা চলে। এই প্রেক্ষিতে, এটা উল্লেখ্য যে এই রাজ্যে রাজনীতির ময়দানে মহিলা ভোটের গুরুত্ব বিগত কয়েক বছরে অনেক বেড়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে মহিলা ভোটারের সংখ্যাও বিগত দশকে বেড়েছে। এই প্রবণতা মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির দিক নির্দেশ করে এবং অর্থনৈতিক পরিসরে তাদের অবস্থান সম্পর্কেও প্রশ্ন জাগায়। বিষয়টিকে আর একটু বিশদে বোঝার জন্য বিগত দশকে রাজ্যে কোন সেক্টরে মহিলা কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটেছে, সেখানকার কাজের ধরণ, কর্মীদের অবস্থান, তারা ঠিক কি ধরণের কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছেন, কোন সেক্টরে তাদের বেশী আধিক্য সেই সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণার প্রয়োজন।
এই আলোচনায় আগেই এসেছে যে বিগত দশকে পশ্চিমবঙ্গে কর্মক্ষম মানুষেরা প্রাথমিক ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছে শিল্প তথা পরিষেবা ক্ষেত্রে কাজের সন্ধানে। কর্মসংস্থানে নারীপুরুষের বিন্যাস দেখলে ঠিক কারা প্রাথমিক ক্ষেত্র ছাড়ছেন এই বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হবে। ২০১১-১২ এবং ২০২২-২৩ এর মধ্যে প্রাথমিক বা কৃষি ক্ষেত্র ছেড়েছেন মূলত পুরুষ কর্মীরা এবং বেছে নিয়েছেন শিল্প তথা পরিষেবা ক্ষেত্রকে কর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে। তবে শিল্প ও নির্মাণ ক্ষেত্রের মধ্যে পুরুষ কর্মীদের মূলত কাজের সুযোগ ঘটেছে নির্মাণ ক্ষেত্রে। অন্যদিকে, ২০১১-১২ এবং ২০২২-২৩-এর মধ্যে মহিলা কর্মীরা মূলত শিল্প ও নির্মাণ ছেড়ে যোগদান করেছেন কৃষি এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে। ঠিক কোন ধরণের কাজ ছেড়ে তারা আবার ফিরে যাচ্ছেন কৃষি ক্ষেত্রে? এখানে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, যে প্রাথমিক ক্ষেত্র মূলত কম উৎপাদনশীল। কৃষিকাজ লাভজনক না হলেই সাধারণত একটু ভালো উপার্জনের আশায় মানুষজন অন্য সেক্টরে কর্মসংস্থানের জন্য যোগদান করেন। তাই পুরুষ কর্মীদের প্রাথমিক ক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়ার অর্থনৈতিক যুক্তিটি স্পষ্ট। কিন্তু মহিলা কর্মীদের কম উৎপাদনশীল প্রাথমিক ক্ষেত্রে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা কি অর্থনৈতিক সঙ্কটের আভাস দিচ্ছে? ঠিক কি ধরণের কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছেন এই মহিলারা? ২০২২-২৩-এর পরিসংখ্যান বলছে প্রাথমিক ক্ষেত্রে কৃষিকাজের সাথে নয়, বরং মহিলারা নিযুক্ত হচ্ছেন পশু প্রতিপালনের মতো কাজের সাথে। সেটি আর যাই হোক খুব লাভজনক কাজ যে নয়, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।
এ তো গেল, এক দশকে কি পরিবর্তন হয়েছে তার কথা। কিন্তু ২০২২-২৩-এ পুরুষ কর্মী এবং মহিলা কর্মীদের কর্মসংস্থানের সেক্টরগত একটি তুলনা করলে দেখা যাবে, প্রাথমিক ক্ষেত্রে ২৯% পুরুষ কর্মী, শিল্প ক্ষেত্রে যুক্ত ১৫.৮% পুরুষ কর্মী, নির্মাণের সাথে যুক্ত প্রায় ১৭% এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে যুক্ত ৩৭.২১% পুরুষ কর্মী। সেখানে মহিলা কর্মীর নিরিখে ৪০% মহিলা প্রাথমিক ক্ষেত্রে, শিল্প ক্ষেত্রে যুক্ত ২৪.৫৯% কর্মী এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ৩৪.১১%। সুতরাং, নারী, পুরুষ শ্রমিকের নিরিখে, প্রাথমিক ক্ষেত্র এবং শিল্প ক্ষেত্রে মূলত নারী শ্রমিক এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে মূলত পুরুষ শ্রমিকের আধিক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, শিল্প ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে মহিলা শ্রমিকের আধিক্য। বিগত দশকে রাজ্যে খুব উল্লেখযোগ্য শিল্পায়ন ঘটেনি, যার প্রতিফলন স্বরূপ মহিলা কর্মী এবং পুরুষ কর্মীদের শিল্প ক্ষেত্র ছাড়ার প্রবণতা দেখা গেছে। তবুও পুরুষ কর্মীদের তুলনায় মহিলা কর্মীদের আধিক্য শিল্প ক্ষেত্রে, শিল্পায়নের প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন জাগায়। ঠিক কী ধরণের শিল্প হয়েছে, যেখানে মহিলা কর্মীরা নিযুক্ত হচ্ছেন? এই উত্তর খোঁজার জন্য শিল্প ক্ষেত্রকে আর একটু বিশদে জানার প্রয়োজন।
শিল্প ক্ষেত্রকে আরও ভেঙে দেখলে দেখা যাবে, মহিলারা মূলত স্বনিয়োজিত ক্ষেত্রের সাথে জড়িত। শিল্পক্ষেত্রে যতজন মহিলা নিয়োজিত আছেন, তাদের মধ্যে প্রায় ৭৩% শতাংশ মহিলা এই স্বনিয়োজিত ক্ষেত্রের সাথে জড়িত। অন্যদিকে পুরুষ কর্মীদের মাত্র ২৩.২৯% স্বনিয়োজিত ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত। পুরুষ কর্মীরা মূলত নিয়মিত বেতন পাওয়া যায়, এমন ধরণের কাজের সাথে যুক্ত। যেখানে প্রায় ৪৯% পুরুষ কর্মী শিল্প ক্ষেত্রে বেতনভুক্ত, মহিলা কর্মীদের জন্য সেই পরিসংখ্যানটা মাত্র ৪%। ঠিক কি ধরণের শিল্পের সাথে যুক্ত এই স্বনিয়জিত মহিলা কর্মীরা? তথ্য বলছে প্রায় ৪৯% মহিলা বিড়ি বাঁধাইের কাজ করছেন। এছাড়াও জরির কাজ এবং বিভিন্ন গয়নাগাটির ট্রিমিং-এর কাজ, টেলারিং-এর কাজ এবং কিছু ঘরোয়া কাজে ব্যবহৃত জিনিষপত্র বানানোর কাজ - এই ধরণের কাজে বিগত দশকে মহিলাদের বেশী উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিল্প ক্ষেত্রে 'স্বনিয়োজিত কাজ' এই ক্যাটাগরিটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। স্বনিয়োজিত কাজ বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। যেমন, একক কর্মী যারা কোনো কর্মচারী নিয়োগ করেন না, এবং যারা কর্মচারী নিয়োগ করেন। কিন্তু উপরোক্ত ক্ষেত্রে এমন ধরণের স্বনিযুক্তির কথা বলা হয়েছে, যেখানে আলাদা করে কর্মচারী নিয়োগ করা হয় না। শিল্প ক্ষেত্রে, প্রায় ৭৩ শতাংশ মহিলা একক কর্মী, অর্থাৎ কোনো কর্মচারী নিয়োগ করার অবকাশ থাকছে না। তাহলে শিল্প ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থান ঘটেছে মূলত কম বিনিয়োগ যুক্ত ছোট শিল্পের ক্ষেত্রে। এনারা মূলত অনিয়োজিত শ্রমিকের অংশ হতেন, না হয়ে খুব কম আয়ের এই ধরণের স্বনিয়োজিত কর্মের সঙ্গে যুক্ত আছেন।
বিগত দশকে, পশ্চিমবঙ্গে যে ক্ষেত্রটি সবথেকে বেশী জীবিকার সুযোগ ঘটিয়েছে তা হল পরিষেবা ক্ষেত্র। তবে কাজের প্রকৃতি বিচার করলে, এখানে যেমন অনেক বেশী টাকার চাকরি রয়েছে, ঠিক একইভাবে বিশেষত গ্রামে রয়েছে, খুচরো ব্যবসায়ী এবং পেটি ট্রেডাররা। এই ক্ষেত্রের কাজের ধরণকে আরও একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, বিশেষত মহিলারা এখানে বেশীরভাগ বেতনভুক কর্মী। পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে নিযুক্ত প্রায় ৬৪.৪৩% মহিলা নিয়মিত বেতনভুক্ত কর্মী। ঠিক কী ধরণের কাজের সাথে যুক্ত এই বেতন আয়ী মহিলারা? প্রায় ৪৩% মহিলা যুক্ত আছেন রান্নার কাজ বা গৃহ পরিচারিকার কাজে। আর প্রায় ১০% মহিলা নিযুক্ত আছেন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে। পরিষেবা ক্ষেত্রে যে ধরণের কাজের সুযোগ ঘটেছে তাকে মূলত অসংগঠিত কাজ হিসেবেই ধরা চলে। অর্থাৎ এই ধরণের কাজে কোনো সবেতন ছুটি, সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই এবং কাজের কোন নিশ্চয়তাও নেই।
ওপরের আলোচনা থেকে একটি ব্যাপার স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর যে গঠনগত পরিবর্তন বিগত এক দশকে হয়েছে, তাতে মহিলা কর্মী জনসংখ্যা অনুপাত বেড়েছে, যা অবশ্যই আশার আলো দেখায়, কিন্তু সেই গঠনগত পরিবর্তন ভালো উপার্জনের রাস্তা, সবেতন ছুটি, কাজের সুরক্ষার পথ মসৃণ করে দেয়নি। বিশেষ করে মহিলাদের জন্য কম উৎপাদনশীল, কম বিনিয়োগ যুক্ত এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বনিয়জিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটেছে। কিছু ক্ষেত্রে নিয়মিত বেতনের কর্মসংস্থান হলেও সেটা কখনই 'আইএলও'-র ভাষায় 'ডিসেন্ট ওয়ার্ক' বা সম্ভ্রান্ত কাজ নয়। এই ধরণের কর্মসংস্থান মহিলাদের উপার্জনের পথ হয়তো খুলে দিয়েছে, কিন্তু এই ধরণের কর্মসংস্থান মহিলাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে পারবে কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন রয়েছে।
এই অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে যেকোনো ধরণের 'ক্যাশ ট্রান্সফার পলিসি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা থাকে। বিশেষ করে কম আয়ের পরিপূরক হিসেবে 'ক্যাশ ট্রান্সফার পলিসি' ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক হবে। 'লক্ষীর ভাণ্ডার' খুব স্বভাবতই সেই অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'প্রতীচি ট্রাস্ট'-এর একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে 'লক্ষীর ভাণ্ডার'-এর টাকা মহিলারা মূলত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য এবং সংসারের খরচের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। স্বল্পকালীন সময়ে, যখন এই ধরণের কর্মসংস্থানেরই সুযোগ ঘটছে, সেই ক্ষেত্রে এই সরকারী প্রকল্পের গুরুত্ব প্রশ্নাতীত।
কিন্তু এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, বিগত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন কোথাও বেশী উৎপাদনশীল সেক্টরে মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেনি বরং স্বল্প উপার্জনের স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। এই কর্মসংস্থানের আকালের সময়ে স্বনিযুক্তি এবং কম উপার্জনের কর্মসংস্থান-এর পরিপূরক হিসেবে 'লক্ষীর ভাণ্ডার' হয়তো একটি তাৎক্ষণিক সুবিধা প্রদান করছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি না করলে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের উন্নয়নের সম্ভাবনা ক্ষীণতর হবে।