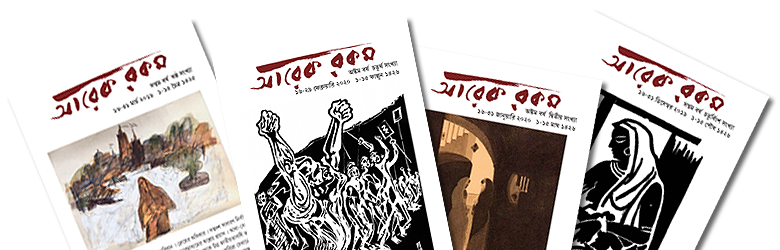আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যা ● ১-১৫ আগস্ট, ২০২৪ ● ১৬-৩১ শ্রাবণ, ১৪৩১
প্রবন্ধ
শিক্ষার রকমফের
শুভাশিস মুখোপাধ্যায়
একবার গেছি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক প্রত্যন্ত গ্রামের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে, সপ্তম থেকে নবম শ্রেণির ছাত্রীদের হাতেকলমে বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহিত করতে। গ্রামটি সত্যিই খুবই প্রান্তিক অবস্থানে। বিদ্যালয় এবং তার সংলগ্ন তিন-চার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনও পরিকাঠমোই নেই। বিদ্যালয় বসে সকাল আটটায়, আর সূর্যাস্তের আগেই, খুব বেশি হলে বিকেল তিনটের মধ্যে বিদ্যালয় ছুটি হয়ে যায় কেননা কোনো শ্রেণিকক্ষেই তখন আর পঠন-পাঠনের উপযোগী পর্যাপ্ত আলো থাকেনা!
ট্রেন, বাস, ভটভটি, আবার বাস এবং ভ্যান রিক্সা করে বিদ্যালয়ে পৌঁছনোর পর এলাহি আতিথেয়তা, যে অপার বিস্ময়-মিশ্রিত দৃষ্টি নিয়ে আমরা সাদা চামড়ার সাহেবদের দিকে তাকিয়ে থাকি, অবিকল সেই দৃষ্টি নিক্ষেপ মারফৎ উঠতি বয়সের বালিকারা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বিদ্যালয়ের উঠোনে এক বিরাট বট গাছ, তার চারপাশ গোলাকার করে বাঁধানো, বেশ বসার বেঞ্চির কাজ চলে যায়। সেখানে ইতিউতি ছাত্রীদের মা-কাকিমা-বৌদিদের ভীড়। আগে থেকেই কড়ার থাকায় সঙ্গে রয়েছে একটি কলেজের এক ভূগোলের অধ্যাপিকা, একজন ভূগোলের গবেষক ছাত্রী, যে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়েসি।
আমার ভাগে পড়েছে সপ্তম শ্রেণির ভৌত বিজ্ঞান আর যে সামান্য রসায়নের অংশ রয়েছে সপ্তম শ্রেণিতে, সেই দুই অংশ সহজ, সরল কিন্তু যথাযথ পরীক্ষার মাধ্যমে পড়াশুনোর বিষয়টি আরও চিত্তাকর্ষক, মনোগ্রাহী এবং নতুন বিষয় শিখতে পারার আনন্দ কীভাবে উপভোগ করা যায় তার এক জীবন্ত উদাহরণ হাজির করা। ফেলে দেওয়া ডটপেনের রিফিল, হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি, টিনের ছিপি, কাগজ, কাঠের টুকরো - এইসব 'বাজে', 'অ-দরকারি' জিনিস দিয়ে বই-এ বর্ণনা করা পরীক্ষাগুলো করা যাবে, ছাত্রীদের মনে এমন বিশ্বাস যোগান দিতেই হিমসিম অবস্থা।
কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে প্রত্যেকের জন্য ওইসব 'খেলনা' বার করে হাতে হাতে ধরিয়ে দেওয়ার পর তাদের বিশ্বাস হল যে এটা 'খেলা'-র ক্লাস নয়, সত্যি সত্যি কিছু পড়াশুনোর বিষয় রয়েছে। জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মা-কাকিমা-বৌদিরাও একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন - যাক, পড়ার ক্লাসটা নেহাৎই নষ্ট বোধহয় হচ্ছে না! ফেলে দেওয়া রিফিল আর হোমিওপ্যাথির শিশি দিয়ে যখন তাপ প্রয়োগের দ্বারা গ্যাসের প্রসারণ সংক্রান্ত পরীক্ষাটি সবাই যে যার মতো করার সুযোগ পেল এবং হাতে, বিদ্যালয়ের সাদা পোষাকে পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটের রং লাগিয়ে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল, তখন আমার সুযোগ এল, পাঠ্য-বইয়ে এই বিষয়ে যা লেখা থাকেনা, বা গোটাগুটি ভুল লেখা থাকে, সেগুলি নিয়ে কথা বলার। ছাত্রীরা উত্তেজিত, বইতে যা লেখা আছে, তা সত্যিই ঘটে, সেই বিষয়গুলি নিজে নিজে পরীক্ষা করে দেখা যায়!
এই সময় আমার নজর কাড়ল বাকিদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোটো, বয়েসের তুলনায় একটু কম উচ্ছ্বল একটি মেয়ে। অন্যদের চেয়ে একটু বেশি মনোযোগী, পরীক্ষাগুলো করার আগে মনে হয় কী করতে হবে একটু ভেবে নিচ্ছে বলে পরীক্ষা শেষ করতে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি সময় নিচ্ছে। সবাই যখন বায়ু ভর্তি শিশির বাইরেটা প্রাণপণে চেপে ধরে পরীক্ষাটা বার বার করছে, তখন মেয়েটি গুটিগুটি পায়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে মেয়েদের আড় ভেঙে গেছে, বয়েসের দূরত্ব ভুলে অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। মেয়েটি বলল, আচ্ছা, শিশিতে জল ভরে এই পরীক্ষাটা করলে কি পরীক্ষার ফল একই হবে? সবাইকে এই নতুন পরীক্ষাটা করতে উৎসাহিত করলাম। অনেকবারের চেষ্টায় প্রায় সবাই পরীক্ষাটা করতে পারল। সবাই অবাক! পরীক্ষার ফল একই হল। সেই ছোটো মেয়েটি বলল, এমনটাই হওয়া স্বাভাবিক, তাপের ফলে জলেরও তো প্রসারিত হওয়ার কথা! আমি তো চমৎকৃত।
ইতিমধ্যে আমার ঘরের মেয়েরা গেল ভূগোলের ঘরে, আর ভূগোলের ঘর থেকে মেয়েরা এল আমার ঘরে। এবারের অভিজ্ঞতা প্রায় একই রকম। খাওয়ার বিরতি, তার মাঝেই চলছে মেয়েদের অজস্র প্রশ্ন। ঘরে আর প্রায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। এবারের মতো ইতি। ছলছল চোখে মেয়েরা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। আমাদের জন্য ভ্যান রিক্সার খোঁজে একজন একটু এগিয়ে লঞ্চ ঘাটের দিকে পাড়ি দিয়েছে।
গল্পের ছলে মেয়েটিকে বললাম, ধর আমি বাসের ছাদে বসে যাচ্ছি, বাসটাও যাচ্ছে খুব জোরে, আমাদের সবাইকে শেষ লঞ্চটা তো ধরিয়ে দিতে হবে। এমন সময় বাসের সামনে এসে গেছে একটা ছাগলছানা, আর বাসটা খুব জোরে ব্রেক মারল (স্থানীয় ভাষা তখন ওদের কাছ থেকেই কিছুটা রপ্ত করেছি)। কী ঘটতে পারে? সেই ছোট মেয়েটির সপ্রতিভ উত্তর - "তুমিতো চলছিলে বাসের সঙ্গে, তুমিতো আর জানোনা যে বাসটা ব্রেক মারবে, তুমি যেমন সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলে, তেমনিই এগিয়ে যাবে"। গতিজাড্য বিষয়ে এমন সঠিক অনুধাবন এর আগে কখনও দেখিনি। পরখ করার জন্য আরও এক ধাপ এগিয়ে বলি, ধরো আরও খানিকদূর গিয়ে বাসটা পড়লো একটা গর্তে, আর আমি সেই ধাক্কায় বাসের ছাদ থেকে ছিটকে ওপরে উঠলাম। ইতিমধ্যে বাস তো চলতে শুরু করেছে আর আমি শূন্যে! কী ঘটতে পারে? মেয়েটি একগাল হেসে ঠাট দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভাষায় বলে উঠলো, "কী আবার হবে, তুমি ফের বাসের ছাদেই পড়বে, নিচে নয়। বাস কি আর জানে যে গর্তে পড়ার সময় তুমি আকাশপানে 'আপ' (বলতে চেয়েছ লাফ) দেছো, ও তো জানে তুমি ঠায় বাসের মাথায় বসে আছো"। এই প্রশ্ন আমি হয়তো কয়েক হাজার বিভিন্ন স্তরের পড়ুয়াদের আগেও করেছি, কিন্তু জীবন থেকে শেখা অভিজ্ঞতাকে এমন নিশ্চিন্তে, এমন সহজে আত্মস্থ করার কেরামতি আজও দেখিনি।
মেয়েটি হতদরিদ্র ঘরের, বিধবা মা, মতান্তরে স্বামী-পরিত্যক্তা। দুবেলা পেট ভরে খাবার জোটেনা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এবং অন্য কয়েকজন শিক্ষিকার আন্তরিক সাহায্যে মেয়েটি লেখাপড়া চালাচ্ছে। পঞ্চম শ্রেণি থেকে প্রতিটি পরীক্ষায় নব্বইএর ঘরে সব বিষয়ে নম্বর পেয়ে প্রথম হয়ে পরের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হচ্ছে। কৌতূহল থাকায় নানান সূত্রে মেয়েটির খোঁজ রাখার চেষ্টা করতাম। মেয়েটি মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে খুব ভালো ফল করে। ওই বছরে প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র বারে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ইংরাজির নম্বর যোগ না করে মেধা তালিকা প্রকাশিত হয়। মেয়েটি তাতে প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে ছিল। এখন সে একটি জেলা হাসপাতালের অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন ডাক্তার।
।। দুই ।।
বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের বিজ্ঞান-মনস্ক করার জন্য ভারত সরকারের একটি প্রকল্পের নাম 'ইন্সপায়ার' প্রকল্প। এই প্রকল্পে বিদ্যালয়গামী পড়ুয়ারা সহজ, কিছুটা সরল, অর্থাৎ তাদের জ্ঞানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, কিছু মডেল বানায়, যে মডেলগুলির মূলসূত্রগুলি তাদের আয়ত্তে থাকার কথা। প্রতিটি জেলায় বছরের এক নির্দিষ্ট সময়ে পড়ুয়ারা তাদের বানানো মডেল নিয়ে জেলার কোনো এক নির্দিষ্ট কেন্দ্রে হাজির হয় এবং সরকারের বিদ্যালয় দপ্তরের অধীনে বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একদল মানুষ এই প্রকল্পগুলির চুলচেরা বিচার করে সেই জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোটা তিনেক প্রকল্প বেছে নেয়। এইরকম ভাবে রাজ্যের সব জেলা থেকে বাছাই প্রকল্পগুলি থেকে গোটা তিনেক বাছা হয় সারা রাজ্যের জন্য। অন্যান্য রাজ্যেও এই একই পদ্ধতিতে সেই সেই রাজ্যের জন্য প্রকল্প বাছা হয়। শেষে সারা দেশের জন্য সব রাজ্যের মধ্যে থেকে কিছু 'সেরা' প্রকল্প বাছা হয় এবং এই প্রকল্প রচয়িতারা পড়ার জন্য জলপানি পায়। বলাই বাহুল্য, এই প্রকল্পটি একদিক থেকে প্রতিযোগিতামূলক।
সেবার এই রাজ্যস্তরের 'সেরা' প্রকল্প বাছাইয়ের কাজে ডাক পড়েছে কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে। দুটো তলা জুড়ে চাঁদের হাট। স্কুলের ইউনিফর্ম পরা একরাশ পড়ুয়া। ছাত্রীর সংখ্যাই তুলনামূলকভাবে বেশি। মডেলগুলি তারা তৈরি করেছে ভৌত বিজ্ঞান, রসায়ন, জীবন বিজ্ঞান, গণিত এবং পরিবেশ বিজ্ঞানের নানান দিক নিয়ে। আলু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে টুনি বাল্ব জ্বালানোর প্রকল্প রয়েছে বেশ কয়েকটা, সাইকেল চালিয়ে গম ভেঙে আটা করা ইত্যাদি প্রকল্পও রয়েছে।
অন্য একদিকে রয়েছে ইলেক্ট্রনিক্স ভিত্তিক নানান কারুকৌশল - স্বয়ংক্রিয় রেল সিগনালিং ব্যবস্থা থেকে শুরু করে চলমান গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ানোর কৃত-কৌশল। স্বাভাবিকভাবেই যে মূলসূত্রের ওপর ভিত্তি করে এইসব মডেল কাজ করে, তা বিদ্যালয় স্তরের পড়ুয়াদের অগম্য। ব্যতিক্রমী কেউ কেউ নিশ্চয়ই এই বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাতেই পারে, যেটা তার সঙ্গে আলোচনা করলেই মালুম হয়। বেশিরভাগ জেলা থেকেই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে সেইসব জেলার সেরা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলি, যে পড়ুয়ারা অংশ নিয়েছে তারা প্রায় সবাই তৃতীয় প্রজন্মের পড়ুয়া, অল্প কয়েকজন দ্বিতীয় প্রজন্মের পড়ুয়া রয়েছে। এদের প্রায় প্রত্যেকেই এই প্রকল্পের জন্য একজন মাস্টার রেখেছে, যিনি তাদের এই প্রকল্প অনেক ক্ষেত্রে তৈরিও করে দিয়েছেন। এদের পাশে যেসব পড়ুয়া জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তের বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলির সেইসব পড়ুয়াদের অবস্থা করুণ - তারা বাংলায় বলছে, তাদের প্রকল্পগুলিতে গ্রামীণ প্রয়োজনীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট। কেউ করেছে শস্য ঝাড়ার 'থ্রেসার', কেউ বা 'হারভেস্টার'। সহজ, সরল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংর-এর কৌশল উদ্ভাবনীর সঙ্গে ব্যবহার করেছে।
বারান্দার ধারে এক কোণে একটা ঘুপচি মতো জায়গায় ঠাঁই মিলেছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আর পশ্চিম মেদিনীপুরের পড়ুয়াদের। মাথার ওপর আলোটা দপদপ করছে, কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়ালেই মাথা ধরে যাবে। বেচারি পড়ুয়ারা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই সকাল দশটা থেকেই। স্কুলশিক্ষা দপ্তরের একজন জাঁদরেল ডব্লুবিসিএস অফিসারকে আলোটা ঠিক করার কথা বলায় তিনি বিষয়টা মোটেই আমল দিলেন না। তখন বাধ্য হয়ে শিক্ষামন্ত্রীর আসন্ন পরিদর্শন নিয়ে ব্যস্ত আইএএস অফিসারকে দেবভাষা, অর্থাৎ ইংরেজিতে বললাম যে মন্ত্রী এলে আমরা বিশেষজ্ঞরা মন্ত্রীকে কিন্তু পুরুলিয়া-বাঁকুড়া ঘুরিয়ে তবে কলকাতার হিন্দু-হেয়ার-সাউথ পয়েন্ট স্কুলের দিকে নিয়ে আসব! ম্যজিকের মতো কাজ হল এবং খান তিনেক টিউব লাইট লেগে গেল ঝপাঝপ।
পুরুলিয়ার মূলবাসী মেয়েটি ভীরু চোখে, সসংকোচে এককোণে প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে সে নিশ্চিতভাবেই বুঝে গেছে যে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য যে যে রসদ লাগে, যেমন ঝকঝকে খাতা, কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট বা নিদেনপক্ষে সুছাঁদ হাতের লেখায়, সরকারি আধিকারিকের ভাষায় 'স্মার্ট-লুকিং প্রজেক্ট রিপোর্ট' - তার কোনোটিই তার ঝুলিতে নেই। আমরা তিনজন 'বিশেষজ্ঞ' তার দিকে যথাসম্ভব হাসিমুখে এগিয়ে গেলাম। ভাগ্যে আমাদের দলে একজন মহিলা ছিলেন। এখানে একটা কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। সরকারি আধিকারিকদের চেতনায় মহিলা বিজ্ঞানী মানে তাঁকে অবধারিতভাবে জীবন-বিজ্ঞানের হতেই হবে। কিন্তু সেই শাশ্বত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছিল আমাদের ক্ষেত্রে, মহিলা বিজ্ঞানী আধুনিক প্রাণ-রসায়নের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। প্রধানত তাঁর দুর্দমনীয় চেষ্টায় এবং আমাদের সন্মিলিত সহমর্মীতায় একসময় সেই অভ্রংলিহ হিমালয়-সদৃশ তুষাররাজি গলতে শুরু করে এবং মেয়েটি আধা-বাংলা আধা-মুন্ডারি ভাষায় প্রাঞ্জল করে তার বক্তব্য রাখতে শুরু করে। আমাদের সঙ্গে ভূবিদ্যার একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন, যিনি 'ফিল্ড' করার সুবাদে ঐ ভাষাতে কিঞ্চিৎ দক্ষতা অর্জন করায় মেয়েটির কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি একটু সহজ হয়ে যায়।
মেয়েটির বাড়িতে তার বাবা, মা, দুই বোন এবং এক ভাই জন্মান্ধ, একটি ভাই সামান্য দেখতে পায় এবং মেয়েটি নিজে রাতকানা। পুরো গ্রামটিই ভিটামিন-স্বল্পতার শিকার। গ্রামের বাজারহাটে এই গ্রামের সবাইকেই প্রায় সব দোকানদারেরা মালপত্র কেনার সময় ওজনে ঠকায়। মেয়েটি দৃষ্টিহীনদের জন্য একটি সহজ আবার খুবই কাজের এবং যথাযথ ওজনদাঁড়ি বানিয়েছে। স্প্রীং আর এদিক-ওদিক থেকে যোগাড় করা, মূলত ফেলে দেওয়া ঘরেলু জিনিসপত্র দিয়ে বানানো - বিরাট বিরাট ইলেক্ট্রনিক্স সার্কিট দিয়ে লাল-নীল আলো দপদপ করে জ্বলছে-নিভছে, নিমেষে সিগন্যাল খুলছে আবার ঘন্টা বেজে বন্ধ হচ্ছে, তার সঙ্গে এই ভাঙা টিনের বাটিকে ওজনদাঁড়ির প্যান করা, তাও নোড়া দিয়ে ঠুকে ঠুকে, অসমান তাদের চেহারা, দুদিকের ওজনের ফারাককে মেলানোর জন্য স্রেফ একদিকে কটা পাথর সুতো দিয়ে বাঁধা।
নানা বাস্তব-অবাস্তব অবস্থায় যন্ত্রটি দিব্যি উতরে গেল। ওর সঙ্গে একটু গল্পের ছলে জানলাম এই যন্ত্রটা ও এবং ওর গ্রামের প্রায় সবাই ব্যবহার করে। আরও জানা গেল ওদের বিদ্যালয় এতটাই প্রান্তিক অঞ্চলে যে এই 'ইন্সপায়ার' প্রকল্পের কোনও খবর সেখানে যায়নি। এদিকে জেলার কোটা পূর্ণ হয়নি। এমন এক সংকটময় মুহূর্তে ডিআই-এর দপ্তরে প্রধান শিক্ষকদের এক সভায় কোনও এক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মারফৎ এই প্রকল্পের কথা জানতে পেরে মেয়েটির বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কথা প্রসঙ্গে ডিআই 'সাহেব'-কে এই ওজনদাঁড়ির বিষয়টি অবহিত করেন। ঘটনাচক্রে পরেরদিনই প্রকল্প জমা করার শেষ দিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সব কাজ হওয়ায় মেয়েটি তার প্রকল্পের রিপোর্ট একটা যেমন তেমন খাতায় যেমন তেমন করে লিখে এনেছে, কিন্তু নির্ভুল বানান এবং নির্ভুল বাক্যবন্ধ সহকারে। তাকে কেউ এই প্রকল্পের বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত করেনি, আবশ্যিক বিষয়গুলিও বুঝিয়ে বলেনি।
মেয়েটি তার গ্রাম থেকে তিন-চারটি গ্রাম দূরের, হাঁটা দূরত্বে আট-দশ কিলোমিটার হবে এমন একটি গ্রামের একজন প্রবীণ শিক্ষকের সঙ্গে এসেছে, তার যাতায়াত ভাড়া পাওয়া নিয়েও নাকি 'সমস্যা' হচ্ছে! আমাদের তিনজনের সন্মিলিত গলাবাজিতে এই প্রকল্পটিকে মনোনীত প্রকল্পের তালিকায় স্থান দিতে দিল্লি এবং কলকাতার আমলারা বাধ্য হলেন। জানা গেল, মেয়েটি পরেরদিন রাতের ট্রেনে পুরুলিয়া ফিরবে। আমাদের সঙ্গের মহিলা বিজ্ঞানী ঐ প্রবীণ শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে মেয়েটিকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। আমরাও গেলাম। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মেয়েটি বিষয়টি বুঝে গেল। প্রজেক্ট লেখার খাতা এল, রঙ্গিন কলম এল, ওজনদাঁড়ির প্যান এল। মেয়েটি এই যন্ত্রের জন্য বেশ কয়েকটি নতুন উপাদান ভেবে বের করে সেগুলি জুড়ে দিল। পরদিন সকালে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওয়ার্কশপ'-এ যন্ত্রটা রং-চং করে বেশ খোলতাই চেহারা দেওয়া গেল। তবে পুরো বিষয়টির তত্ত্বাবধান করেছে মেয়েটিই, কোথায় কী কী বিষয় জুড়তে হবে তার নির্দেশ দিয়েছে মেয়েটিই। সারা দুপুর ধরে সে বেশ কয়েকবার 'ইন্সপায়ার'-এর ফর্ম্যাট মেনে প্রকল্পটি লিখে তারপর তার চূড়ান্ত বয়ান সে লেখে। এক লপ্তে, একটাও কাটাকুটি না করে।
ওকে তুলতে আমি হাওড়া গিয়েছিলাম। যন্ত্র এবং খাতা দেখে আমি চমৎকৃত। আরও চমৎকৃত একদিনে মেয়েটির রূপান্তর দেখে। একরাতে, কেবলমাত্র কয়েকটি সামান্য সুযোগ তাকে সমাজ-ভীরু, দিশাহারা অসহায় হরিণশিশু থেকে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এক চনমনে কিশোরীতে পরিবর্তিত করে দিয়েছে।
ন-মাস পর একদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় মন্ত্রক থেকে একটা চিঠি এল ক্যুরিয়ার সার্ভিস মারফৎ - পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেসব 'ইন্সপায়ার' প্রকল্প প্রাইজ পেয়েছে, সেইসব পড়ুয়াদের সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। কাজের চাপে ভুলেই গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানের দিন সকালে একটা অচেনা নম্বর থেকে চলভাষে ফোন, ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে পুরুলিয়ার সেই মেয়েটি বলল, স্যার, আজ আসছেন তো, আমি এসে গেছি। বলেই ফোন কেটে দিল। দ্রুত দৌড়োলাম এবং মন্ত্রী মশাই-এর বক্তৃতার মধ্যেই চেয়ারে বসলাম। প্রাইজ বিতরণের সময় দেখলাম মেয়েটি সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম হয়েছে, ভারত সরকারের 'ন্যাশানাল ইনোভেশন কাউন্সিল' এই যন্ত্রটিকে ঐ বছরের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। মেয়েটি যদিও নির্বিকার। ওকে কিছু বলতে বললে ও বলল, ওদের এবং আশপাশের গ্রামে যদি প্রতি দুটি পরিবার পিছু একটি করে এমন যন্ত্র সরকার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে তো ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই যন্ত্রগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করবে। অবশ্য তার এই কথায় হাততালি ছাড়া আর কিছুই তার পাওনা হয়নি।
মেয়েটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল করে 'ইন্সপায়ার' জলপানি পেয়েছিল। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরেও ভাল ফল করেছে, হ্যাঁ, কোনো গৃহশিক্ষক ছাড়াই। এখন সে পশ্চিমবাংলার বাইরের একটি আইআইটিতে 'বায়ো-মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টেশন' নিয়ে গবেষণা করছে। সে নিজের খরচায় সেই ওজনদাঁড়ির আরও উন্নত প্রতিরূপ ঐ অঞ্চলে জনপ্রিয় করেছে বলে খবর পেয়েছি। অন্যায্য সুযোগ নিয়ে যে বা যারা মৌরসীপাট্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এটা সম্ভব হচ্ছে এইসব পড়ুয়াদের বঞ্চিত করে। সামাজিক বঞ্চনার ফলে প্রত্যাখ্যাত পড়ুয়াদের কাছে সেই ন্যায্য সুযোগ তৈরি করার সংগঠিত চেষ্টা হয়তো বিদ্যমান, তবে সেগুলি কতটা সংহত, তার ফল দেখেই মালুম হচ্ছে। যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মাননীয় মন্ত্রীরা নিজেরাই রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে এসেছিলেন; শিক্ষকতা ও শ্রেণি সম্পর্ক নিয়ে তাঁদের সম্যক অভিজ্ঞতাও কম ছিল না, এই বিষয়ে দীর্ঘ আন্দোলনে তাঁদের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এরই মাঝখানে যাপনের ফলেও তাঁদের চিত্তে যে কেন এই বিষয়ে তাঁরা আন্দোলিত হলেন না, সেই রহস্যের সন্ধান আজও পাইনি। ইতোমধ্যে গ্রামের মেধাবীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি গো-মাতার প্রতি উৎসর্গ করা নিষ্পন্ন হয়েছে। কেবল ফুলের ঝারি দিয়ে ধানক্ষেতে ক্ষুদ্র জল-সিঞ্চন যদি এমন সুগন্ধী বাসমতীর জন্ম দেয়, তবে সংগঠিত সিঞ্চন এক বিশালকায় ফলবতী বৃক্ষর জন্ম দেবে এই এক দুর্মর আশা বুঝি শেষ পর্যন্ত নিরাশায় পর্যবসিত হয়ে যাবে!