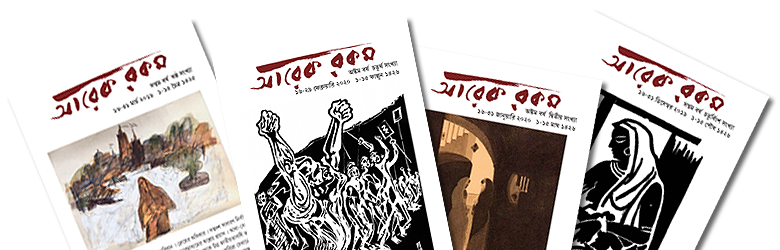আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ ত্রয়োদশ সংখ্যা ● ১-১৫ জুলাই, ২০২৪ ● ১৬-৩১ আষাঢ়, ১৪৩১
প্রবন্ধ
সল্টলেকের আধুনিকতা
অন্বেষা সেনগুপ্ত
স্বাধীনতার পরপর ভারত, পাকিস্তান জুড়ে নতুন শহর তৈরি করার অথবা পুরোনো শহর সম্প্রসারণের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। চণ্ডীগড়, ভুবনেশ্বর, ইসলামাবাদ, নতুন ঢাকা বা পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে সল্টলেক, দূর্গাপুরের মতো শহরকে এই উদ্যোগের উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখতে পারি। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক পরিকল্পনা মাফিক তৈরি এই শহরগুলি সরকারি উদ্যোগে, পশ্চিমী স্থপতিদের নেতৃত্বে তৈরী হয়। চণ্ডীগড়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল ফরাসী স্থপতি লে কর্বুজিয়ারের নাম। তেমনই ভুবনেশ্বরের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জার্মান স্থপতি ওটো কয়েনিসবার্গ; ইসলামাবাদে ছিলেন গ্রীক স্থপতি ডক্সিয়াডিস, ঢাকায় ছিলেন দুই ব্রিটিশ স্থপতি এডোয়ার্ড হিক্স ও রোনাল্ড ম্যাকোয়েল। এই পরম্পরা মেনেই সল্টলেকের পরিকল্পনা ও রূপায়নের সিংহভাগ দায়িত্ব পড়ে সার্বিয়ান স্থপতি দব্রিভজ তস্কোভিচের উপর।
কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবেন সদ্য স্বাধীন হওয়া ভারত পাকিস্তানের এই সাহেব প্রীতি কেন? কয়েকটা সম্ভাব্য উত্তর আছে। প্রথমত, যদিও বিভিন্ন ভারতীয় ও পাকিস্তানী স্থপতিরা এই শহরগুলি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সহকারী হিসাবে বা শিক্ষানবিশ হিসাবে, তাঁদের মধ্যে কেউই কর্বুজিয়ার বা কয়েনিসবার্গের মাপের স্থপতি তখনও হয়ে ওঠেননি। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমী আধুনিকতা, বিজ্ঞান ও উন্নতির ধারণার প্রতি নেহরুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। দারিদ্র, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, বা ভাষাভিত্তিক পরিচিতি নিয়ে ভারত জুড়ে যে লড়াই, তার থেকে উত্তোরণের পথ নেহরু পশ্চিমী আধুনিকতার মধ্যে খুঁজেছিলেন। চণ্ডীগড় প্রসঙ্গে নেহরু বলেছিলেন “Let this be a new town, symbolical of the freedom of India, unfettered by the traditions of the past - an expression of the nation's faith in the future...”। পুরোনোকে পিছনে ফেলে, ভবিষ্যতমুখী শহর নির্মাণের যে স্বপ্ন নেহরু দেখেছিলেন সেই শহর হিন্দু-মুসলমান, মারাঠি-গুজরাতি, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের লড়াইয়ে মত্ত দেশবাসীর পক্ষে কল্পনা করা সেই মুহূর্তে কষ্টসাধ্য ছিল। তাই পশ্চিমী স্থপতিদের এদেশে নিয়ে এসে ভারতবর্ষের স্বপ্নশহর তৈরির প্রয়াস শুরু হয়েছিল। নেহরুর নাম ধরে বলছি ঠিকই, কিন্তু মনে রাখতে হবে নেহরু একধরণের চিন্তাধারার প্রতীক। সেই চিন্তাদর্শনকে বলা যেতে পারে নেহরুয় আধুনিকতা (Nehruvian Modernity), এবং ভারত-পাকিস্তানী নানা প্রকল্পে (যেমন বড় বাঁধ, বিজ্ঞান শিক্ষায় বিপুল বিনিয়োগ, বড় কারখানা) এই চিন্তার প্রভাব স্পষ্ট। তাই ইসলামাবাদ থেকে বিধাননগর সবই নেহরুয় শহর।
স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দুই-তিন দশকে তৈরি এই শহরগুলি কি সত্যি সত্যি জাতি-ধর্মের পরিচিতির ঊর্ধ্বে উঠে 'আধুনিক' হতে পেরেছিল? সল্টলেকের প্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখি। কলকাতার পুব বরাবর বিস্তীর্ণ নোনা জলাভূমি বুজিয়ে শহর তৈরি করা শুরু হয়েছিল ১৯৬২ সালে। মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় এপ্রিলের ১৬ তারিখ (১৯৬২) আনুষ্ঠানিকভাবে সুইচ টিপে পাইপে করে গঙ্গার মাটি ফেলার কাজ শুরু করেন। সল্টলেকের প্রথম বাসিন্দা জীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পরিবার। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে তাঁরা থাকতে শুরু করেন। এরপর একে একে আসেন অপরেশ চৌধুরী (অক্টোবর, ১৯৭০)[১], শিবাজীপ্রতিম বসু (ডিসেম্বর, ১৯৭০)[২] এবং আরও একটা দুটো করে পরিবার। এঁদের মধ্যে কিছু মিল ছিল - বাঙালি, হিন্দু, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবর্ণ, পেশায় সরকারী ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কলেজ লেকচারার ইত্যাদি। এক কথায় বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক। তাঁদের হাত ধরে যে সমাজ তৈরি হয় তার কেন্দ্রে ছিল দুর্গাপুজো, নাটক-থিয়েটার, গানের অনুষ্ঠান, নিয়মিত আড্ডা ইত্যাদি। অপরেশবাবু যেমন স্মৃতি থেকে বলেন, “১৯৭০ সালে প্রথম আমরা - মানে আমাদের বাবারা - পাঁচঘর মিলে দুর্গাপুজো করেছিলাম।... তারপর ৭১ সালে দ্বিতীয় পুজো... তখন লোকসংখ্যা একটু বাড়ল, ৫ ঘরের জায়গায় ১০-১২, তার বেশী না। ’৭২ সালে সংখ্যাটা বাড়ল।... এতটাই বন্ধন আমাদের ছিল যে কারোর কোনো আপদে বিপদে আমরা দৌড়ে যেতাম, তাঁরাও আসতেন। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে 'লবণ হ্রদ নাগরিক সমিতি' তৈরি করি... দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে যে জমায়েত, সামাজিক বন্ধন। পুজোর পর নাটক করতাম, ছেলেদের একটা নাটক, মেয়েদের একটা নাটক, আর ছোটদের নাটক... কাকু, জেঠু, তুই-তোকারি, জমাট বাঁধতে শুরু করলাম”।[৩] এই বর্ণণা থেকে আমরা একধরণের শিক্ষিত, সমরুচি সম্পন্ন, হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের ধারণা পাই। সল্টলেকের ‘আমরা’ এই সমাজ। ‘আমাদের’ উৎসবে কখনও কখনও হাতেগোণা মুসলমান মানুষ সামিল হতেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা ‘ভালো মুসলমান’ - অর্থাৎ মুসলমান পরিচিতি গৌণ।
তাহলে সল্টলেকের ‘ওঁরা’ কারা? সল্টলেকের বাঙালিদের জিজ্ঞাসা করলে প্রায় সমস্বরে সবাই বলবেন অবাঙালিরা বিশেষ করে মারোয়াড়িরা - মোটের উপর সমার্থক হিসাবেই তাঁরা ব্যবহার করেন এই দুটি শব্দ। এ প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করি। আমি সল্টলেকে একটি আবাসনে ফ্ল্যাট কেনার সময়ে দালালবাবু আমায় বলেছিলেন, নিশ্চিন্তে কিনুন, মাড়োয়াড়িদের 'উপদ্রব' এখানে কম। আবাসনের উল্টোদিকেই বসেন এক বিহার থেকে আসা ইস্ত্রিওয়ালা। তবে তাঁদের নিয়ে ক্ষোভ বা দুশ্চিন্তা বাঙালি ভদ্রলোকের তেমন ধরা পড়ে না। মূল অস্বস্তি তাঁদের সল্টলেকের বিত্তশালী মাড়োয়াড়ি সমাজকে নিয়ে। গোটা সল্টলেকে ২০১৫ সালের একটি খবর অনুযায়ী প্রায় ৩৩ শতাংশ অধিবাসী মারোয়াড়ি।[৪] ব্লক ডিরেক্টরি ভিত্তিক আরেকটা সমসাময়িক হিসাব দিলাম নীচে।[৫] নিচের সংখ্যাগুলি থেকেও স্পষ্ট সংখ্যায় বাঙালি বেশী হলেও, সল্টলেকে চোখে পড়ার মতো মাড়োয়াড়ি উপস্থিতি।
| সেক্টর-ব্লক | মোট প্লট | বাঙালি মালিকানা | মাড়োয়াড়ি মালিকানা | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|
| সেক্টর ১ - এই | ৭৫৭ | ৬৮৫ | ৪৪ | ২৮ |
| সেক্টর ২ - সিজে | ৩৩০ | ১৮৮ | ১০৪ | ৩৮ |
| সেক্টর ৩ -৭৫৬ | ৭৫৬ | ২৭৩ | ৩৬৭ | ১১৬ |
মাড়োয়াড়িদের সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, রুচি - সব নিয়েই ভদ্রলোক বাঙালির নানা আপত্তি, অস্বস্তি। যেমন অপরেশবাবুর পর্যবেক্ষণঃ “সমস্ত ব্লকেই তো এখন হাতবদল হচ্ছে। হাত বদলে তো অবাঙালিই আসছে।... সে প্রথমেই কী করছে, বাড়িটা ভেঙে ফেলছে, তার তো প্রচুর পয়সা।... এবং নতুন করে বাড়ি তৈরি করছে। যে ধরণের মেটেরিয়াল দিয়ে বাড়ি করছে তা বলবার মতো নয়, যে ধরণের ডেকরেশন, ভাবা যায় না।... সল্টলেক এখন মিক্স কালচারের জায়গা। একটা সেকশন খুবই এফ্লুয়েন্ট, তারা যে ধরণের লাইফ লিড করে... আনহেলদি খাবার খায়, শিক্ষাদীক্ষার তোয়াক্কা করে না, ফ্যামিলি বিজনেসই মেইন।... দুটো, তিনটে, চারটে করে গাড়ি”।
ইতিহাসবীদ অনুরাধা রায় ও তাঁর মা, ১৯৭৬ থেকে তাঁরা সল্টলেকের বাসিন্দা, তাঁদের কথায়ঃ “একটা বড় ফল্টলাইন বাঙালি-অবাঙালি। পার্কে গেলে দেখবে, মাড়োয়াড়ি মহিলারা দল বেঁধে (ধর্মের) গান গাইছেন... 'জাগরণ'... মাড়োয়াড়িদের ফাংশন হয় পার্ক বন্ধ করে।... সেক্টর-১টা মাড়োয়াড়িদের হয়ে গেছে। ওরা এত টাকা দিচ্ছে...”।[৬] এক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বলেন, “জানি না কতদিন বাঙালিরা আর সল্টলেকে বসবাস করতে পারবে... বাঙলিয়ানাটা চলে যাচ্ছে... বাঙালিরা এমন একটা জাত তাঁদের মধ্যে সহনশীলতা আছে, বোঝাপড়া আছে, অন্যদের ভালোবাসে, কমিউনিটি ফিলিংস আছে, আমাদের কি মুসলিম বন্ধু নেই? আমরা কি মুসলিম রেস্টুরেন্টে খাই না? আমাদের মধ্যে একটা সেকুলারিজম আছে। Bengalis believe in secularism. সেই secularism is vanishing day by day in Salt Lake. ...বাঙালিরা ভদ্রতা জানে। They (অবাঙালি/মাড়োয়াড়ি) are only thinking of themselves and not about the society. That is the problem of Salt Lake at present... they will arrange fair for only their community, not for the mass. বাঙালিরা donate করে, বাঙালিয়ানার খাতিরে donate করে, মানবিকতার খাতিরে donate করে।”[৭] বাঙালি-মাড়োয়াড়ি ভাগটা কোথাও যেন এই বয়ানগুলির মাধ্যমে শিক্ষা বনাম সম্পদ, রুচি বনাম দেখনদারি, দুর্গাপুজোর সংস্কৃতি বনাম হিন্দুত্বের আতিশয্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। শুধু তাই না, মাড়োয়াড়িরা এই কল্পনায় নতুন আসছেন, বহিরাগত, বাঙালি ভদ্রলোক আদি। তবে এই বয়ানগুলি থেকে স্পষ্ট একধরণের ভীতিও। মাড়োয়াড়িদের হাতে টাকা বেশি, তাঁরা সল্টলেকের সব সম্পত্তি কিনে নেবেন, বাঙালিরা আর ঠাঁই পাবেন না এখানে।
স্বভাবতই এখানে প্রশ্ন ওঠে মাড়োয়াড়ি সমাজ তাঁদের এই অপরায়নকে কী চোখে দেখেন? সল্টলেকে থাকার অভিজ্ঞতা তাঁদের কেমন? এই অঞ্চল নিয়ে তাঁদের কী দৃষ্টিভঙ্গি? সল্টলেকের মাড়োয়াড়ি মাত্রই নতুন বাসিন্দা, কোনো পুরোনো বাড়ি কিনে ভেঙে অট্টালিকা বানাচ্ছেন তা কিন্তু নয়। ’৭০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই অল্প সংখ্যক মাড়োয়াড়ি পরিবারের বাস। ১৯৭৭ সালে তৈরি হয় তাঁদের সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদ’। 'সমবাদ' বলে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন সল্টলেকের মাড়োয়াড়ি সমাজ। ডিসেম্বরে তাঁরা সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করেন এখানে। বলা চলে, বাঙালিরা তাঁদের যতই বহিরাগত ভাবুক, সল্টলেকের সঙ্গে তাঁদের নিবিড় যোগ। কিন্তু বাঙালিদের তাঁদের প্রতি মনোভাব নিয়ে মাড়োয়াড়িরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। দুই সমাজে মেলামেশা হয় না। এক মাড়োয়াড়ি গৃহবধূ যেমন বলেন, তিনি পরিচিতর কাছে শুনেছেন বাঙালির থেকে বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কত ঝামেলা। শুধু তাই না, এমন বাঙালি আছেন যাঁরা মাড়োয়াড়িদের বাড়ি বিক্রি করতে নারাজ, তা তাঁরা যত টাকাই দিন না কেন! এই ভদ্রমহিলার কথায় "বাঙালিরা মনে করে আমাদের টাকার গরম।... বাঙালিদের একটা বাড়ি, একটা গাড়ি হলেই মিটে গেল। মাড়োয়াড়িদের একটা গাড়ি থাকলে আরেকটা চাই। বাঙালিদের ক্ষমতা থাকলে আমাদের রাজ্য থেকেই তাড়িয়ে দিত"। তাঁর বান্ধবী, একই ব্লকের বাসিন্দা, আবার মনে করিয়ে দেন, "সল্টলেক আগে পুরো জঙ্গল ছিল। কেউ আসতে চাইত না।... আজকের এই উন্নতি মাড়োয়াড়িদের জন্যই। ৯০ শতাংশ কৃতিত্ব আমি মাড়োয়াড়িদের দেবো, ১০% বাঙালিদের"। তাঁর মতে, মাড়োয়াড়িরা আসার পরপরই সল্টলেকে রেস্তোরাঁ, শপিং কমপ্লেক্সের চাহিদা তৈরি হয় আর 'সিটি সেন্টার' তৈরি করে সেই চাহিদা মেটান হর্ষ নেওটিয়া - আরেক মাড়োয়াড়ি। অর্থাৎ সল্টলেকের গড়ে - বেড়ে ওঠার সঙ্গে তাঁর সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তা বাঙালি মানুক আর না মানুক।[৮]
সল্টলেকে ভাষা-ভিত্তিক আমরা-ওরার আলোচনা হল, এবার এই অঞ্চলে ধর্মভিত্তিক সামাজিক মেলামেশার পরিধিটা বোঝার চেষ্টা করি। নেহরুয় আধুনিকতায় আপাতভাবে ধর্মীয় পরিচিতির কোনো স্থান নেই। তবে আধুনিক শহরে ধর্মের স্থান কী এবং কতটা এই নিয়ে তরজা শুরু হয়েছিল ’৫০-’৬০-এর দশকেই। ইসলামাবাদ বা ভুবনেশ্বর প্রসঙ্গে এ নিয়ে আলোচনাও রয়েছে কিছু।[৯] গোড়ার সল্টলেকে মন্দির-মসজিদ কিছুই ছিল না। কিন্তু বছর বছর ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হতো। প্রায় সব বাড়িই তখন হিন্দু বাড়ি - সেখানে ভিত পুজো, গৃহপ্রবেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী পুজো, নানা হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান লেগেই থাকত। সল্টলেকে বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির দাপট ছিল বললে ভুল হয় না। হাতেগোনা কিছু মুসলমান পরিবার ছিলেন। কেমন ছিল তাঁদের দিনযাপন? এ প্রসঙ্গে একজনের অভিজ্ঞতা বলি। তাঁর নাম আদিল খান। ১৯৮২ সালে সল্টলেকে জন্ম তাঁর, বাবা ছিলেন সরকারী কলেজের অধ্যাপক। খুব আনন্দে কেটেছিল তাঁর শৈশব, কৈশোর। ছোটবেলার স্মৃতির অনেকটা জুড়ে রয়েছে তাঁর সল্টলেকে নাটক করা, ফুটবল খেলা, দুর্গাপুজোর সময়ে নানা হৈহৈ’র গল্প। মুসলমান পরিচিতিটা এই স্মৃতিচারণে গুরুত্ব পায়না তেমন, যতক্ষণ না সরাসরি আদিলকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। সরাসরি প্রশ্নের উত্তরে আদিল অনেককিছু বলেন, স্পষ্ট হয় সল্টলেকের আরেক চেহারাঃ
সল্টলেকে 'হারমোনি অ্যাসোসিয়েশন' বলে একটা মুসলিমদের অ্যাসোসিয়েশন ছিল, বাবা’রাই করেছিলেন। প্রতি মাসে কম্যুনিটি গেট টুগেদার হতো। বেশ কিছু মুসলিম পরিবার ছিলেন - যেমন ম্যাঙ্গালোর থেকে আসা এক চিংড়ির ব্যবসায়ী, অসমের এক পরিবার - সবাই গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিলেন - বাংলা নানা প্রান্ত এবং ভারতের নানা প্রান্তের মুসলমান পরিবার ছিল। বেশ কিছু আমলা ছিলেন। কেউ কেউ এঁরা লাবণী হাউসিং-এ থাকতেন। এই জমায়েতগুলো খানিকটা ধার্মিক খানিকটা সামাজিক জমায়েত হতো।... ৩টে বড় অনুষ্ঠান হতো, সাধারণত 'উন্নয়ন ভবন'-এর হল ভাড়া করে। দুটো ঈদের পর, একবার মিলাদ-উন-নবীর পর। 'উন্নয়ন ভবন'-এ একজন আমলা ছিলেন। পাড়ার দুর্গাপুজো বাদ দিয়ে এটা আরেকরকম মেলামেশার জায়গা ছিল।
আদিলের কথায় স্পষ্ট যে এই আরেকরকম মেলামেশায় বাঙালি পরিচিতির তেমন গুরুত্ব নেই - সহজেই ভারতের নানাপ্রান্তের মানুষ এখানে অংশ নিতে পারতেন। ধর্মই ঠিক করে দিত কে এই মেলামেশায় আসতে পারবেন কে পারবেন না।
এই 'হারমোনি অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্যদের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সল্টলেকে নমাজের জায়গা পান মুসলমানরা। আদিলের ছোটবেলায় জুম্মার নমাজ পড়তে বা ঈদের নমাজ পড়তে সল্টলেকের মুসলিম বাসিন্দাদের যেতে হতো বেলেঘাটা ই.এস.আই. হাসপাতালের পিছনে। সল্টলেকে কোনো জায়গা ছিল না। নানা মুসলিম আমলা চেষ্টা চরিত্র করেছিলেন - মসজিদ না হোক, নমাজ পড়ার একটা জায়গা দেওয়া হোক। কিন্তু জ্যোতিবাবুর সরকার রাজি হননি। তাঁদের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট - সল্টলেকে কোনো ধর্মের জন্যই কোনো জমি দেওয়া যাবে না। কিন্তু বছর বছর পুজো প্যান্ডেল অবশ্য চোখ এড়িয়ে যেত বামপন্থী সরকারের। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলে সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে একটা জায়গা দেওয়া হয়। তাঁর দুই ব্যক্তিগত সচিবই ছিলেন মুসলমান, সল্টলেকের বাসিন্দা। হয়তো তাঁদের প্রভাবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এখন অবশ্য বেশ কিছু মসজিদ ও নমাজ পড়ার জায়গা রয়েছে সল্টলেকে - 'বিকাশ ভবন'-এর ভিতরে আছে, 'আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়'-এর সল্টলেক ক্যাম্পাসে আছে, সংখ্যালঘু দপ্তরের অফিসে আছে।[১০]
নমাজ পড়ার জায়গা আছে, মসজিদ আছে - এসবই ঠিক, কিন্তু সল্টলেকের মুসলমানরা কি ভালো আছেন? আবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ফিরে যাই। ফ্ল্যাট কেনার প্রক্রিয়া চলাকালীন আবাসনের সেক্রেটারি ফোনে একদিন বললেন, “সবরকম সহযোগিতা করব, কোনো চিন্তা নেই। এখানে শুধু মুসলিম কাউকে বাড়ি বিক্রি করা বা ভাড়া দেওয়া নিয়ে একটু আপত্তি আছে, বুঝতেই পারেন, দিনকাল যা... থানা পুলিশের চক্করে পড়তে হয় যদি”। মুসলমান মানুষকে বাড়ি বিক্রি করলে বা ভাড়া দিলে থানা-পুলিশ কেন হবে, সে প্রশ্নের উত্তর আন্দাজ করতে পারি, কথা বাড়াই না। মনে পড়ে ২০২০ সালে ১০ জন মাদ্রাসা শিক্ষককে একটা হোটেল থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল এই সল্টলেকেই, ইসলামভীতি থেকে। 'প্রতীচী ট্রাস্ট'-এর গবেষক সবির আহমেদের কাছে শুনেছি আরেকটা একইরকম ঘটনা। তাঁর এক পরিচিত মুসলমান পরিবার সল্টলেকে বাড়ি ভাড়া পেয়েছিলেন। কথাবার্তা হয়ে যাওয়ার পর আচমকাই বাড়ির মালিক বেঁকে বসেন। সুদূর আফগানিস্তানে তালিবানরা ক্ষমতা পুনর্দখল করেছে শুনে তাঁর মনে হয় মুসলমান ভাড়াটে না রাখাই ভালো। সল্টলেক অবশ্য ব্যতিক্রম নয়। কলকাতার হাতেগোণা কিছু জায়গা ছাড়া সর্বত্রই মুসলমানদের বাড়ি কেনা বা ভাড়া পাওয়া খুব কঠিন, এ কথা একটু চোখ কান খোলা মানুষ মাত্রই জানেন।
তবে আজ সল্টলেকে দাঁড়িয়ে মনে হয় যে নেহরুয় আধুনিকতা উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিদ্বেষকে রুখে দেওয়ার যে স্বপ্ন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর কিছু অনুগামীরা দেখেছিলেন তা ছিল নিছকই অলৌকিক দিবাস্বপ্ন। সোজা সোজা রাস্তা, গোল চক্কর, নানা ব্লকে ব্লকে ভাগ করা আপাতভাবে গোটাটাই একইরকম এই সব শহর একইরকম নাগরিক তৈরি করবে - আধুনিকমনস্ক, নিয়মমাফিক, ভবিষ্যতমুখী - এমন আশা ছিল স্বাধীনতার পরপর অনেকের। প্রথম বাসিন্দার বসবাসের সময় থেকে ধরলে সল্টলেকের বয়স ৫০ পেরোলো। এই মুহূর্তে পিছন ফিরে তাকালে মনে হয় না পরিচিতির রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছে এই উপনগরী। এখনকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বললে এমন আশাও হয় না যে সেই লক্ষ্য পূরণ হবে অদূর ভবিষ্যতে কখনও।
তথ্যপঞ্জিঃ
১) ৫ম বাসিন্দা।
২) বিদ্যুৎ সংযোগ নম্বর অনুযায়ী ১২ নম্বর বাসিন্দা।
৩) এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন 'সল্টলেক আর্কাইভস'-এর পক্ষ থেকে শরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়। এটি 'সল্টলেক আর্কাইভস' ও 'ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ' কলকাতার একটি উদ্যোগ। এখানে আপাতত রয়েছে শতাধিক সল্টলেক বাসিন্দার সাক্ষাৎকার, পুরোনো ছবি, খবরের কাগজ, ম্যাপ ও সল্টলেক বিষয়ক বই ও রিপোর্ট। বিশদে জানতে দেখুন - https://idsk.edu.in/salt-lake-archives/ ও https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4116445.
৪) https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/salt-lakes-marwari-community-to-support-tmc/articleshow/49038915.cms
৫) সূত্রঃ স্বাতী মন্ত্রী, Marwaris of Kolkata: Community, Identity and City, Unpublished Dissertation, IIT Delhi, 2019, http://hdl.handle.net/10603/443462, পৃঃ ৭৮।
৬) এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন 'সল্টলেক আর্কাইভস'-এর পক্ষ থেকে বর্ষণা বসু।
৭) এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন 'সল্টলেক আর্কাইভস'-এর পক্ষ থেকে শরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়।
8) এই অংশটি লেখা হয়েছে স্বাতী মন্ত্রীর উপরোক্ত গবেষণার উপর ভিত্তি করে। বিশেষ করে তাঁর প্রথম ও তিন নম্বর চাপ্টার দেখুন।
৯) দেখুন Markus Daechsel, ‘Seeing like an expert, failing like a state? Interpreting the fate of a satellite town in early post-colonial Pakistan’ in Maussen, Bader and Moors (Eds), Colonial and Post-Colonial Governance of Islam: Continuities and Ruptures, University of Amsterdam Press, Amsterdam, 2011, pp 155-174; Ravi Kalia. “Cityscapes.” India International Centre Quarterly, vol. 33, no. 3/4, 2006, pp. 140-49. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/23006076. Accessed 1 Dec. 2023.
১০) আর আছে ফুটপাথে ফুটপাথে অজস্র মন্দির। চোখ সয়ে গেছে এত যে আলাদা করে খেয়াল থাকে না কেমনভাবে একটা ধর্ম রাস্তা দখল করে চলেছে অবিরাম।