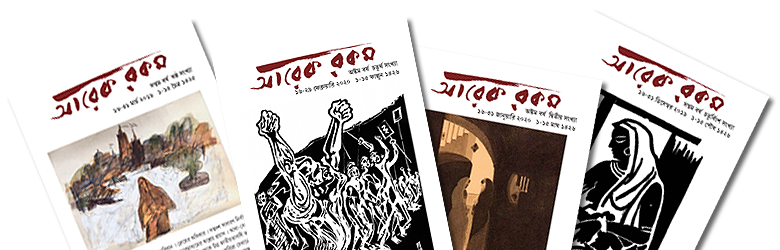আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ ত্রয়োদশ সংখ্যা ● ১-১৫ জুলাই, ২০২৪ ● ১৬-৩১ আষাঢ়, ১৪৩১
প্রবন্ধ
তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রদ্ধাস্পদেষু
শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়
আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের নয়। মেরেকেটে বছর দশেকের। ২০১৪ সালে আমাদের ‘কোমল গান্ধার’ পত্রিকার প্রথম বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেবার ছিল 'সুবিমল লাহিড়ী সংখ্যা'। আপনি কোনো সূত্রে জানতে পেরে পত্রিকা কিনেছিলেন। তারপর সুনন্দন চক্রবর্তী আমায় চেনেন জেনে তাঁকেই ফোন করে বলেন ‘কোমল গান্ধারে’র সম্পাদকের সঙ্গে আপনি দেখা করতে চান। এভাবেই একদিন সুনন্দনদার বাইকে চেপে হাজির হয়েছিলাম আপনাদের বোসপুকুরের ফ্ল্যাটে। তখন আমার বেজায় সংকট চলছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আর দেশভাগ সংক্রান্ত একটা লেখা নিয়ে। গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিস নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি। আর বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে তীরে ভিড়বার চেষ্টা চালাচ্ছি। আপনি দু-চার কথায় প্রথম দিনই আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। তখনই আপনার সুবিদিত উইটের কথা জেনেছিলাম। যা পরবর্তী বছরগুলোতে অপ্রকাশ্য থাকেনি।

সুবিমল লাহিড়ীকে আপনি চিনতেন ১৯৬৪ সালের আগে থেকেই। সেবছর আপনার এম.এ. শেষ হয়েছিল। সম্ভবত সুবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে কয়েকবার গিয়েছিলেন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর মূল বাড়ির সংলগ্ন 'রমেশ ভবন'-এ। সেখানে তখন ‘ভারতকোষ’ প্রকাশের তোড়জোড় চলছে। ১৯৬৪-তেই প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ‘ভারতকোষ’-এ প্রকাশন সহকারী হিসেবে কাজ করতেন সুবিমল লাহিড়ী এবং আপনার বাল্যবন্ধু বিমান সিংহ। সুবন্ধু ভট্টাচার্য, বিমান সিংহ আর আপনি ছাত্রাবস্থায় একটি ক্ষণজীবী লিটল ম্যাগাজিন বের করতেন। ‘বক্তব্য’ নামে সেই পত্রিকা আমি কখনও চোখে দেখিনি, কিন্তু শুনেছি তাতে কমলকুমার মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদারের লেখা ছাপা হয়েছে। এম.এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর যখন চাকরি খুঁজছেন সেসময় সুবীরবাবু আর বিমান সিংহের উৎসাহে আপনি ‘ভারতকোষ’-এ পার্ট টাইম চাকরি পেলেন। ততদিনে ‘ভারতকোষ’-এর রপ্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, দ্বিতীয় খণ্ড ছাপার কাজ শেষ, তৃতীয় খণ্ডের লেখা আসা শুরু হয়েছে। আপনার প্রাথমিক কাজ ছিল সুবীরবাবুর সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য শুদ্ধিপত্র তৈরি করা। পরে সুবিমল লাহিড়ী আর বিমান সিংহের সঙ্গে তৃতীয় খণ্ডের প্রুফ দেখার কাজও করেছেন। সেই সুবিমল লাহিড়ীকে নিয়ে আমাদের সংখ্যা হাতে পেয়ে আপনি স্বাভাবিকভাবেই নস্ট্যালজিক হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আপনার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে খুব অল্প সময়েই নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছিলেন।
সুবিমল লাহিড়ীকে একদিন দেখতে যেতে চেয়েছিলেন। আমি নির্দিষ্ট দিনে পদ্মশ্রী সিনেমা হলের সামনে সময়ের আগেই গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। চোখ ছিল ট্যাক্সির দিকে। কিন্তু খানিকবাদেই বাটার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল গড়িয়াগামী একটা বাস, আর তা থেকে নেমে এলেন আপনি। ঋজু, মুখে স্মিত হাসি। ‘সুবিমলবাবু’র সঙ্গে সেদিন প্রায় তিন দশক পরে আপনার দেখা হল। তারপর দুই বন্ধুকে পুরোনো দিনের গল্পে মাতোয়ারা হয়ে যেতে দেখাই আমার একমাত্র ভূমিকা ছিল। ফেরার সময় আর রিক্সায় না উঠে আপনার সঙ্গে হেঁটেই বাস রাস্তা অব্দি এলাম। আপনি ফের গড়িয়াহাটমুখী একটা বাসে উঠে বাড়ির দিকে গেলেন। এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে আপনাকে বাড়িতেও কোনোদিন ঘরের পোশাকে দেখিনি। সব সময় শার্ট-প্যান্ট, একবার শীতকালে পাঞ্জাবির ওপরে শাল জড়িয়ে বসে থাকতে দেখেছি। একইরকমভাবে আপনাকে কখনও বাঙালি-সুলভ পরনিন্দা করতে দেখিনি। তাই বলে পরচর্চা কোনোদিন আপনার সঙ্গে করিনি তা নয়, কিন্তু সবটাই শোভন ভঙ্গিতে, নির্মল কৌতুক মিশিয়ে।
আপনার নির্দেশে আমার প্রথম কাজ সম্ভবত ‘সারা দুনিয়ার সেরা গল্প’ বইয়ের জন্য। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার যৌথ সম্পাদনা। দুই খণ্ডে ‘সারা দুনিয়ার সেরা গল্প’-এর পরিচিতির পাতায় লেখা আছে - "বত্রিশটি দেশের ছাপ্পান্নজন গল্পকারের গল্প, ছাপ্পান্নরকম স্বাদের। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, দুই আমেরিকা, ওশিয়ানিয়া, কোথায় বিছানো নেই গল্পের মায়াজাল? সেইসব মহাদেশই হাজির এই ছোটোগল্পের সংগ্রহে। বাংলা অনুবাদে।" প্রায় ছ-মাস ধস্তাধস্তি করে আমি ফ্রাঙ্ক ও’কোনর-এর একটা গল্প ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করলাম। আপনি ছ-মাসে দু-বারের বেশি জিগ্যেস করেননি কতটা এগোল। আপনার আস্থাও বড়ো সহায়ক ছিল সেই অনুবাদ শেষ করায়। বই বেরোনোর পর প্রথম খণ্ডের প্রথম গল্পটাই আমার অনুবাদ করা দেখে আমি পুলকিত হয়ে পড়ছি বুঝে আপনি মজার ভঙ্গিতে বললেন, এতে অনুবাদকের কোনো কৃতিত্ব নেই, ফ্র্যাঙ্ক ও’কোনর আয়ারল্যান্ডের লেখক হওয়ায় আমি অ-কারাদিক্রমের সুবিধে নিয়ে সবার মাথায় চড়ে বসেছি! সেদিন নিজের মূর্খামি ধরতে পেরে আপনার সঙ্গে আমিও খুব একচোট হেসেছিলাম।
এরপর দুটো কাজে আপনার সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা আর দেখা হতে লাগল। একটা আপনার নিজেরই উদ্যোগে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশি বছর বয়সে বন্ধুদের শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক ‘মানবেন্দ্র ২০১৮’ বইটির কাজ শুরু হয়েছিল কয়েক বছর আগেই। তাতে আমাকে একটা প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব দিলেও বইয়ের আকার-প্রকার নিয়েও বহুদিন আলোচনা করেছি। শেষমেশ মার্চ ২০১৯-এ বইটি প্রকাশিত হয়। ওদিকে ‘কোমল গান্ধার’-এর পরের সংখ্যা 'সুবীর রায়চৌধুরী বিশেষ সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হবে এটাও ঠিক করে ফেলেছিলাম ২০১৫ সালেই। প্রথম দিন থেকেই আপনি এ-কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নিজে একটা লেখাও দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে দফায় দফায় চলেছে আলোচনা। কাজ করতে করতে হাতে এসে গিয়েছিল সুবীরবাবুর অনেক চিঠি। তাঁর নিজের লেখা, তাঁকে লেখা - মোট চিঠির সংখ্যা কম নয়। কিন্তু চিঠি ছাপতে গেলে পুরোনো প্রসঙ্গ আর ব্যক্তি পরিচয়ের টীকা-টিপ্পনী দিতে হয়। চার-পাঁচ বছরের চেষ্টায় সেকাজও করা গিয়েছিল। সুবীর রায়চৌধুরী সংখ্যার কাজে আপনি অভিভাবকের মতো পাশে থেকেছেন। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সুবীরবাবুর নিকট বন্ধু। তাই তাঁর একটি লেখা বা সাক্ষাৎকার সেই সংখ্যায় রাখতে আমরা মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখনই বেশ অসুস্থ। তিনবারের চেষ্টাতেও আমরা ছাপার উপযোগী কিছু তৈরি করতে পারিনি। একবার আপনিও সঙ্গে গিয়েছিলেন। যদি পুরোনো প্রসঙ্গ তুলে সুবীরবাবুকে নিয়ে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি জাগরূক করা যায়। আমাদের সে-চেষ্টাও ফলপ্রসূ হয়নি। আপনি চিঠির টীকা-টিপ্পনীর জন্য কয়েকটা সাদা পাতায় কিছু সূত্র লিখে রেখেছিলেন। সেই কাগজগুলো যে সে-কাজে বড়ো সম্বল ছিল সে-কথা বলাই বাহুল্য। পত্রিকার কাজ করতে কয়েক বছর লেগে যাওয়ায় সবাই এক সময় হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবছিলেন আর বুঝি ওই সংখ্যা বেরোবে না। কিন্তু আপনি জানতেন সেসময় সুবীরবাবু ছাড়া আমাদের মাথায় আর কিছু ছিল না। ২০১৯-এ পুজোর পর যখন পত্রিকা প্রকাশিত হল, আপনার হাতে দিয়ে বাড়ি চলে এসেছিলাম। কথা বিশেষ হয়নি। তারপর একদিন সকালে ফোন করে বললেন, এই পত্রিকা একটা বিমান সিংহের হাতে দিয়ে আসা উচিত। সম্পাদনা-প্রকাশনায় বিমান সিংহের ব্যুৎপত্তির কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা বুঝবেন এই কথার অর্থ। আপনি কোনোদিন বলেননি সংখ্যাটা ভালোলেগেছে কি না। কিন্তু আপনার সেই টেলিফোন কলে আমি বুঝে নিয়েছিলাম আপনার মনের কথা। তারপর একদিন নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন বিমানবাবুর বাড়ি।
আপনি ফোন করতেন হয় সকাল আটটা, নইলে বিকেল পাঁচটা নাগাদ। প্রথমে জিগ্যেস করতেন পেশাগত দু-একটা কথা। বিশেষ করে খাতা দেখার চাপ আছে কি না। তারপর মৃদু স্বরে কোনো পত্রিকার জন্য লিখতে বলতেন - সাধারণ সংখ্যা হোক বা শারদ সংখ্যা। কখনো বিষয় বলে দিতেন, বেশিরভাগ সময়ে আমাকেই বলতেন কী লিখব তা ঠিক করে জানাতে। আমার নিজস্ব মুদ্রাদোষে আমি সব সময়েই লেখা দিতে দেরি করেছি। কিন্তু প্রত্যেকবারই সে-লেখা নির্দিষ্ট সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। একবার ‘আরেক রকম’ পত্রিকা নিয়ে কোনো কথা ওঠায় আপনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন - “অনেক দিন লেখা দিচ্ছ না ‘আরেক রকম’-এ”। আমার মতো তুচ্ছ কলমচিকে এভাবেই প্রশ্রয় দিয়েছেন আপনি।
এই বছর বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে ‘সাক্ষাৎ মানবেন্দ্র’ নামে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮টি সাক্ষাৎকারের একটি সংকলন। এক্ষেত্রেও মুশকিল আসান ছিলেন আপনি। কৌশল্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ই-মেল আইডি দিয়ে অনুমতি সংগ্রহ করতে বলেছিলেন। বইটি বেরুনোর পর গোটাটা পড়ে তিন শব্দে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন - "জরুরি কাজ হল"। আপনার মতো এত নিবিষ্ট হয়ে বই পড়তেও আজকাল কম মানুষকেই দেখি।
গত শীতে শুরু হয়েছিল আপনার জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে লেখা বই প্রকাশের আয়োজন। ‘উত্তরপ্রবেশের কবিতাঃ জীবনানন্দ ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৮’ বইটি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। কাজ যখন অনেকটাই এগিয়েছে তখন একদিন হঠাৎ ফোন করে বললেন - "বুঝলে, এবার থেকে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি বিভাগ আছে তারা মনে হয় আমাকে সেমিনারে ডাকবে"। আমি থই না পেয়ে বোকার মতো চুপ করে আছি দেখে আপনি জানালেন - " ‘উত্তরপ্রবেশের কবিতা’র বদলে প্রুফে নাকি ছাপা হয়েছে ‘উত্তর প্রদেশের কবিতা’!" তারপর একদফা হাসি-ঠাট্টা চলল।
আপনার সামনে বসে পুরোনো কলকাতার গল্প শুনতে ভালো লাগত। বিশেষ করে উত্তর কলকাতার গল্প। কিন্তু প্রথাগত আত্মজীবনী লিখতে আপনার খুব একটা আগ্রহ ছিল না। তাই ২০২৪-এর বইমেলায় ‘বইয়ের দোকান’ নিয়ে যখন ‘চমৎকার’ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশের সুযোগ হল তখন আপনাকে বলেছিলাম অল্প বয়সে কলকাতায় দেখা বইয়ের দোকানের স্মৃতি নিয়ে একটা লেখা দিতে। সে-লেখা আপনি লিখেছিলেন আশ্চর্য এক শিরোনামে - ‘বই! বই!! বই!!!’। বিধান সরণি আর রামদুলাল সরকার স্ট্রিটের মোড়ে আপনার ছোটোবেলায় ছিল 'বৈকুণ্ঠ বুক হাউস'। সেই দোকানের গোলাকার একতলার দরজার পাশের টিনে শব্দগুলো বড়ো বড়ো করে লেখা থাকত বিস্ময় চিহ্ন সহ।
গত সেপ্টেম্বরের এগারো তারিখে বোসপুকুরের বাড়িতে যেতেই হাতে দিয়েছিলেন একটি আশ্চর্য বই - ‘দ্য বেঙ্গলি বুক অফ ইংলিশ ভার্স’। কলেজ স্ট্রিট থেকে আমার জন্য এনে রেখেছিলেন। ১৯১৮-য় প্রথম প্রকাশিত থিয়োডর ডগলাস ডান সংকলিত বইটির বিশেষত্ব হচ্ছে এতে ‘Foreword’ লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা হয়েছে ‘স্যর রবীন্দ্রনাথ টেগোর’। আমি এমন বই এর আগে দেখিনি যাতে রবীন্দ্রনাথের নামের আগে ‘স্যর’ লেখা আছে।
গত কয়েক মাসে চিকিৎসার জন্য আপনাকে মাঝে-মাঝেই থাকতে হচ্ছিল রিজেন্ট এস্টেটের ঠিকানায়। সে-বাড়ির রাস্তার ধারের বারান্দায় সকালে-সন্ধেয় বেশ কয়েকবার আপনার সঙ্গে বসে থেকেছি। অল্প অল্প কথা বলেছেন। নতুন-পুরোনো বইয়ের কথা বলেছেন।
আপনার মনে হচ্ছিল জন্মশতবর্ষে সমরেশ বসুর গল্প নিয়ে নতুন করে লেখালিখি হওয়া দরকার। তাই আমাকে বলেছিলেন নতুন করে সমরেশের গল্প পড়তে। আমি পড়তে শুরুও করেছি, কিন্তু আপনি হাত ছাড়িয়ে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন। সমরেশ বসুকে নিয়ে আমাদের আলোচনাটা বাকি থেকে গেল। বাকি থেকে গেল বাংলা বানান আর প্রয়োগ নিয়ে আপনার অভিনব সব পর্যবেক্ষণ শোনা। প্রত্যেকবার ফোন রাখার আগে বলতেন, "সময় করে একদিন এসো"। বুঝতে পারছি এই শহরে কাছে ডাকার মতো মানুষের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে।
পুনশ্চঃ পরিচয় হবার পর আপনার লেখা বা সম্পাদিত বইগুলির কথা কোনোদিন নিজের মুখে বলেননি। আমি জানতাম 'সাহিত্য অকাদেমি' থেকে আপনার সম্পাদনায় প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক প্রবন্ধ সংকলন ‘অতীত তথা অনাগতের দাবি’ বইটির কথা, কিংবা 'ওয়েবকুটা' থেকে বেরোনো জীবনানন্দ বিষয়ক সংকলন ‘একদিন শতাব্দীর শেষে’র কথা। কিন্তু ভগৎ সিং-কে নিয়ে আপনার লেখা ‘ভগৎ সিং: শহিদ-এ-আজম’ বইটির কথা আমার জানা ছিল না। যেদিন সংবাদপত্রের পাতায় সে-তথ্য জানলাম তখন আর আপনাকে প্রশ্ন করার উপায় নেই।