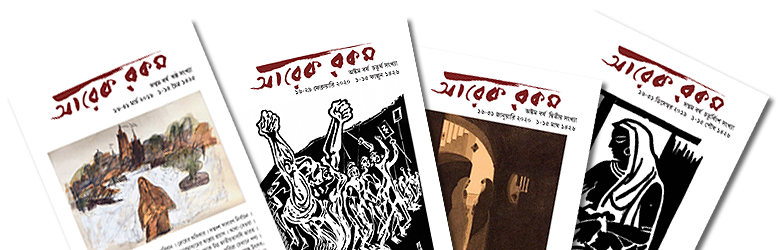আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ ত্রয়োদশ সংখ্যা ● ১-১৫ জুলাই, ২০২৪ ● ১৬-৩১ আষাঢ়, ১৪৩১
প্রবন্ধ
বামপন্থীরা বারবার শূন্য কেনঃ একটি অভিমত
শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার
প্রচারের জোশে খামতি ছিল না। ছিল না সামাজিক মাধ্যমে বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনার অভাব। একাধিক ঝকঝকে ভাবমূর্তির উজ্জ্বল নবীন প্রার্থীরাও ছিল। একটি সুসংহত জোটও তৈরি হয়েছিল। রাজপথে ছাত্র-যুবদের উদ্দীপ্ত করা লড়াই ছিল। উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গে সাড়া জাগানো ইনসাফ যাত্রা ছিল। অবিস্মরণীয় একটি ব্রিগেড সমাবেশ ছিল। উল্টোদিকে দুর্নীতির অভিযোগে জেরবার সরকার ছিল। জনমনে দুর্নীতি নিয়ে অসন্তোষও ছিল। কেন্দ্রের ইলেক্টোরাল বন্ড কেলেঙ্কারিও ছিল। তবু আবারও শূন্য বামপন্থীরা। কেন? ২০০৯ থেকে শুরু যে বিপর্যয়ের তাতে কিছুতেই লাগাম পরানো যাচ্ছে না। বামপন্থীদের বিপর্যয় বললে সাধারণভাবে সিপিআই(এম)-এর বিপর্যয়ের কথাই বোঝা হয়। বাকি বামপন্থীরাও যে এ রাজ্যে শূন্য সেটা বলাই বাহুল্য। সমস্ত নজর সিপিআই(এম)-কে ঘিরেই। কারণ সিপিআই(এম)-এর পুনরুত্থান ব্যতিরেকে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব।
কেন এই বিরামহীন পরাজয়ের ধারা? দল হিসেবে সিপিআই(এম), তাদের সমর্থক ও দরদীরা এই প্রশ্ন তুলবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সিপিআই(এম)-এর এই ধারা-পরাজয় বামপন্থার সামগ্রিক শক্তিহীনতাকে এতটাই প্রকট করেছে যে এই প্রশ্নটি উঠছে এখন সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে, এমনকী অন্য রাজনৈতিক শক্তির তরফেও। অমর্ত্য সেন থেকে অপর্ণা সেন বামেদের নির্বাচনী বিপর্যয়ে হতাশা ও দুঃখ ব্যক্ত করেছেন। হয়ত সকলের অচেতনে এই প্রশ্নটিই অনুরণন করছে, যা বলেছিলেন অধ্যাপক প্রভাত পট্টনায়ক। তিনি বলেছিলেন, এদেশে বামপন্থীদের কোনো ভবিষ্যৎ আছে কিনা সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল বামপন্থীদের বাদ দিয়ে এদেশের কোনো ভবিষ্যৎ আছে কিনা। বিজেপির আগ্রাসী নয়া উদারবাদ ও চরম সংখ্যাগুরুবাদী হিন্দুত্বের রাজনীতির বিকল্প হিসেবে এবারে নির্বাচনে যে রাজনীতিটি উঠে এসেছে সেটা এক ধরনের বামপন্থাই যেখানে মানুষের রুটি, রুজি ও সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন বড়ো হয়ে উঠেছে। বলতে দ্বিধা নেই, এই বিকল্প কন্ঠস্বরটি জোরালো করেছে একদিকে রাজধানীর উপকন্ঠে আছড়ে পড়া কৃষক সংগ্রাম ও রাহুল গান্ধীর দেশকে নাড়িয়ে দেওয়া দু’টি পদযাত্রা। একটি কথা স্মর্তব্য, এবারের নির্বাচন বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতিকে একটি ধাক্কা দিতে পেরেছে মাত্র, পরাস্ত করতে পারে নি। ফলে আহত শ্বাপদের মতই নতুন সরকার আরও হিংস্র হয়ে উঠবে আগামীদিনে, সেই ইঙ্গিত প্রথম দিন থেকেই স্পষ্ট। আশার কথা বিরোধীরা আগের মতো হীনবল নয়। আগ্রাসী শাসক ও শক্তিশালী বিরোধীপক্ষের এমন একটি যুদ্ধ পরিস্থিতি বামপন্থীদের জোরালো অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করে। কিন্তু বামপন্থীরা কিছুতেই সেই প্রত্যাশা পূরণের জায়গায় উঠে আসতে পারছে না। উল্টে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার লাগাতার পরাজয়ের ধারা অব্যাহত থাকার মধ্যেই কেরলের রাজনীতির আকাশেও সিঁদূরে মেঘ দেখা যেতে শুরু করেছে। কেরলে ২০২১-এর বিপুল জয়ের পর ২০২৪-এ ভোটপ্রাপ্তির হারে এতটা হ্রাস, পশ্চিমবঙ্গের ২০০৬-এর বিপুল বিজয়ের পর ২০০৯-এর বিপর্যয়ের স্মৃতিকে উসকে দিচ্ছে।
২০০৯ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের সমর্থনভিত্তিতে ভাঙনের শুরু। ২০১৯ থেকে শুরু শূন্য ফলাফল। প্রতিটি বিপর্যয়ের পর কারণ অনুসন্ধান সিপিআই(এম) দলীয় স্তরেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। ২০২৪-এর ফলাফলের পর সিপিআই(এ রাজ্য কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলের বাইরে থেকেও মতাভিমত গ্রহণের। কারণ সমস্যা যে শুধুমাত্র নির্বাচনী জয়-পরাজয় নয়, বরং আরও বড় সংকটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে সেটা সম্ভবত দলীয় নেতৃত্ব উপলব্ধি করছেন। ২০০৯ সালের বিপর্যয়ের পর সিপিআই(এম)-এর অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনায় বিরোধী দলের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র ও সরকারের জনমুখী উন্নয়নকামী কর্মসূচি সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের অপপ্রচারকে দায়ী করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, জনগন এই ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের শিকার হয়ে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। তখন সিদ্ধান্ত হয়েছিল আরও জোরালোভাবে সরকারি কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ও বিরোধীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে প্রচারকে জনগনের কাছে নিয়ে যাওয়ার। এর পরের দু’টি বছর প্রচারের মাত্রা আরও তীব্র করা হয়। স্মরণ করা যেতে পারে সিপিআই(এম) নেতা গৌতম দেব বিরোধীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নানা তথ্য-প্রমাণ সহ সংবাদমাধ্যমের সামনে নিয়ে আসেন। তবু ২০১১-র সার্বিক পরাজয়কে ঠেকানো যায় নি। দলের সমর্থনভিত্তিতে ভাঙন অব্যাহত থেকে যায়। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর দলের অভ্যন্তরে ব্যাপক আলাপ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে কিছুটা আত্মসমালোচনাও হয়। দলের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে নিচের তলায় ও কিছুটা মাঝের স্তরে বেনোজলের অনুপ্রবেশের কথা স্বীকৃতি পায় আলাপ আলোচনায়। তবে মূল অভিমুখ থেকে যায় বামফ্রন্টের সাফল্য ও জনমুখী কর্মসূচিকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে না পারার ব্যর্থতা ও বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের দিকে। তারপরও সংবাদমাধ্যমের পরিভাষায় যাকে বলা হয় ‘বামেদের রক্তক্ষরণ’ তা অব্যাহত থেকে যায়।
এর মধ্যেও ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোট জনসাধারণের মাধ্যমে বামপন্থীদের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের একটি পারসেপশন বা ধারণা জনগনের মধ্যে তৈরি হয়। সর্বভারতীয় কিছু সংবাদমাধ্যমও তখন বামপন্থীদের পুনরুত্থানের ইঙ্গিত দেয়। শেষ পর্যন্ত তৃণমূলই জয়ী হয়। সেই নির্বাচনের পর্যালোচনায় বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসে কংগ্রেসের সাথে জোটের সিদ্ধান্ত। জোটপন্থীরা জোটস্থাপনে বিলম্ব এবং জোটবিরোধীরা ‘সত্তরের দশকে পার্টি কমরেডদের রক্তমাখা’ কংগ্রেসের হাত ধরাকে বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে। ২০১৬-র নির্বাচনে বিজেপির ভোট ২০১৪ সালে যতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় ঠিক ততটাই হ্রাস পায়। কিন্তু ২০১৭ সালের পুর নির্বাচন ও ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের শাসক তৃণমূলের তরফ থেকে সংবাদমাধ্যম ও সাধারণ নাগরিক সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির উপর অভূতপূর্ব হিংসাত্মক আক্রমণ নেমে আসে। এর সরাসরি ফলশ্রুতিতে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এক গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায় নাগরিকদের ভোটদানের ক্ষেত্রে। পুর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসাত্মক ঘটনার মুখে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অক্ষম বামপন্থীদের সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করে তৃণমূলের অত্যাচারে অতীষ্ঠ বামপন্থী ভোটারদের বড় অংশটি ২০১৯-এ বিজেপির স্বপক্ষে ভোট দেয়। সংবাদমাধ্যম ও বিরোধীরা একে ‘বামের ভোট রামে’ বলে অভিহিত করে। বামপন্থীরা শুধু শূন্যই নয়, নির্বাচনী সমর্থনের নিরিখেও তৃতীয় শক্তিতে পরিণত হয়। সেই থেকে শূন্যের শুরু। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ও তাদের মূল নিয়ন্ত্রক আরএসএস উত্তর থেকে দক্ষিণে ডালপালা বিস্তার করতে শুরু করে। দেশভাগ ও উদ্বাস্তুদের দেশছাড়া হওয়াকে মূল উপজীব্য করে পশ্চিমবঙ্গের কোণে কোণে তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু করে সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন। তৃণমূল ও বামপন্থী উভয় রাজনৈতিক শক্তিকে মুসলিম তোষণকারী হিসেবে জনসাধারণ্যে তুলে ধরতে থাকে তারা। সাধারণ মানুষের মোবাইলে মোবাইলে ঘুরতে শুরু করে তাদের আইটি সেলের উস্কানিমূলক অর্ধসত্য ও মিথ্যা প্রচার। এই প্রচারের তীব্রতা এতটাই বেশি হয়ে ওঠে যে বহু বামপন্থী সমর্থক ও সাধারণ দলীয় সদস্যদেরও এর দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখা যেতে থাকে। ২০২১-এর নির্বাচনে তরুণ প্রজন্মের প্রার্থী মনোনয়ন ও কংগ্রেস ও আইএসএফ-এর সাথে জোটের মাধ্যমে বামপন্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও ফলাফল সেই শূন্যই থেকে যায়। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও সেই শূন্যই। এই নির্বাচনে বামপন্থীরা সারা রাজ্যজুড়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে তেমনটা হয়ত সিপিআই(এম) দলের তরফেও মনে করা হয় নি। শূন্য অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে জোর দেওয়া হয়েছিল মূলত পাঁচটি আসনে। তার মধ্যে দু’টি মাত্র আসনে বামপন্থীরা দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসতে সক্ষম হয়। এটা একটা উন্নতি হয়ত, কিন্তু যে দল একসময়ে রাজ্যের সিংহভাগ আসনে দীর্ঘদিন ধরে এক নম্বর স্থানে স্থিত থেকেছে তাদের জন্যে একে সাফল্য বলে অভিহিত করাটা কাম্য নয়। বরং নজর দেওয়া উচিত আরও গভীরতর অনুসন্ধানে কেন এই দুরবস্থা বামপন্থীদের? এটা কি শুধুই নির্বাচনী কৌশল বা সাংগঠনিক পরিচালনায় পেশাদারী দক্ষতার অভাবের জন্যে? নাকি নানা সাংগঠনিক, রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে এর জন্যে? প্রকৃত আত্মসমালোচনা ও আত্মসমীক্ষা ব্যতিরেকে যা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ নাটকে শেষ দৃশ্যে রাজাকেও দেখা যায় নন্দিনীদের সাথে যোগ দিয়ে দুর্গের প্রাকার ভাঙায় যোগ দিতে। নাটকের এই অংশটি অনেক বামপন্থীদের মনে ধন্দ জাগায়, এর অর্থ কী? নিজের বিরুদ্ধে লড়াই দিয়ে শুরু না করলে যে কোনো লড়াইই সার্থকতায় পৌঁছয় না রবীন্দ্রনাথ হয়ত সেই জীবনসত্যের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।
পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের আত্মসমীক্ষা শুরু হতে হবে প্রতিটি স্তরের কর্মী ও নেতাদের ব্যক্তিগত স্তর থেকে নিজের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার মনোভাব অর্জন করা থেকে। নিজেকে প্রশ্নের উর্ধে রেখে এই পর্যালোচনা সম্ভব নয়। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে এমন দৃষ্টান্ত অবশ্যই রয়েছে। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে রণদিভের নেতৃত্বে যে হঠকারিতা ও বামপন্থী বিচ্যুতির পথ গ্রহণ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে রণদিভে নিজেই পরবর্তী সময়ে একটি পার্টি কংগ্রেসে নিজের কঠোর আত্মসমালোচনা করেন। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা গেছে বড় ধরনের বিপর্যয়ের পর পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বে ব্যাপক রদবদল ঘটে। এক নাগাড়ে ৩৪ বছর রাজ্যের ক্ষমতায় থাকার পর ২০১১ সালে বামফ্রন্টের যে পরাজয় ঘটে তারপর বামপন্থী দলের ভেতরে সেই ধরনের মন্থন প্রক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় নি। সম্ভবত পার্টি সংগঠন পরিচালনাগত ত্রুটি, নিচের তলার সদস্য ও মাঝের স্তরের নেতৃত্বের কিছু অংশে দুর্নীতি ও ত্রুটি বিচ্যুতিকেই ২০১১ সালের ফলাফলের কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রাম বা আরও কিছু কিছু সরকারি সিদ্ধান্ত রূপায়নে আরেকটু ধৈর্যের প্রয়োজন ছিল এর চেয়ে গভীরতর আত্মানুসন্ধান উঠে আসেনি বামপন্থীদের আত্মসমীক্ষায়। অর্থাৎ সরকার বা দল, সবক্ষেত্রেই কিছু পরিচালনগত ত্রুটিকেই ২০১১ সালের ফলাফলের জন্যে প্রধানত দায়ী করা হয়। এই ঘটনাকে নির্বাচনী পরাজয় ছাড়া বাড়তি কোনো রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক বিপর্যয় হিসেবে দেখা হয়নি। ফলে সংশোধনের অঙ্গ হিসেবে সাংগঠনিক স্তরে শাখা ও জেলা কমিটির মধ্যবর্তী স্তরে থাকা লোকাল কমিটি ও জোনাল কমিটির প্রথা তুলে দিয়ে 'এরিয়া কমিটি' নামে নতুন একটি স্তর নিয়ে আসা হয়। এই পর্যায়ে সমালোচনা বা আত্মসমালোচনা যা হয়েছে, সবই হয়েছে দলের অভ্যন্তরে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে অভ্যন্তরীণ সম্মেলনের প্রতিবেদনে।
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর এই সাময়িকীতেই আমার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে বামপন্থীদের বিপর্যয়ের মূল কারণ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর একটি সময়পর্বের পর থেকে ক্রমান্বয়ে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। এই বিষয়টি শুধুমাত্র সিপিআই(এম)-এর জন্যে সত্য নয়। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শোভনলাল দত্তগুপ্ত বাম শাসনের অবসানের পর একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, সারা বিশ্বজুড়েই এটা একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা যে ক্ষমতায় যাওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জনগনের যোগসূত্র ক্রমে ছিন্ন হতে থাকে। কেন্দ্রীভূত সাংগঠনিক কাঠামোর ফলে বেশিরভাগ সময়ই এই বিচ্ছিন্নতা ঘটতে থাকার বাস্তবতাটি পার্টি নেতৃত্বের নজরে আসে না। একটা সময়ে এই বিচ্ছিন্নতা বাড়তে বাড়তে জনগনের মধ্যে প্রত্যাখানের মানসিকতার সৃষ্টি করে এবং তখন উপযুক্ত বাহন পেলে মানুষ কমিউনিস্টদের ক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে ফেলে। তিনি বলেছেন, এটা একটা তাত্ত্বিক সংকট। কমিউনিস্ট সাহিত্যে ক্ষমতা দখলের নানা পন্থা নিয়ে যতটা চর্চা দেখতে পাওয়া যায়, ক্ষমতায় যাওয়ার পর জনগনের সাথে দৈনন্দিন স্নায়ুর বন্ধনটি কীভাবে কমিউনিস্ট পার্টি জীবন্ত রাখা যেতে পারে তা নিয়ে চর্চা ততটা নেই। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার বিপর্যয় ও পূর্ব ইউরোপ বা সোভিয়েতে কমিউনিস্টদের পতন এখানেই এসে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে যায়। জনগনের বিপুল সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া, ক্ষমতায় যাওয়ার পর ক্রমে জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া - এটা কোনো স্থান বিশেষের সমস্যা নয়, এটা কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ সাংগঠনিক কাঠামোর ধরন থেকে জন্ম নেওয়া একটি সমস্যা। তর্কের খাতিরে কেউ বলতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরা কোনো বিপ্লবী রাষ্ট্র কায়েম করেনি। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে একটি অঙ্গরাজ্যে বুর্জোয়া সংবিধানের অধীনস্থ একটি সরকার গঠন করেছে মাত্র। এটা সত্যি হলেও সরকার পরিচালনার থেকে শুরু করে সামাজিক সংগঠন, ক্লাব, লাইব্রেরি, সমবায় সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল কলেজের ম্যানেজিং কমিটি, পাড়ার বিবাদের মধ্যস্ততা - সর্বক্ষেত্রে পার্টির সর্বাত্মক প্রাধান্য স্থাপন করতে গিয়ে প্রতাপসর্বস্বতার শিকার হয়ে পড়ার ধরনটি পূর্ব ইউরোপ বা সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্মধারারই অন্ধ অনুকরণের ফল। ওইভাবে পার্টিরাষ্ট্র এবং পার্টিসমাজ গড়ে তোলার জন্যেই যে মূলত সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপে নানা ধরনের বিচ্যুতি আত্মপ্রকাশ করার ফলেই যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পতন ঘটেছিল, সেটা সিপিআই(এম)-এর নথিতে বা কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অনেকের লিখিত নিবন্ধে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর এই সমালোচনামূলক সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছিল ন'য়ের দশকেই, অথচ নিজেদের সরকার বা দল পরিচালনার ক্ষেত্রে এর থেকে কোনো শিক্ষা নেওয়া হয়নি। ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর যে বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীণ প্রশাসনিক পরিচালনার পত্তন হয়, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিখ্যাত বামপন্থী কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায় তখন ‘আজকাল’ পত্রিকার একটি নিবন্ধে বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে। প্রকৃতপক্ষেই 'গ্রামসভা'র ধারণাটি অনেকটাই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আদলেই তৈরি। কিন্তু কেন্দ্রীভূত দলীয় সাংগঠনিক কাঠামোর দ্বারা পরিচালিত এই গ্রামসভাও পরবর্তীতে পার্টিসভার সিদ্ধান্ত অনুমোদনের যান্ত্রিক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। জনগন যে উৎসাহ নিয়ে তাতে অংশ নিত, সেখানেও ভাঁটা পড়ে। পরে গ্রামসভা কার্যত উঠে যায়। জনবিচ্ছিনতার এই একই কারণে পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরায় ক্ষমতা থেকে বামফ্রন্টের বিদায় হয়েছে। এমনকী এবারের নির্বাচনে কেরলের ফলাফলে যে সিঁদূরে মেঘ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার কারণও এই সাংগঠনিক সমস্যার মধ্যেই নিহিত। বিপুল জনসমর্থনের মধ্যেও নীরবে জনবিচ্ছিন্নতা ঘটে যাওয়া, একটি সংগঠনকেন্দ্রিক তাত্ত্বিক সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যাকে এড়িয়ে গেলে ক্ষতিই হবে আখেরে।
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর এই সাময়িকীতেই আমি নিম্নলিখিতভাবে বিষয়টির উল্লেখ করেছিলামঃ
“বামেরা ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসেছিল মূলত জনগনের দু’টি অংশের মধ্যে শক্তিশালী গণভিত্তির সুবাদে। এই দু’টি অংশ উদ্বাস্তু সমাজ ও কৃষক জনসাধারণ। স্বাধীনতার পর থেকেই দেশভাগের বলি হয়ে আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিল বামপন্থীরা। এই দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ফলেই উদ্বাস্তুদের মধ্যে বামপন্থীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে অবিভক্ত বাংলার কৃষক আন্দোলনের পরম্পরায় ছ'য়ের দশকের বেনামী ও খাস জমি দখলের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সমাজের মধ্যে বামপন্থীদের শক্তিশালী গণভিত্তি গড়ে ওঠে। বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলার পঞ্চায়েতগুলিতে বাস্তুঘুঘুর বাসা ভেঙে গরিবের ক্ষমতায়ন হয়। ওই সময়পর্বেই 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচির মাধ্যমেও কৃষকদের অধিকারের সীমা সম্প্রসারিত হয়। বামপন্থীরা কৃষকদের মধ্যে দুর্ভেদ্য শক্তি হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়ায় গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতে গরিব কৃষক ক্ষেতমজুরদের ক্ষমতায়ন ঘটলেও কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বে কৃষক সমাজের দরিদ্রতর অংশের মানুষদের তুলে আনা সম্ভবপর হয়নি। বরং ন'য়ের দশকে এসে দেখা গেল গ্রামে যাদের জমি বর্গা হয়েছে সেই ধনী কৃষকরাই সাধারণভাবে কৃষকসভার সাংগঠনিক নেতৃত্বে। ২০০৬ সালের পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে উদ্বাস্তু সমাজ ও গ্রামীন কৃষকদের মধ্যে বামপন্থীদের সমর্থন ভিত্তির ক্ষয় স্পষ্ট হতে থাকে এবং সেই জায়গা দখল করে নেয় তৃণমূল। ২০১১ সালে বামফ্রন্টের বিদায় সুনিশ্চিত হয় মূলত এই দু’টি অংশের সাথে বামপন্থীদের সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতার ফলেই। বিগত ১০ বছরে বামপন্থীদের এই পরম্পরাগত সমর্থন ভিত্তির পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়নি। ...ন'য়ের দশকের পর থেকে কৃষক আন্দোলন বা সামগ্রিকভাবে কৃষির বিষয়টি কোন পথে এগোবে এ নিয়ে স্পষ্টতা ছিল না। ২০১১ সালে ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পরও তৃণমূল সরকারের নতুন কৃষি আইন নিয়ে বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৃষক সমাজের নতুন নতুন সমস্যাকে কৃষক আন্দোলনে তুলে আনা সম্ভবপর হয়নি। এমনকী সাম্প্রতিক সময়ে সারা দেশে তিনটি কৃষি আইন নিয়ে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠলেও এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে উল্লেখযোগ্যভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়নি। অন্যান্য রাজ্যে পিছিয়ে পরা সমাজের মানুষের সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে পৃথক গণসংগঠন বা কৃষকসভার বাইরে ক্ষেতমজুরদের জন্যে আলাদা গণসংগঠন তৈরি হলেও পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বাম শাসনের ৩৪ বছরে। ফলে অনুসূচিত জাতি, উপজাতিদের পরিচিতি সত্তার আর্তি অথবা কৃষক সমাজের মধ্যেকার দরিদ্রতম অংশের কন্ঠস্বর স্বতন্ত্র স্বীকৃতি পেলো না বামপন্থী রাজনীতিতে। ন'য়ের দশক থেকে কৃষক সংগঠনের গুরুত্ব কমে এলো বামপন্থী রাজনীতির সামগ্রিক পরিসরে। অন্য রাজ্যে কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বে ছাত্র-যুব সংগঠকদের নিয়ে আসার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বের স্তরে তারুণ্যের অভিষেক ঘটানো হয়নি। ন'য়ের দশকের শেষ থেকেই গ্রামীন সমাজের দরিদ্রতর অংশের সাথে কৃষক সভার সংযোগ দুর্বল অথবা যান্ত্রিক হয়ে গেল। গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক সংগঠন হয়ে পড়ল কার্যত সরকারি ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।”
স্বাধীনতার পর থেকে বামপন্থীদের নেতৃত্বে উদ্বাস্তু আন্দোলন গড়ে উঠেছে মূলত পুনর্বাসনের প্রশ্নকে ঘিরেই। কলোনির স্বীকৃতি, পাট্টা প্রদান ইত্যাদিই ছিল মূল দাবি। ২০০৩ সালে বাজপেয়ী সরকারের উদ্যোগে নাগরিকত্ব আইনের যে সংশোধনী নিয়ে আসা হয় তার ফলে উদ্বাস্তু সমাজের সামনে নাগরিকত্বের প্রশ্নটিই হয়ে ওঠে প্রধানতম উদ্বেগের বিষয়। এই সংশোধনীতে ‘অবৈধ অনুপ্রবেশকারী’-র ধারণাকে নাগরিকত্ব আইনে যুক্ত করে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে কঠিনতর করার মাধ্যমে নাৎসী নাগরিকত্ব আইনের মতো করে বংশসূত্রে নাগরিকত্বের ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে এক বিশাল অংশের উদ্বাস্তু পরিবারের সদস্যদের নাগরিকত্ব সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মুখে এসে দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতের নাগরিকত্ব আইনের সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক এই সংশোধনীটি সংসদে পাশ হয়েছিল সর্বসম্মতিতে। বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন ১৯৯৯ সালের এনডিএ সরকার আসামের তৎকালীন রাজ্যপাল এস. কে. সিনহার অনুপ্রবেশ সম্পর্কিত একটি ভিত্তিহীন রিপোর্টকে সম্বল করে সুপরিকল্পিতভাবে অনুপ্রবেশ নিয়ে সারা দেশে আতঙ্ক সৃষ্টি করে জাতীয় নাগরিক পঞ্জী তৈরিকে আড়াল হিসেবে রেখে ভবিষ্যতের ধর্মীয় বিদ্বেষের রাজনীতির বীজ বপন করে ওই সংশোধনীর মাধ্যমে। বলতে দ্বিধা নেই বামপন্থীরাও সেদিন এই বিপদের দিকটি উপলব্ধি করতে পারেনি। এনডিএ মন্ত্রীসভার সদস্য হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থক। সিপিআই(এম)-এর চক্রান্তে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গেছে এই অভিযোগ তুলে তিনি লোকসভা অধ্যক্ষের মুখে একতাড়া কাগজপত্রও ছুঁড়ে মেরেছিলেন। পরে পরিস্থিতি আঁচ করে তিনি একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে মতুয়াদের বড়মা বীণাপাণিদেবীর সঙ্গী হয়ে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত লড়াইয়ের শরিক হয়ে গেলেন। এভাবে উদ্বাস্তুদের মধ্যে বামপন্থীদের পরম্পরাগত সমর্থনভিত্তি ধ্বসে গিয়ে সেখানে প্রথমে ঢুকল তৃণমূল। পরে ২০১৯-এর নির্বাচনে উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রধান শক্তিতে পরিণত হয় বিজেপি। বিগত ১৩ বছরে যতই সাংগঠনিক পর্যালোচনা বা সম্মেলনগুলিতে সমালোচনা আত্মসমালোচনা হোক, কৃষক সমাজ ও উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর সাথে যোগসূত্র পুনঃস্থাপন কিছুতেই করে উঠতে পারেনি বামপন্থীরা। উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও মহারাষ্ট্রে শক্তিশালী কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠলেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বামপন্থীরা এর ন্যূনতম প্রভাবও ফেলতে পারেনি। অন্যদিকে নাগরিকত্ব নিয়ে উদ্বাস্তুদের সাথে ধারাবাহিকভাবে তঞ্চকতা করে এসেছে এই সময়পর্বে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তা সত্ত্বেও সিএএ, এনআরসি-র প্রশ্ন উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিজেপির মুখোস উন্মোচন করার মতো আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়নি বামপন্থীরা। ২০২৪-এর নির্বাচনে বিজেপির আসন সংখ্যা কমে গেলেও উত্তরবঙ্গের সমস্ত শহরাঞ্চল সহ পশ্চিমবঙ্গের শহর অঞ্চলে ব্যাপক সমর্থন বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে। এটা ঘটেছে মূলত উদ্বাস্তু প্রাধান্যের শহরাঞ্চলে। এর পেছনে রয়েছে বিজেপির দেশভাগ নিয়ে সামাজিক গণমাধ্যম ও সমাজের নানা পরিসরে নিরন্তর প্রচার। এটাও প্রকৃতপক্ষে বামপন্থীদেরই ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতা উত্তর সময়ে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যেহেতু ভোটের বিচারে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার কোনো অস্তিত্ত্ব নেই। স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে হিন্দু মহাসভা ও জনসঙ্ঘ পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর অভিভাবকহীন হিন্দু মহাসভাপন্থীরা এন. সি. চ্যাটার্জীর অনুগামী হয়ে দলে দলে কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে শামিল হয়। রাম চ্যাটার্জীর মত সরাসরি মুসলিম হত্যায় জড়িত থাকা মানুষেরা কেউ কেউ সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ না দিয়ে অন্য বামপন্থী দলে যোগ দিয়ে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে চলে আসে। দেশভাগ ও মহাত্মা গান্ধী নিয়ে হিন্দু মহাসভা ও কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিকভাবেই স্বতন্ত্র। কিন্তু যেহেতু দেশভাগের রাজনীতির চর্চা কমিউনিস্ট পার্টির দৈনন্দিন মতাদর্শগত অনুশীলনের অংশ কখনওই ছিল না, ফলে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমাজ ও বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী সমর্থকদের একটি বড় অংশের মধ্যেও দেশভাগজাত মুসলিম বিদ্বেষ, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ঘৃণা সুপ্ত অবস্থায় ছিল দীর্ঘদিন, যা বিজেপি-আরএসএস-এর প্রত্যক্ষ উস্কানিতে এখন অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানির সমাজকে নাৎসী ভাবাদর্শ থেকে মুক্ত করার ‘ডিটক্সিফিকেশন’ বা নেশামুক্তির যে রাজনৈতিক উদ্যোগ ছিল, দেশভাগ উত্তর সময়ে সেরকম কর্মসূচি গ্রহণকে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনীতিতে কখনওই প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে দেশভাগের রাজনৈতিক ছায়া যে এতটা প্রলম্বিত হয়ে ৭৫ বছর পরও দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে কোনও ধারণা ভারতের কোনও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তিরই ছিল না। সারা দেশে সার্বিকভাবেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক সক্ষমতাকে ছোট করে দেখা হয়েছে স্বাধীনতা উত্তর কালে।
আরেকটি ভ্রান্তিকর ধারণা পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বাম রাজনীতির অভিমুখ নির্মাণকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। মূলধারার বামপন্থীরা মনে করেন পশ্চিমবঙ্গে জাতিগত নিপীড়ন বা বৈষম্যের কোনো স্থান নেই। জাতপাতভিত্তিক রাজনীতিকে নিরুৎসাহিত করতেই সম্ভবত জ্যোতি বসু একদা মন্তব্য করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে জাতপাতের সংঘাত নেই, শ্রেণি সংঘাত রয়েছে। এই মন্তব্য যখন করেন তিনি তখনও পরিচিতিসত্তার সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক স্বীকৃতির লড়াই বামপন্থার লড়াইয়ে অঙ্গীভূত করে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। ফলে পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক ন্যায় ও আত্মপরিচিতির আকাঙ্ক্ষা ও তার জন্যে রাজনৈতিক লড়াই উপেক্ষিত হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীগুলিকে সামাজিক ন্যায়ের সংগ্রামে সংগঠিত করার লক্ষ্যে পৃথক গণসংগঠন তৈরি করাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শুধু সামাজিক সংগ্রাম নয়, ক্ষেতমজুরদের আলাদা সংগঠনের আওতায় আনার কথাও উপলব্ধিতে আসেনি ৩৪ বছরে। সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগনের লড়াইয়ে বামপন্থীদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মতাদর্শগতভাবে চূড়ান্ত উচ্চবর্ণবাদী বিজেপি এই শূন্যস্থান দখল করে। পশ্চিমবঙ্গের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও বাঙালি জাতিকে একাকার করে দেখার প্রবণতাও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলিকে বামপন্থীদের থেকে দূরে ঠেলেছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতির দাবি উঠলেই তাকে পৃথকত্ববাদ বলে দেখে ‘কোনো অবস্থাতেই বাংলা ভাগ হতে দেবো না’ ধরনের উত্তর দিলে এর মধ্যে বাঙালি আধিপত্যবাদের বিপদ দেখতে পায় অন্য জনগোষ্ঠীগুলি, এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার ফলেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠী থেকে দূরত্ব রচিত হয়েছে। এই বিষয়গুলিই ন'য়ের দশক থেকে বিভিন্ন অংশের জনগন থেকে বামপন্থীদের দূরত্ব রচনা করেছে।
এর বাইরে ২০২৪-এর নির্বাচনে আলাদা করে ভূমিকা রেখেছে হাইকোর্টের দু’টি রায়। সাম্প্রতিক সময়কালে হাইকোর্টের ভূমিকা সন্দেহের উর্দ্ধে নয়। এক কলমের খোঁচায় ২৬,০০০ চাকুরিরত শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করা এবং সেই রায়কে বিনা সমালোচনায় স্বাগত জানানো সৎভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরকে ক্ষুব্ধ করেছে। এর চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়েছে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাঝে ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করার হাইকোর্টের রায়। পুরোনো মামলার নির্বাচন চলাকালীন সময়ে হঠাৎ করে এই রায় ঘোষণা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যহীন নাও হতে পারে। এর ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত বেকার ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি অপেক্ষায় থাকা ছাত্ররা চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। এই রায়কে সোচ্চারে স্বাগত জানানোও রণকৌশলগত দিক থেকে যথার্থ নয়। রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোটদাতাদের একটি বড় অংশ এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়।
এবার সিপিআই(এম)-এর তরফে বলা হয়েছে মানুষের মতাভিমত নেওয়া হবে। এটাকে শুধুমাত্র নির্বাচনী পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। দলের সাংগঠনিক কাঠামোর সংস্কারের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে শাখাগত স্তরে রাজনৈতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে পাবলিক কনসালটেশন বা জনসাধারণের সাথে মতবিনিময়ের একটি স্থায়ী সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। প্রয়োজনে এরিয়া, জেলা বা রাজ্যস্তরেও গণপরামর্শের একটি স্থায়ী সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার কথা ভাবা যেতে পারে। পার্টির সাধারণ সদস্য ও কর্মী, সমর্থক দরদী ও সাধারণ জনগণের সাথে সমান্তরালভাবে আলাদা আলাদা গণপরামর্শের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার কথা ভাবা যেতে পারে। পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে লাতিন আমেরিকার নতুন ধারার বামপন্থীরা তাদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মধারায় জনগনের অংশগ্রহণের নানা নতুন ব্যবস্থাপনার কথা ভাবছে। সারা পৃথিবীজুড়েই বিকল্প রাজনৈতিক ভাবনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে 'পাবলিক কনসালটেশন' বা 'গণপরামর্শ'। লাতিন আমেরিকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জনগনের তরফ থেকে এর অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জনসাধারণের স্নায়ু বন্ধনের জীবন্ত ব্যবস্থাপনা ব্যতিরেকে আজকের দিনে শক্তিশালী বাম আন্দোলন গড়ে তোলা অসম্ভব। কেন্দ্রীভূত সংগঠনের সর্বময় কর্তৃত্বের রাজনীতির দিন এখন আর নেই। সারা বিশ্বব্যাপী উগ্র দক্ষিণপন্থার উত্থানের এই সময়কালে গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ ভাবনায় পরিচালিত গণআন্দোলন ও দল ছাড়া বিকল্প রাজনীতির পথ তৈরি করা অসম্ভব।
ন'য়ের দশকে সোভিয়েত উত্তর সময়ের নয়া উদারবাদের সময়ে কেরলে উন্নয়নের বিকল্প ভাবনা নিয়ে এগোনোর জন্যে যেভাবে 'কংগ্রেস ফর কেরালা স্টাডিজ' সংগঠিত হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের বিকল্প পথ অন্বেষণের জন্যে একটি মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের আয়োজন করা যেতেই পারে যেখানে অংশ নেবেন রাজনৈতিক কর্মী, বিদ্যাচর্চার পরিসরের মানুষ, সামাজিক আন্দোলনের কর্মী ও সমাজের বিভিন্ন অংশের সাধারণ মানুষেরা। এমন একটি প্রস্তাব নিশ্চয়ই অভিনব এবং কিছুটা দুঃসাহসিক। আজকের সময় এমনই অভিনব, দুঃসাহসিক ও সন্নিষ্ঠ উদ্যোগেরই প্রত্যাশা করে।