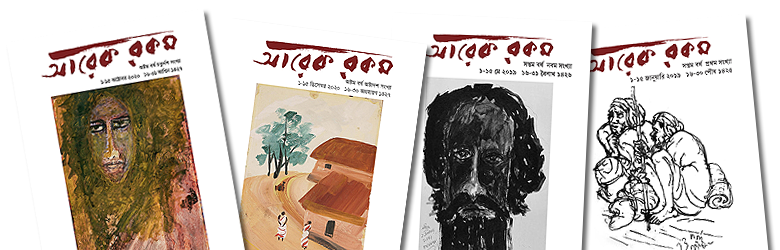আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ ত্রয়োদশ সংখ্যা ● ১-১৫ জুলাই, ২০২৪ ● ১৬-৩১ আষাঢ়, ১৪৩১
সম্পাদকীয়
প্রকৃতির প্রতিশোধ

সিকিম। হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত এই ছোট্ট ভূখণ্ড ১৯৭৫ থেকে ভারতের অন্যতম রাজ্য। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী সেখানে নিয়মিত লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জয়ী হয়ে গত পঞ্চাশ বছর ধরে রাজ্যের প্রশাসন পরিচালনা করে চলেছে। দল ভিন্ন হলেও একটি বিষয়ে সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তা হল - সকলেই সিকিমের উন্নয়ন চায়।
সত্যি সত্যিই উন্নয়ন হয়ে চলেছে। কংক্রিট সমৃদ্ধ উন্নয়ন। ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক শহরে পাকা দোতলা বাড়ি ছিল একটি। চোগিয়াল রাজাদের প্রাসাদ। বাদবাকি মূলত একতলা এবং পাকা নয়, কাঠ-বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত। আর এখন উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় শহরজুড়ে গড়ে উঠেছে অসংখ্য বহুতল। পাহাড় কেটে, প্রাচীন গাছ কেটে তৈরি হয়েই চলেছে রাস্তা-ইমারত-বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি।
পর্যটন যে রাজ্যের প্রধান অর্থনৈতিক উপাদান সেখানে সময় সুযোগ করে পর্যটক দু’ দন্ড স্বস্তির আশায় নিশ্চয়ই যাবেন। এটাই তো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। পর্যটনের মরসুমে এত বেশি পর্যটকের পদচিহ্ন সিকিমের মাটিতে অঙ্কিত হচ্ছে যে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। সঙ্গে রয়েছে জলাভাব। ফলাফল - বোতলের জলের চাহিদা বাড়ছে। এবং বেড়ে চলেছে প্লাস্টিকের শূন্য বোতল, যা তৈরি করছে অপরিমেয় পরিবেশ দূষণ। এত কিছুর পরেও বর্তমানে সেই স্বস্তি দুশ্চিন্তায় পর্যবসিত। প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া একাধিক পর্যটনকেন্দ্রকে স্বাভাবিক করে পর্যটকদের উদ্ধার করাই সিকিম প্রশাসনের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বারেবারেই একই ঘটনা ঘটে চলেছে। উদ্ধারকাজ শেষ করে পর্যটকদের কোনোরকমে বাড়ির পথে পাঠিয়ে বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে ভেঙে পড়া পরিকাঠামোকেও কাজ চালানোর মতো সুস্থ করার প্রচেষ্টা জারি আছে। কিন্তু প্রশ্নগুলো মিলিয়ে যায়নি - পরিবেশ বনাম উন্নয়নের সংঘাতের প্রশ্ন। উত্তরাখণ্ডের পথ পেরিয়ে সিকিম হয়ে আপাতত সেই প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের একেবারে শিয়রে এসে পৌঁছেছে।
প্রায়শঃই প্রকাশিত হয় সিকিমের ধ্বংসের খবর। বৃষ্টি-প্লাবনে ধুয়ে যায় উন্নয়নের কীর্তি। প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়। কখনও কখনও পুরো রাজ্যটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সামরিক বাহিনী যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালিয়ে স্থানীয় মানুষ ও পর্যটকদের উদ্ধার করে। সত্যি সত্যিই একমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ই যেন সিকিমের নাম সংবাদমাধ্যমে উচ্চারিত হয়। সিকিম সংক্রান্ত অন্য কোনো খবর বছরের অন্য সময় নজরে আসে কি?
সাম্প্রতিক অতীতে গত অক্টোবরে হিমবাহ হ্রদ ফেটে উত্তর সিকিমে ভয়াল বন্যার ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার হিসেব কষে ওঠার আগেই প্রবল বৃষ্টি, ধস ও ফুঁসতে থাকা তিস্তা ফের সেই বিপর্যয়ের দিনগুলি ফিরিয়ে দিল। অক্টোবর এবং জুন - তীব্রতা ও ব্যাপ্তির দিক থেকে দু’টি বিপর্যয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ঘটনাপরম্পরা প্রায় একই। প্রবল বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গ থেকে সিকিম পৌঁছনোর গুরুত্বপূর্ণ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ, উত্তর সিকিমে প্রবল বৃষ্টি ও ধসে প্রাণহানি, তিস্তার জল বিপদসীমা পার করে কালিম্পঙেরও একাংশ ভাসিয়ে দেওয়া - প্রতি বছর এমনটিই যেন পাহাড়ের নিয়ম হয়ে গেছে।
কেন বার বার বিধ্বস্ত হচ্ছে পাহাড়, এর উত্তরটি লুকিয়ে আছে সরকারি নানা সিদ্ধান্তের অন্দরে। স্থানীয় ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যর বিরুদ্ধে গিয়ে উন্নয়নের প্রচেষ্টা আত্মধ্বংসকারী। উত্তরাখণ্ড, হিমাচল থেকে সিকিম বার বার সেই প্রমাণই দিয়ে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে অরুণাচল প্রদেশও সেই তালিকায় যুক্ত হতে পারে।
সিকিমের পাহাড় চরিত্রগতভাবে ধসপ্রবণ। সামান্য বর্ষাতেই পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে নামে মাটি, পাথরের স্রোত। ভূপ্রকৃতিগত সেই বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করে সেখানে পাহাড় ফাটিয়ে তৈরি হচ্ছে সেবক-রংপো রেলপথ। যে উত্তর সিকিম বার বার প্রকৃতির রোষে পড়ছে, সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্বিচারে প্রাচীন গাছ, পাহাড় কেটে চওড়া হয়েছে রাস্তা, গড়ে উঠেছে অগুনতি হোটেল। সেখানে পাহাড়ি নদীর দু’পাশের প্লাবনভূমি প্রায় চোখেই পড়ে না। নদীখাতের উপরে হুমড়ি খেয়ে গড়ে উঠেছে হোটেল, রেস্তোরাঁ। অতিবৃষ্টিতে নদীর জল বৃদ্ধি পেলে বাড়িঘর ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণটি তাই সহজবোধ্য। এই সমস্ত নির্মাণের পূর্বে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে বিপদের সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখা হয় কি না অথবা বিশেষজ্ঞদের মতামত বিবেচনা করা হয় কি না, সন্দেহ আছে।
উষ্ণায়নের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাবটি ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। তার থেকে পাহাড়ও যে রেহাই পাবে না, তা নিশ্চিত। কিন্তু প্রাকৃতিক সেই পরিবর্তনকে আরও উস্কে দিতে পারে, এমন বিবেচনাহীন কর্মকাণ্ডের খুব কি প্রয়োজন আছে? হিমালয় পর্বতমালার ভূতাত্বিক (geological) সমীক্ষা হলেও ভূপ্রাকৃতিক (geomorphological) (ভূগর্ভস্থ পাথর, জলের স্তর বিন্যাস, ভূমিকম্প প্রবণতা ইত্যাদি) বিষয়ে সমীক্ষা হয়েছে কি? গত পঞ্চাশ বছর ধরে এই প্রশ্নটি যে কোনো প্রকল্প প্রণয়নের সময় তোলা হলেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তার উত্তর এড়িয়ে যাওয়াটাই যেন দস্তুর। এই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক শর্ত অস্বীকার করে কেন প্রকল্পের নীলনকশা ছকা হয়? কেন বিশেষজ্ঞরা নীতি নির্ধারকদের বোঝাতে সক্ষম হন না যে প্রকৃতির প্রকৃত চরিত্র না বুঝে প্রকল্প প্রণয়নের মধ্যে কী বিপদ জড়িয়ে রয়েছে? প্রাচীন গাছের শিকড় পাহাড়ের ভূমি সংরক্ষণে কী ভূমিকা পালন করে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা কি বড্ডো কঠিন? বিকাশের স্বপ্ন ফেরি করে নীতি নির্ধারকদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। জনগণের কাছে তাঁদের দায়বদ্ধতা আছে। বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে দায়বদ্ধ। নীতি নির্ধারকদের সুরে সুর মেলানো কি এতটাই জরুরি?
বিশেষজ্ঞরা তিস্তা নদীর খাত পাথর, পলিতে ভরাট হয়ে আসার কথা বহুবার বললেও আশ্চর্যজনকভাবে সরকারের কাজ এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র একের পর এক বাঁধ নির্মাণেই আবদ্ধ। পাহাড়ের উন্নয়ন প্রয়োজন অবশ্যই, কিন্তু সেই উন্নয়নের বিপুল ভার সামলানোর জমিটি যথেষ্ট শক্তপোক্ত কি না, সেটা দেখে নেওয়াও একই রকম জরুরি। জঙ্গল কাটায়, বাঁধ নির্মাণে স্থানীয়দের আপত্তিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার, কারণ ভূমিপুত্র হওয়ায় তাঁরাই সেখানকার মাটিকে নির্ভুলভাবে চেনেন।
নীতি নির্ধারক বা সরকার এ বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত উদাসীন। প্রতিটি বিপর্যয়ের পর সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়, -
● বিপর্যয় মোকাবিলায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চলছে।
● বিপর্যস্ত মানুষের উদ্ধারকাজ অব্যাহত।
●অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা রচিত হবে।
তারপর আবার যে কে সেই। কোনো পরিবর্তন নেই। এ যেন এক বৃত্তপথে অন্তবিহীন পরিক্রমা। বিকাশের তকমা এঁটে ধারাবাহিকভাবে প্রকৃতির ধ্বংসসাধন। তারপর প্রকৃতির প্রতিশোধ জনিত বিপর্যয়। এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় ব্যস্ত প্রশাসন। কাজেই নিয়মিত ধ্বংস-বিপর্যয়-প্রাণহানি ঠেকানোর উপায়টিও আপাতত তিস্তাগর্ভেই বিলীন হয়ে গিয়েছে।