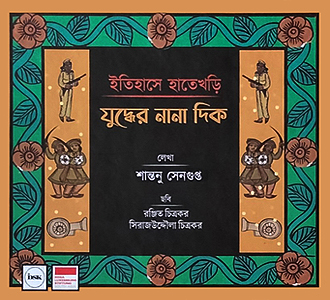আরেক রকম ● একাদশ বর্ষ চতুর্বিংশ সংখ্যা ● ১৬-৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ ● ১-১৫ পৌষ, ১৪৩০
প্রবন্ধ
ইতিহাস গুলিয়ে দেওয়া সময়ের ভ্যাকসিন
সম্বিত বসু
ভরা ডিসেম্বরের শুরুতে এ-লেখা নিয়ে বসেছি। ডিসেম্বর - শীতের সঙ্গে সঙ্গে একখানা বিষাদের স্মৃতিও নিয়ে আসে। কিন্তু বিষাদ, আজ আর তেমন সুলভ নয়। উল্লাস আর হিংস্রতাও আজ আর দুর্লভ নয় তেমন। এই ভারতের শরীরে, নদ-নদীতে, গাছে-পাথরে, বড়রাস্তায়-অলিগলিতে, আত্মায় আত্মায় ওই উল্লাস, ওই নারকীয় হিংস্রতা ঢুকে পড়ছে, আমরা দেখতে পারছি। দেখতে পারছি রোজকার খবরে, সামাজিক মাধ্যমে, পাড়ায়, চায়ের দোকানে, এমনকী, ঘরেও ঢুকে পড়ছে তা। কেজো এক দূরবিন দিয়ে ৩১ বছর আগের এক দিন, দেখতে পাচ্ছি, করসেবকদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বাবরি মসজিদ। দেখতে পাচ্ছি, আমাদেরই স্থাপত্য, প্রতি মুহূর্তে কীভাবে বদলে যাচ্ছে। ঠিক কোন অভিপ্রায়ে বদলে যাচ্ছে মিউজিয়ম, বদলে যাচ্ছে ঐতিহ্যময় সংসদ ভবন, সিলেবাস। বদলে দেওয়া হচ্ছে ইতিহাস, যে ইতিহাসের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক যৌথতা, আমাদের কৌম সমাজ, আমাদের কথা বলা, বেঁচে থাকা, নিত্যদিনের শ্বাস-প্রশ্বাস।
শোক ক্রমে ঘন হয়। উত্তর সম্পাদকীয়তে বাবরি প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে কেউ কেউ লেখেন, রামমন্দির গড়ার মধ্য দিয়েই যেন মন্দির-মসজিদের বিভেদ রাজনীতির ইতি ঘটে। এই বিপুল পজেটিভিটি দেখে, কপালে আরও কিছু দাগ জমা পড়ে। সিলেবাস থেকে বাদ পড়ে ইতিহাস-বিজ্ঞানের জরুরি অধ্যায়গুলো। ঢুকে পড়ে পুরাণ। কোথায় জন্ম হয়েছিল রামের, এই সকল অগা ইতিবৃত্ত। কে দেখেছে রামকে - এমন প্রশ্ন এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগেও করা চলে না। অবশ্য কৃত্রিমত্বে ভরসা করে এখন যে-কেউই রামকে অযোধ্যায় বসিয়ে ফেলতে পারে। আর ভারত যদি কোনও কারখানা গড়ে রাখে নিজের মনে, তা বিশ্বাসের। নইলে, স্রেফ সন্দেহের বশে, ফ্রিজে গরুর মাংস রাখা আছে - এই অপরাধে খুন হওয়া এই একুশ শতকে অসম্ভব!
এই ভারতে ইতিহাসই ভয়াবহ বিপাকে। কারণ আমাদের আত্মপরিচয় বহন করছে আমাদের ইতিহাসই। আমাদের আত্মার একমাত্র আধার কার্ড ওই ইতিহাস। যে ইতিহাসে স্বীকার করা রয়েছে মুঘলদের, শক, হুন, পাঠানদেরও। সংস্কৃতির এই মিশ্রণ ছাড়া, আজকের ভারত তৈরি হতে পারত না। যে কোনও ভারতীয়, সে তার ইতিহাসকে অস্বীকার করতে পারে হয়তো, কিন্তু ইতিহাস তাকে বহন করছে - এ জিনিস হাতেনাতে প্রমাণও করে ফেলা যাবে তর্কের পরিসর তৈরি হলেই। তা শুধু স্থানিক নয়, শারীরিক, বাচনিক - বিভিন্ন পদ্ধতিতেই।
রামের বনবাস থেকে সিলেবাস - এই বিচিত্র যাত্রা, এই পুরাণের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়া হল পাঠ্যক্রমে, ঢেকে দেওয়া হল সত্যকে, ঐতিহাসিকতাকে - এর থেকে নিস্তার পাওয়ার কি উপায় ছিল না কোনও? তার একমাত্রই ভ্যাকসিন, সদর্থক ইতিহাস পড়া, যুক্তি দিয়ে, তথ্য মেনে, সঠিক ইতিহাসের দিকে মনকে নিয়ে যাওয়া। ‘ইতিহাসের হাতেখড়ি’ সিরিজের বইগুলো একলপ্তে পড়ে এইসব কথাই মনে হল ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে। ‘হাতেখড়ি’ শব্দবন্ধের ব্যবহারও লক্ষ করুন। এ অনেকটাই যেন প্রাথমিকতা দিয়ে গড়া। অর্থাৎ, ইতিহাসের ভিত গড়ুন। এইটুকু সঙ্গে থাকলে, বোধহয় ওই সিলেবাসীয় পুরাণের প্রগলভতা গায়ে এসে লাগবে না সহজে। এইটুকু সঙ্গে পেলে, গুলিয়ে দেওয়া সহজ হবে না। ইতিহাস লেখার ইতিহাস ও তারও নেপথ্যে যে ইতিহাস চাপা দেওয়া, সেই অন্ধকারেও আলো ফেলে দেখাতে চেয়েছে এই সিরিজ। কল্পিত নয়, তথ্য জুগিয়েছে তবু তথ্য ভারাক্রান্ত হয়নি। গল্পচ্ছলে, কিন্তু গল্প বলেনি মোটেই। তা দিনশেষে ইতিহাসেরই সজীব পাঠ। যে পাঠ, সিলেবাসীয় খাঁচায় আটকে থাকেনি। যে পাঠ তৈরি করতে পারে অজস্র প্রশ্ন করার ক্ষমতা, বুঝে নেওয়ার চর্যা।
যদিও ওই অন্যায্য আঘাত শুধু সিলেবাসে এসে লেগেছে, এমন না। লেগেছে আমাদের ভাষাতেও। কারণ তারও তো রয়েছে প্রতুল ইতিহাস। সে ইতিহাস বুঝলে, অনুভব করলে, এ-ও বোঝা উচিত এ-দেশ কখনও একটি ভাষায় যোগাযোগ করার কথা বলতে পারে না। একটি ভাষাই হয়ে উঠবে সেতুসম, রাজনীতিকরা বললেও, সাধারণ একে মান্যতা দেওয়ার, এমনকী, পক্ষ নিয়ে তর্ক করার কথাও হয়তো বা ভাবতে পারতেন না। দেবারতি বাগচী যেমন সামান্য একটা উদাহরণেই খোলসা করে দিচ্ছেন ব্যাপারটা, তার ইতিহাসের হাতেখড়ি ‘দেশের ভাষা’ সিরিজটিতে। তিনি যাচ্ছেন কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরু। ট্রেন যখন চলা শুরু করেছিল, তখন স্টেশনের নাম ছিল তিনটি ভাষায়। বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি। ক্রমে, ট্রেন যত এগোয়, তত বদলাতে থাকে ভাষা, হরফ। ভুবনেশ্বরে ওড়িয়া হরফ, বিজয়ওয়াড়ায় তেলুগু, কর্ণাটকে কন্নড়। হরফে ও ভাষাতেই তো অনেকটা ভারতদর্শন হয়ে যায়। ইতিহাসের ঝাঁপি থেকে তিনি বের করেছেন ভাষার এই সীমানা মোটামুটি কীভাবে নির্ধারিত হল, সে সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি। লিখেছেন ভাষা সংগ্রামের কথাও। বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, অসমের ভাষা সংকট, একটা ভাষার জন্য তৈরি হওয়া রাজ্য - অন্ধ্রপ্রদেশ নির্মাণের নেপথ্য কাহিনিও। এই সুযোগে আরও একবার, আমার বলে নেওয়া উচিত, ভারতের কোনও ‘জাতীয় ভাষা’ নেই। সংবিধান অনুযায়ী নেই, হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় অনুযায়ী অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা হতে পারে। কেন ‘জাতীয় ভাষা’ নেই, হতে পারে না, তার ইঙ্গিত যশোধরা বাগচীর লেখা থেকে স্পষ্ট - "বাংলা-নেপালির ঝগড়ার খবরে চাপা পড়ে গিয়ে উত্তরবঙ্গের এক কোণে টোটো ভাষাও কোনও রকমে টিকে আছে। দেশের কোনও রেল স্টেশনে এই সব ভাষার দেখা পাওয়া যায় না। আচ্ছা, দেশের একটাই ভাষা হওয়া উচিত, না কি নয়, এই ঝগড়ায় কি এঁরাও গলা মেলাতে পারেন? মোটেই তা পারেন না। সে এক্তিয়ার কেবল তামিল, বাংলা, মারাঠি, অসমীয়ার মতো ক্ষমতায় বড় অন্য ভাষাগুলির।"
এবং, এর পরেই রয়েছে সেই অমোঘ প্রশ্নঃ “তাহলে কোনটা দেশের কোনটা জাতীয়, এসব কি আসলে ঠিক করে কিছু মানুষ? তাহলে ‘দেশের’ - এই শব্দটার মানে কী? ‘জাতীয়’ কাকে বলে? যা সকলের, নাকি সকলকে মানতে হবে? এই প্রশ্নের জবাব কিন্তু রাষ্ট্র কেবলই এড়িয়ে যায়।”
এই এড়িয়ে যাওয়া, স্বভাবতই সত্যের সম্মুখীন হওয়ার ভয়ে। কোনও ইতিহাস-বিরোধী রাষ্ট্রক্ষমতাই এইসব প্রশ্নকলার খোসায় হড়কাতে চাইবে না। ক্ষমতা শুধু প্রশ্ন করবে, যেমনটা অনেক আগেই বলে গিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষঃ "তুমি কোন দলে?" এবং এজন্য দরকার পড়বে চিহ্নিতকরণের। আর সেই ছুতোয় গড়ে উঠবে এক আশ্চর্য পচা-গলা দেশ, দেশের মন, আত্মা। তা অ-সম্ভব করে তুলতে, আমরা জেনে নিতে পারি ‘আমরা’ বলতে আমরা আসলে কাকে বুঝি? আদৌ কি বুঝি? আজ থেকে বছর ৪-৫ আগে, ‘অহর্নিশ’ পত্রিকার একটা ছোট লিফলেট হাতে এসে পড়েছিল। তাতে লেখা ছিল, ‘প্রতিবেশীকে চিনুন’। শুধুমাত্র এই যৎসামান্য কাজটা করলেই ‘আমরা’ এই শব্দটা থেকে সদর্থক আলো বেরোতে থাকে। প্রতিবেশীকে জানতে গেলে, ব্যক্তিগতের সীমানা এবং সীমানা পেরিয়ে চেনাটাও জরুরি। কিন্তু জরুরি এ-ও যে, ‘নাগরিক’ বলতে কাকে বুঝব। কীভাবেই বা আমরা ‘নাগরিক’ হয়ে উঠতে পেরেছি, বা আদৌ পেরেছি কি না। কাকে বলছি ‘দেশের মানুষ’, আর দেশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কাদের অস্বীকার করা হচ্ছে? রাজনীতি আসলে এমন এক ঘড়ির কাঁটা, যা অনেকের গলায় আটকে যায়। যে কারণে বাঁকুড়ার রাধানগরের গঙ্গাধর প্রামাণিক কাজের খোঁজে অসম গিয়ে আটকা পড়েন ‘বিদেশি’ সন্দেহে। নিজেকে ‘ভারতীয়’ প্রমাণ না করতে পারার অপরাধে অসমের গোয়ালপাড়া ক্যাম্পে তাঁকে থাকতে হয়েছিল চার বছর। একইরকমভাবে বারবার হেনস্তা হতে হয় হাসিনা ভানুকেও। সীমান্ত, দেশভাগ, আইন-কানুন, নাগরিক আইন ২০১৯ এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জির মতো বিবিধ বিষয় নিয়ে সাধারণের ‘আইডিয়া’কে মজবুত করে তুলেছেন তিস্তা দাস। ‘দেশের মানুষ’ হয়ে ওঠার বন্ধুর পথে, তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন আমাদের অতি-জরুরি এক কথা - "নাগরিকত্ব আর তার ছাঁকনি যেন জীবনের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা এই মানুষদের জীবনে। ছাঁকনিতে আটকে পড়লেই হল! এই ছাঁকনি যেন দেশের মানুষকে বিপদে না ফেলে, সেই চেষ্টা করে যাওয়া আমাদের সকলের কাজ, সকল নাগরিকের দায়িত্ব।" এত দূর এসে, দেখি, ইতিহাস কী, তারও একটা সহজবোধ্য উত্তর দেওয়া যাচ্ছে - "...ইতিহাস তো আর শুধুই কবে, কী ঘটেছে, তার ফর্দ নয়। ইতিহাস মানে কোনও পুরনো ঘটনাকে নানাভাবে বোঝার চেষ্টা করা। সেই ঘটনা কীভাবে ঘটল, তার ফলে কী হল, এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করা।" একথা অন্বেষা সেনগুপ্ত লিখছেন ‘ইতিহাসের হাতেখড়ি’ সিরিজের ‘দেশভাগ’ বইটিতে। দেশভাগ এমন এক ক্ষত, যা আমরা বহন করে চলেছি রক্তে। স্মৃতি থেকে কখন যে রক্তে এই প্রবেশ - সেই মুহূর্তটিকে ঠিক আন্দাজ করে বলা সম্ভব না। দেশভাগেই ইতিহাস বলতে বলতে, তিনি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বাস্তুদের কথা বলেছেন। বলেছেন ইংরেজ আমল, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কথা। ভারতীয়দের ‘জাতপাত’ সমস্যা এবং ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্রুরতায় ঐক্য আলগা করে রাখা। উদ্বাস্তদের কথা বলতে গিয়ে বড় অস্বস্তির এক ইতিহাস সামনে এনেছেন অন্বেষা। দেশভাগের সময় বিধান রায়ের বক্তব্য ছিল দেশভাগের উদ্বাস্তু মানুষদের দায় গ্রহণ করতে হবে সকলকেই, এ শুধু পশ্চিমবঙ্গর দ্বারা অসম্ভব। খালিচোখে, বড় উপকারি, স্নেহময়, বিচক্ষণ লাগে অনুভবী মানুষটি। তিনি উদ্যোগ নিয়ে উদ্বাস্তুদের পাঠিয়েওছিলেন আন্দামানে। কিন্তু এখানেই ইতিহাসকে অন্যভাবে খতিয়ে দেখছেন তিনি, দেখছেন, আসলে ওই উদ্বাস্ত কারা? যাঁরা পৌঁছেছিলেন আন্দামান নামক দ্বীপে? জানা গিয়েছে, তাঁরা ছিলেন চাষি, জেলে, কামার কিংবা মিস্ত্রি। এবং, তিনি লিখছেন, "কোনও ডাক্তার, কবিরাজ, মাস্টার, ব্যবসায়ী বা জমিদারকে কিন্তু আন্দামানে পাঠানো হয়নি।" এই বই শুধুই জিন্নাহ, নেহরু কিংবা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কথাই বলে না, বলে সাধারণ মানুষদের কথাও - দেশরাজ, নাসের, বীথি এবং উদ্বাস্তু হয়ে যাঁরা আন্দামানে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদের কথাও। যে ইতিহাস চর্চিত, সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি থেকে সরে এসে, দেশভাগের স্বল্প-চর্চিত আখ্যান তুলে ধরেছে এই বই।

আপাতত, কথা বললাম ‘ইতিহাসে হাতেখড়ি’ সিরিজের তিনটি বই নিয়ে। ‘দেশভাগ’, ‘দেশের মানুষ’ এবং ‘দেশের ভাষা’। যদিও এ-ছাড়াও সিরিজের আরও তিনটি বই, ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে - ‘চায়ের দুনিয়া’, ‘যুদ্ধের নানা দিক’ এবং ‘নদীর চলা’। সে নিয়ে না হয় আর-একদিন কথা বলা যাবে। তবে, এ লেখায় যা না বললেই নয়, শুধুই অনর্গল ইতিহাস বলে চলেনি এই বইগুলো, ইতিহাসকে দেখিয়েওছে। রয়েছে মানচিত্র, চমৎকার অলংকরণ - যা স্বতন্ত্র গুরুত্ব বহন করছে। অলংকরণ শিল্পী রঞ্জিত চিত্রকর ও সিরাজদৌল্লা চিত্রকরকে ধন্যবাদ বাংলা বইয়ের অলংকরণের ইতিহাসে এই নতুন সংযোজনের জন্য।